 এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকরা যুক্তরাষ্ট্রের অতিভোগ, সঞ্চয়ের অভাব এবং দায় পরিশোধ না করার প্রবণতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। লেখকদের মতে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় অন্য দেশগুলো আর যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের ওপর আস্থা রাখবে না। তখন অর্থনীতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকরা যুক্তরাষ্ট্রের অতিভোগ, সঞ্চয়ের অভাব এবং দায় পরিশোধ না করার প্রবণতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। লেখকদের মতে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় অন্য দেশগুলো আর যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের ওপর আস্থা রাখবে না। তখন অর্থনীতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।
একসময় সত্যি দ্বীপের এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যেটি তাঁরা তাঁদের বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দেখিয়েছেন। অর্থনীতি যখন ভেঙে পড়ে, তখন একজন সিনেটর, যাঁকে আসলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে, অসহায়ভাবে বলেন, ‘Does anybody here remember how to make a net? I think it’s time we all went fishing.’
এই বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি বোঝায় যে যদি কখনো কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে পড়ে, তখন আমাদের আবার মৌলিক উৎপাদন সক্ষমতায় ফিরে যেতে হবে। প্রশ্ন হলো, আমরা সেই সক্ষমতা এখনো রাখি তো?
এই বইয়ে লেখকরা বলতে চেয়েছেন প্রকৃত সমৃদ্ধি আসে যখন মানুষ সঞ্চয় করে, নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়ায় এবং সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। ডলার ছাপিয়ে ভোগ বাড়িয়ে অর্থনীতিকে সচল রাখা একটি ভঙ্গুর ব্যবস্থা, যা যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। লেখকদের মতে, অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকদের উচিত এই বাস্তবতা বোঝা এবং সুশৃঙ্খল, উৎপাদননির্ভর পথে ফিরে যাওয়া।
লেখকরা দেখিয়েছেন, একটি অর্থনীতি তখনই টেকসই হয়, যখন সেটি উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগভিত্তিক হয়। মুদ্রা ছাপানো, অতিভোগ এবং ঋণের ওপর নির্ভরতা একটি ফাঁপাকাঠামো তৈরি করে, যা ভেঙে পড়লে আবার ‘জাল বানিয়ে মাছ ধরতে’ শিখতে হয় অর্থাৎ প্রকৃত উৎপাদনে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু তখন সেটি অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে।
আমেরিকা কি বুঝতে পেরেছে যে দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তাদের আবার ‘মাছ ধরা’ শুরু করা উচিত? গত শতকের ত্রিশের দশকে মহামন্দার পর যে অর্থনৈতিক পুনরুত্থান ঘটেছিল, তার মূল চালিকাশক্তি ছিল তাদের শক্তিশালী উৎপাদনব্যবস্থা। এতটাই উৎপাদন হতো যে এক পর্যায়ে তাদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এসব পণ্যের কী করা হবে। কিন্তু সেই যুগ পেরিয়ে আমেরিকা অনেক আগেই উৎপাদননির্ভরতা থেকে সরে এসেছে। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কি আবার সেই উৎপাদনের পথেই ফিরে যেতে চাইছে?
ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতিকে অনেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ হিসেবে দেখে। কিন্তু বাস্তবে এই শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্য হয়তো পুরো পৃথিবীকে শায়েস্তা করা নয়, বরং নিজ দেশের মানুষের অতিরিক্ত খরচের প্রবণতায় লাগাম টেনে ধরা। মার্কিন সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সঞ্চয়ের তুলনায় খরচকে উৎসাহ দেওয়া হয় বেশি।
সরকারের দিক থেকেও এই খরচকে উৎসাহ দেওয়া হয়। কারণ তাদের মুদ্রা ডলার গোটা বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তারা যখন খুশি তখন টাকা ছাপিয়ে বাজারে সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু এই একচেটিয়া সুবিধা চিরকাল টিকবে, এমনটি ধরে নেওয়া ঠিক নয়।
যদি ডলারের এই একচ্ছত্র আধিপত্য একদিন হারিয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমদানিকারক ও সবচেয়ে বেশি খরচ করা জাতি মার্কিনরা অর্থনৈতিকভাবে এমন এক সংকটে পড়বে, যেখানে ‘ঘটি-বাটি’ বেচার অবস্থা হয়ে যেতে পারে; যেই ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কাঠামোর চিত্র পিটার ও অ্যান্ড্রু শিফের ‘How an Economy Grows and Why It Crashes’ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।
শুধু খরচের অভ্যাস বদলানোই নয়, আমেরিকার সামনে আরো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, তারা এখন আর সেভাবে উৎপাদন করে না। তারা শুধু কেনে। এই শুল্ক আরোপের ফলে যদি আমদানি করা পণ্যের দাম বাড়ে, তবে খরচ কমাতে বাধ্য হবে জনগণ, যার ফলে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়তে পারে। সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগে গতি আসবে। সেই বিনিয়োগই আবার উৎপাদন খাতকে সক্রিয় করতে পারে।
যদি চিন্তা করা যায় একটি জাতি, যাদের হাতে সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি রয়েছে, উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে এবং রয়েছে এমন এক ভোক্তা শ্রেণি, যারা উচ্চমূল্যেও পণ্য কিনতে আগ্রহী, তাদের নিজ দেশে উৎপাদনের বিকল্প কি সত্যি আর থাকবে? বিশেষ করে যখন তারা বিদেশি পণ্যের অভাব অনুভব করতে শুরু করে?
এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে তারা উৎপাদন থেকে সরে এসেছিল কেন? এর দুটি বড় কারণ ছিল : প্রথমত, শ্রম ব্যয় অত্যন্ত বেশি হওয়ায় ওই ব্যয়ে ব্যবসা লাভজনক রাখা সম্ভব হচ্ছিল না; দ্বিতীয়ত, কঠোর পরিবেশগত বিধি-নিষেধের কারণে দেশে উৎপাদন জটিল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে রোবটিকস ও অটোমেশনের চরম উন্নতির ফলে, এমনকি গার্মেন্টসের মতো শ্রমনির্ভর খাতেও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠেছে। আর যদি এই প্রযুক্তির সঙ্গে দ্রুতগতির এআই ব্যবহৃত হয়, তাহলে শ্রমিকনির্ভরতার প্রয়োজন অনেকটাই কমে যাবে। এর ফলে উচ্চ শ্রম ব্যয়ের বাধা দূর হবে এবং উৎপাদন আবারও লাভজনক হয়ে উঠতে পারে।
এখানেই আসে চীনের প্রসঙ্গ। ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতির লক্ষ্যবস্তু প্রধানত চীন। কারণ চীন থেকেই আমেরিকার আমদানি সবচেয়ে বেশি। এই শুল্ক কি আমেরিকার নিজস্ব উৎপাদনে ফিরে যাওয়ার সংকেত নয়? সম্ভবত তাই। এবং চীনও এই পরিবর্তন অনুধাবন করেছে বলেই এক দশক ধরে তারা চেষ্টা করছে তাদের জনগণের ভোগের প্রবণতা বাড়াতে। ঐতিহ্যগতভাবে সঞ্চয়প্রবণ একটি জাতি হিসেবে পরিচিত হলেও চীন এখন তার জনগণকে আরো বেশি খরচ করতে উৎসাহ দিচ্ছে।
এই উভয় দিকের পরিবর্তন একদিকে আমেরিকার উৎপাদনে ফিরে যাওয়ার প্রয়াস এবং অন্যদিকে চীনের খরচে উৎসাহ প্রদান বিশ্ব অর্থনীতির ভারসাম্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে, যেখানে উৎপাদন ও ভোগের নতুন সীমানা নির্ধারিত হবে। হয়তো ট্রাম্পের শুল্কনীতি আবার সেই মাছ ধরার শুরু।
লেখক : প্রাবন্ধিক
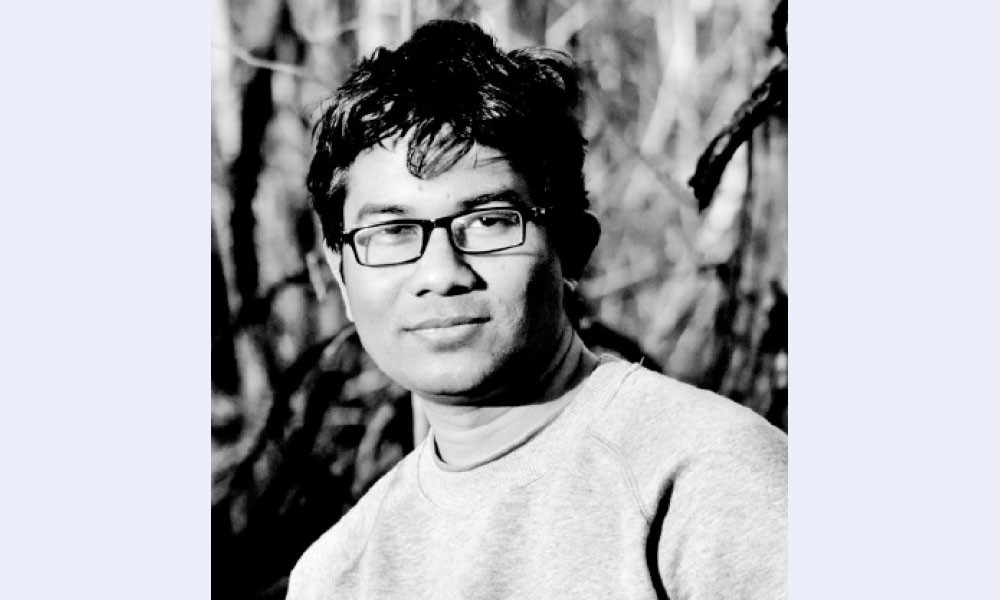
 এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকরা যুক্তরাষ্ট্রের অতিভোগ, সঞ্চয়ের অভাব এবং দায় পরিশোধ না করার প্রবণতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। লেখকদের মতে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় অন্য দেশগুলো আর যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের ওপর আস্থা রাখবে না। তখন অর্থনীতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকরা যুক্তরাষ্ট্রের অতিভোগ, সঞ্চয়ের অভাব এবং দায় পরিশোধ না করার প্রবণতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। লেখকদের মতে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় অন্য দেশগুলো আর যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের ওপর আস্থা রাখবে না। তখন অর্থনীতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।






 বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সংকট ও অনাস্থার পরিবেশ নতুন নয়। অনাস্থার বেড়াজাল থেকে রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই বের হতে পারেনি। গণতন্ত্রের নামে এবং গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকারে রাজনৈতিক দলগুলো বারবারই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে এমনই এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে বিদ্যমান রাজনীতি।
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সংকট ও অনাস্থার পরিবেশ নতুন নয়। অনাস্থার বেড়াজাল থেকে রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই বের হতে পারেনি। গণতন্ত্রের নামে এবং গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকারে রাজনৈতিক দলগুলো বারবারই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে এমনই এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে বিদ্যমান রাজনীতি।