দেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে নিয়মিত যে পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বাস্তবতার সঙ্গে তার মিল থাকে কম। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার, মূল্যস্ফীতি, উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাতে সাধারণ মানুষের পুরোপুরি আস্থা থাকে না।
খাদ্য নিরাপত্তার জন্য উৎপাদনের সঠিক পরিসংখ্যান দরকার
- ড. জাহাঙ্গীর আলম

বিগত সরকারের আমলে প্রায় ১৫ বছর ধরে নিয়মিতভাবে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে প্রায় ৬ থেকে ৮ শতাংশ। এর সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের উপলব্ধি তেমন বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। তবে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো বরাবরই তাতে আপত্তি জানিয়েছে। তারা ওই হিসাব থেকে এক থেকে দেড় শতাংশ পর্যন্ত কম অনুমান করেছে। দেশে  বিদ্যমান জনজীবনের আর্থিক অবস্থা, ভোগ চাহিদা ও বিনিয়োগের পরিস্থিতি বিবেচনায় বিগত সরকার প্রদর্শিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অনেকের কাছেই অতি মূল্যায়িত মনে হয়েছে। এর ঠিক উল্টো অবস্থা আমরা লক্ষ করেছি মূল্যস্ফীতির হিসাব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। কাগজে-কলমে মূল্যস্ফীতির হার সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ৫-৬ শতাংশের মধ্যে। কখনো তা প্রদর্শন করা হয়েছে ৭-৮ শতাংশে। বাস্তবে তা অনেক সময় দুই ডিজিটও অতিক্রম করে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ ও অনাস্থা ছিল প্রবল। গত জুলাই মাসে এই হার ছিল প্রায় ১৪ শতাংশ। অনেকে অনুমান করেছে ১৫ শতাংশেরও বেশি। একইভাবে সরকার বেকারত্বের হার কম দেখিয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছে। বিভিন্ন হিসাবে তা দেখানো হয়েছে সাড়ে ৪ থেকে সাড়ে ৫ শতাংশ। বেকারত্বের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত সংখ্যার কারণেও এই হারে কিছুটা তারতম্য ঘটেছে। তবে সাধারণভাবে দেশে বেকার মানুষের ঘনত্ব বিবেচনায় প্রদর্শিত হার অনেক কম বলে ধারণা করা হয়েছে। এমনিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বিগত সরকার। জনতুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে অনেকটা বিফল হয়ে পুষ্পশোভিত পরিসংখ্যান দিয়ে জন-অসন্তোষ ঢাকতে চেয়েছে।
বিদ্যমান জনজীবনের আর্থিক অবস্থা, ভোগ চাহিদা ও বিনিয়োগের পরিস্থিতি বিবেচনায় বিগত সরকার প্রদর্শিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অনেকের কাছেই অতি মূল্যায়িত মনে হয়েছে। এর ঠিক উল্টো অবস্থা আমরা লক্ষ করেছি মূল্যস্ফীতির হিসাব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। কাগজে-কলমে মূল্যস্ফীতির হার সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ৫-৬ শতাংশের মধ্যে। কখনো তা প্রদর্শন করা হয়েছে ৭-৮ শতাংশে। বাস্তবে তা অনেক সময় দুই ডিজিটও অতিক্রম করে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ ও অনাস্থা ছিল প্রবল। গত জুলাই মাসে এই হার ছিল প্রায় ১৪ শতাংশ। অনেকে অনুমান করেছে ১৫ শতাংশেরও বেশি। একইভাবে সরকার বেকারত্বের হার কম দেখিয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছে। বিভিন্ন হিসাবে তা দেখানো হয়েছে সাড়ে ৪ থেকে সাড়ে ৫ শতাংশ। বেকারত্বের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত সংখ্যার কারণেও এই হারে কিছুটা তারতম্য ঘটেছে। তবে সাধারণভাবে দেশে বেকার মানুষের ঘনত্ব বিবেচনায় প্রদর্শিত হার অনেক কম বলে ধারণা করা হয়েছে। এমনিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বিগত সরকার। জনতুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে অনেকটা বিফল হয়ে পুষ্পশোভিত পরিসংখ্যান দিয়ে জন-অসন্তোষ ঢাকতে চেয়েছে।
দেশের পণ্য উৎপাদন, চাহিদা এবং স্থিতির পরিসংখ্যান সম্পর্কে অতীতে সরকারের সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষি পরিসংখ্যানের কথা উল্লেখ করা যায়। অনেক সময় সরকারি ভাষ্যকে অতিকথন বলে মনে হয়েছে। প্রায়ই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রয়েছে। অথচ প্রায় প্রতিবছরই গড়পড়তা ৬০ থেকে ৭০ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে বিদেশ থেকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৯৮ লাখ মেট্রিক টন। স্বাধীনতার পর মোট আমদানির পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টন। এরপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় আড়াই শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে নেমে এসেছে ১.২ শতাংশে। অন্যদিকে মোট খাদ্যশস্যের কথিত উৎপাদন এক কোটি টন থেকে বেড়ে হয়েছে পাঁচ কোটি টনেরও অধিক। অথচ খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ সে অনুপাতে হ্রাস না পেয়ে বরং বেড়ে গেছে দ্বিগুণেরও বেশি। এ ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনের পরিসংখ্যান অতি মূল্যায়িত ভাবা অস্বাভাবিক নয়। অতি সম্প্রতি দেশে বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই স্ফীত; যে কারণে বাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনেক সময় পণ্যের সরবরাহ সংকট হেতু বাজার অস্থির হয়ে পড়ছে। পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। আমদানির আগাম প্রস্তুতি না থাকায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
উদাহরণস্বরূপ ২০২৩-২৪ সালের আলু উৎপাদনের হিসাব সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে আলুর উৎপাদন ছিল এক কোটি ছয় লাখ টন। খাদ্য চাহিদা ও বীজ মিলে আমাদের বার্ষিক সর্বোচ্চ চাহিদা ৯০ লাখ টন। এতে ১৫-১৬ লাখ টন আলু উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু বাজারে অস্থিরতা ও আলুর মূল্যবৃদ্ধি দেখে ধারণা করা হয়েছে যে ওই পরিসংখ্যান অতিরঞ্জিত ও স্ফীত ছিল। কারণ বিদেশ থেকে আলু আমদানি করেও মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো যায়নি। বাজারে আলু বিক্রি হয়েছে প্রতি কেজি ৭০ থেকে ৮০ টাকা। কোল্ড স্টোরেজগুলোতে অন্যান্য বছরে যেখানে ৪০ থেকে ৫০ লাখ টন আলু সংরক্ষণ করা হতো, সেখানে গত অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ মিলেও ৩০ লাখ টন আলু মজুদ ছিল না।
পেঁয়াজের উৎপাদন বার্ষিক ৩৪-৩৫ লাখ টন বলে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে দাবি করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯ লাখ মেট্রিক টন। আমাদের দেশে পেঁয়াজের চাহিদা ২৬ থেকে ২৮ লাখ টন। তার পরও প্রতিবছর ন্যূনপক্ষে ছয়-সাত লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। অনেক সময় পেঁয়াজের দাম হয়ে পড়ে আকাশচুম্বী। ভারত থেকে পেঁয়াজের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হলে বাংলাদেশে এর আকাল নেমে আসে।
চালের উৎপাদন নিয়ে সব সময়ই বিভ্রান্তি বিরাজ করে। আমাদের বার্ষিক উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে বিশাল উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর ১০ থেকে ১৫ লাখ টন চাল আমদানি করতে হয়। অনেক সময় আমদানি কম হলে সরবরাহ সংকটের কারণে চালের দাম বেড়ে যায়। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমাদের চালের উৎপাদন ছিল চার কোটি সাত লাখ মেট্রিক টন। ১৭ কোটি ৩০ লাখ মানুষের জন্য বার্ষিক খাদ্য চাহিদা সর্বোচ্চ তিন কোটি ৭৩ লাখ টন। এতে উদ্বৃত্ত থাকার কথা ৩৪ লাখ টন চাল। কিন্তু বাজারের অস্থিরতা ও মূল্যবৃদ্ধি দেখে মনে হয়নি এই উৎপাদনের পরিসংখ্যান সঠিক। ইউএসএআইডির হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চালের মোট উৎপাদন হয়েছিল তিন কোটি ৭০ লাখ টন। অর্থাত্ বাংলাদেশের সরকারি তথ্য অনুসারে চালের উৎপাদন ৩৭ লাখ টন বেশি দাবি করা হয়েছিল। এ বছর আন্তর্জাতিক বাজারে চালের উচ্চমূল্যের কারণে বেসরকারি ব্যবসায়ীরা আমদানিতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু গমের আমদানি ছিল রেকর্ড উচ্চতায় ৬৬ লাখ মেট্রিক টন।
২০২৪ পঞ্জিকা বর্ষের আমন চালের উৎপাদন এক কোটি ৭১ লাখ টন বলে দাবি করছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ। ইউএসএআইডি বলেছে, উৎপাদন হতে পারে এক কোটি ৪০ লাখ টন। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পর পর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় রিমালের কারণে চালের উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। দেরিতে চারা রোপণের কারণে হেক্টরপ্রতি ফলনও কম হয়েছে। কিন্তু তার প্রকৃত চিত্র কৃষি বিভাগের পরিসংখ্যানে নেই। তবে সাম্প্রতিক অস্থির চালের বাজারের অবস্থা দেখে মনে হয় না যে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হিসাব সঠিক। বিবিএস এখনো এবারের আমন চাল উৎপাদনের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। ওরা এত দেরি করে পরিসংখ্যান দেয়, যখন এর কোনো কার্যকারিতা থাকে না। এর ওপর ভিত্তি করে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন পরিসংখ্যান নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। বর্তমানে দুধ, মাংস ও মাছের বার্ষিক উৎপাদন যথাক্রমে ১৪১, ৮৮ ও ৪৯ লাখ মেট্রিক টন। ডিমের উৎপাদন দুই হাজার ৩৩৮ কোটি। গত ১৫ বছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে দুধের ক্ষেত্রে বার্ষিক ১২ শতাংশ, মাংসের ক্ষেত্রে ১৩ শতাংশ, ডিমের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ এবং মাছের ক্ষেত্রে সাড়ে ৩ শতাংশ। পণ্যের উৎপাদনে এত বেশি প্রবৃদ্ধি যখন হয়, তখন পণ্যমূল্য এত বেশি বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক নয়। কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যাড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে প্রদত্ত দৈনিক জনপ্রতি দুধ, মাংস, ডিম ও মাছ ভক্ষণের পরিসংখ্যানের সঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের মিল নেই। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) মোট দুধ উৎপাদনের যে হিসাব দিচ্ছে, সে অনুযায়ী দৈনিক জনপ্রতি দুধের প্রাপ্যতা ২২৫ গ্রাম। অথচ বিবিএসের তথ্য মতে, জনপ্রতি দুধের ভোগ মাত্র ৩৪ গ্রাম। ডিএলএসের তথ্য মতে, মাংসের প্রাপ্যতা জনপ্রতি ১৪০ গ্রাম, ডিম ১৯ গ্রাম, মাছ ৭৯ গ্রাম এবং মাছ-মাংস মিলে ২১৯ গ্রাম। বিবিএসের তথ্য মতে, মাংসের ভোগ ৪০ গ্রাম, ডিম ১৩ গ্রাম, মাছ ৬৮ গ্রাম এবং মাছ-মাংস মিলে ১০৮ গ্রাম। দুটি পরিসংখ্যানের মধ্যে বিশাল ফারাক।
ডিএলএসের তথ্যে মনে হয়, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন জাতীয় চাহিদার একান্ত কাছাকাছি, যা খুবই ভালো। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এসব পণ্যের দাম এত বেশি কেন? পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যখন ডিমের দাম বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি পিস ছয় টাকা, তখন সেটি এখানে ১৪-১৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। দুধের দাম পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বেশি। বর্তমানে প্যাকেটজাত দুধ প্রতি লিটার ১০০ টাকা, প্রায় এক ডলার। এটি বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বেশি। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে উৎপাদন খরচ আমাদের চেয়ে অর্ধেক। তারা সারা বিশ্বে সরবরাহ করছে দুধ। ডিম, মাছ ও মাংসের উৎপাদন খরচও বাংলাদেশে বেশি। ব্রাজিল ৫০০ টাকার কমে এক কেজি মাংস বাংলাদেশে সরবরাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাহলে তাদের উৎপাদন খরচ আরো কম। আর বাংলাদেশে ৮০০ টাকার বেশি দামে প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের উৎপাদন খরচ কমানোর উপায় হচ্ছে দক্ষভাবে আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা। প্রডাকশন স্কিল বাড়ানো। সে জন্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা দরকার।
বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রদানের রাষ্ট্রীয় সংস্থা হচ্ছে বিবিএস। এই সংস্থাটির কাছ থেকে সঠিক পরিসংখ্যান প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু সংস্থাটির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব না-ও হতে পারে। সে কারণে সংস্থাটিকে একটি স্বতন্ত্র ও প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাঁদের কাজের দক্ষতা বাড়াতে হবে। নির্মোহভাবে কাজ করে তাঁদের জাতির সামনে সঠিক পরিসংখ্যান উপস্থাপনে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। বিভ্রান্তিকর, অতি মূল্যায়িত ও অবমূল্যায়িত তথ্য প্রদান থেকে তাঁদের বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় সঠিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।
লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ
সম্পর্কিত খবর
রাজনীতিতে জনসমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর
- ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো পুরোপুরি ঐক্য দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর যথেষ্ট টানাপড়েন দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। তা ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।
নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রধান কাজ।
নির্বাচন কখন হবে, কিভাবে হবে—এ বিষয়ে নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মতামত এবং অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনীতিতে তারা এখন বিশেষ ফ্যাক্টরে পরিণত হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র-তরুণদের এই দলটি আলাদা ধরনের গুরুত্ব বহন করছে বলে পরিষ্কার ধারণা করা যায়।
এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় ১১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত নির্বাচনের যেমন সুস্পষ্ট রোডম্যাপ সরকারের পক্ষ থেকে আসেনি, ঠিক তেমনি কোনো রাজনৈতিক দলও তাদের জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক রোডম্যাপ যথাযথভাবে ঘোষণা করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো ভিশন আমাদের সামনে সুনির্দিষ্টভাবে উত্থাপিত হয়নি। এমনকি এনসিপি যে জুলাই পদযাত্রা করছে, সেটি জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলেও কম সময়ে সারা দেশের মানুষের সঙ্গে যথাযথ মিথস্ক্রিয়া করতে পারছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এরই মধ্যে জামায়াত একটি জাতীয় সমাবেশ করে আগামী দিনে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে। অন্যদিকে বিএনপিও নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে অপেক্ষাকৃত দ্রুততম সময়ে নির্বাচনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ আমরা জানি, যেকোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা। এ ক্ষেত্রে জনগণ যেভাবে চায়, ঠিক সেভাবেই তাদের কাজ করতে হয়।
নির্বাচনের দিন-তারিখ ঠিক হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তা-ও কিন্তু নয়। রাজনীতিতে টানাপড়েন বাড়তে থাকলে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাও বাড়তে থাকবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে সব পক্ষকে একটি যথাযথ এবং ন্যায্য দিকে হাঁটতে হবে। কারণ যথাযথ রাস্তায় হাঁটতে না পারলে কোনোভাবেই দেশে ইতিবাচক রাজনীতির সূত্রপাত হবে না। এ কারণে প্রয়োজন একটি উইন-উইন পরিস্থিতির। এ ক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক পক্ষকেই বিশেষ ছাড় দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে রাজনীতির মাঠে থাকতে হবে। সব পক্ষ থেকে ছাড় দিতে না পারলে কোনোভাবেই উইন-উইন পরিস্থিতি আশা করা যায় না।
বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পাওয়া রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি শতাধিক নিবন্ধনহীন এবং ব্যক্তিনির্ভর দল রয়েছে। যেসব নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন জমা দিয়েছে, সেগুলোর অনেকগুলোরই কোনো অফিস নেই, আবার অফিস থাকলেও সভাপতির নিজের বাসার ড্রয়িংরুম অফিসের ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছি। এমনকি বেশির ভাগই প্রাথমিক যোগ্যতা পূরণ করতে পারেনি বলে নির্বাচন কমিশন চিঠি দিয়ে জানিয়েছে।
অনেক দল রয়েছে, যেগুলোর সভাপতির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় না। এ ছাড়া বিদ্যমান নিবন্ধিত অনেক দলই সাইনবোর্ডসর্বস্ব রাজনৈতিক দল। নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া আর কারো তেমন জনসমর্থন নেই। বাকি দলগুলোর তেমন একটা জনসমর্থন না থাকলেও দলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড রয়েছে। এদের তৎপরতা দেখা যায় শুধু নির্বাচন মৌসুম এলেই। নির্বাচনের আগে এই দলগুলোর কদর বেড়ে যায়। বড় দলগুলোর সঙ্গে জোটভুক্ত হওয়া, নির্বাচনে মনোনয়ন এবং ক্ষমতা ভাগাভাগির দর-কষাকষি চলে।
যেকোনো রাজনৈতিক দল বৈধ এবং সাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক দলগুলো জোট গঠন করেও ক্ষমতায় আসে এবং আসার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে বিদ্যমান নামসর্বস্ব দলগুলোর কোনো জনসমর্থন নেই।
আমরা আশা করব, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সত্যিকার অর্থেই জনগণের জন্য কাজ করবে। এমনকি সব দল এবং দলের নেতারা সহনশীল হবেন, সংযত হবেন। অতীত বা বিগত দিনগুলোর অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর কল্যাণের রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবেন, যাতে দেশ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ধারায় চলতে পারে, যাতে দেশে কোনো অপশক্তি মাথাচাড়া দেওয়ার মতো অবস্থা ভবিষ্যতে সৃষ্টি না হয়। রাজনীতিতে প্রতিহিংসা এবং পারস্পরিক টানাপড়েন যত কমিয়ে আনা যাবে, ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল হবে। এ ক্ষেত্রে সব পক্ষকে একটি যথাযথ এবং ন্যায্য দিকে হাঁটতে হবে। কারণ যথাযথ রাস্তায় হাঁটতে না পারলে কোনোভাবেই দেশে ইতিবাচক রাজনীতির সূত্রপাত হবে না।
রাজনৈতিক দলগুলোক মনে রাখতে হবে, ভোটের রাজনীতিতে বিজয়ী হওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হলো সাংগঠনিক ভিত্তি এবং জনসমর্থন। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত না হলে এবং জনসমর্থন না থাকলে সেই দল নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে না। প্রসঙ্গত বলতে হয় যে নতুন দলগুলোর উচিত সাধারণ মানুষের জন্য ব্যতিক্রম চিন্তা বা জনমুখী কর্মসূচি নিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বাস্তবতাবিবর্জিত রাজনৈতিক দর্শনের কারণেও অনেক দল মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না। ফলে জনসমর্থনও বাড়ে না, বরং হিংসা-বিদ্বেষ এবং হানাহানির পরিবেশ তৈরি হয়। আর মোটাদাগে ওই সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের ফলাফল নেতিবাচক হয়।
লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আমরা কি কেবল ভোক্তাই থেকে যাব
- আবু তাহের খান

২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদেশ থেকে মোট ৬৩ হাজার ২২৬ মিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। বিপরীতে এ সময়ে পণ্য রপ্তানি হয়েছে মোট ৫১ হাজার ১১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য আমদানি করা বস্ত্রের হিসাব বাদ দিলে নিট রপ্তানির পরিমাণ আরো কম। অন্যদিকে এ সময়ে যা কিছু আমদানি হয়েছে, সেখানে শিল্পে ব্যবহার্য মৌলিক যন্ত্রপাতির অংশ মাত্র ৪.১৫ শতাংশ; অর্থাৎ আমদানির বেশির ভাগ জুড়েই রয়েছে ভোগ্যপণ্য।
শিল্পপণ্যের নামে রপ্তানি করা আরএমজি পণ্য আসলে তেমন যন্ত্রনির্ভর পণ্য নয়, এর প্রায় পুরোটাই হচ্ছে এ দেশের গরিব-দুঃখী নারীর হাতের নিপুণ দক্ষতায় তৈরি অযান্ত্রিক পণ্য। এই অবস্থায় বলা যেতে পারে, আমরা হচ্ছি এমন একটি ভোক্তা জনগোষ্ঠী, যারা সারাক্ষণ অন্যের কাছ থেকে ধারদেনা করে হলেও উচ্চমূল্যের ভোগ্যপণ্য আমদানি ও ব্যবহার করে এমন ধারার জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যেটিকে মহাজনি আমলের দাদন প্রথার সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যেতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার, জনগণের মধ্যকার এই অভ্যস্ততা বস্তুত রাষ্ট্রই তৈরি করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মহাজনি দাদন ব্যবস্থার আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে বৈদেশিক ঋণের কিস্তি বাবদ বাংলাদেশকে পরিশোধ করতে হয়েছে প্রায় ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার।
আসলে আমাদের বোধ ও চিন্তায় উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের তেমন কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বাসনা নেই। আমরা সারাক্ষণ শুধু তাকিয়ে থাকি উন্নত বিশ্বের দিকে। তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা হিসেবে নিজেদের কপট বাহাদুরি করে যাই।
গত ৫৪ বছরের সরকারগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ভোক্তা রাষ্ট্র হিসেবে আটকে রেখেছে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একে উৎপাদক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি। ১৯৯০-পরবর্তী গত ৩৫ বছরের মধ্যে গঠিত সরকারগুলো দেশে মোট ছয়টি শিল্পনীতি (১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০৫, ২০১০, ২০১৬ ও ২০২২) প্রণয়ন করেছে।
উল্লিখিত শিল্পনীতিগুলোতে সেবা খাতকে শিল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিনিয়োগকারীরা তুলনামূলকভাবে কঠিনতর, সময়সাপেক্ষ ও অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদন শিল্প ছেড়ে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকেছেন। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে উৎপাদন শিল্পের হিস্যা ক্রমেই আরো সংকুচিত হয়ে পড়বে। রাষ্ট্রের এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণে এ দেশের শিল্পোদ্যোক্তারা ৩৫ বছরে ধরে কিভাবে ঘাটে ঘাটে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন এবং সেবা খাত হয়ে উঠেছে অর্থনীতির সাময়িক কৌশলের মূলধারা।
শুধু ভোক্তাপ্রধান অর্থনীতির দেশ হয়ে না থেকে বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে একটি উদ্ভাবক ও উৎপাদক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শিল্পনীতি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। তবে এ ক্ষেত্রে শিল্পনীতির পাশাপাশি রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি, বাণিজ্যনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার চর্চা এবং সর্বোপরি সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি-কৌশলের বিষয়গুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। দেশে যদি ব্যাবসায়িক পরিবেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি না আসে, তাহলে ভোক্তা থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভাবক ও উৎপাদক হয়ে ওঠার কাজটি ঘটাবে কারা?
মোটকথা, সৃজনশীল উদ্ভাবক ও উৎপাদক হওয়ার লক্ষ্যে জাতিগত বিকাশ ও এর আত্মমর্যাদার জায়গাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে এ রাষ্ট্র বড়ই উদ্যমহীন। তার পরও আমরা আশাবাদী যে শিগগির না হলেও একসময় এ রাষ্ট্র অবশ্যই উদ্ভাবক ও উৎপাদকের রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং শুধু ভোক্তা হয়ে থাকার গ্লানি থেকে আমাদের মুক্তি ঘটবে।
লেখক : সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
শিল্প মন্ত্রণালয়
আফ্রিকার মুক্তির সংগ্রাম ও ইব্রাহিম ত্রাওরে
- মাহবুব আলম
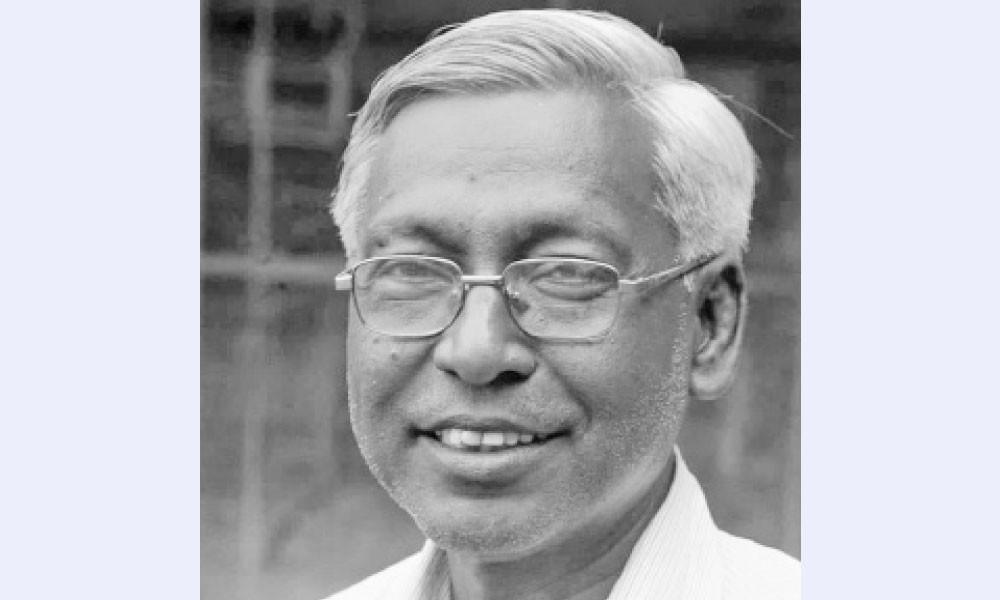
ক্ষুধা, রোগ আর বেকারত্বে জর্জরিত পশ্চিম আফ্রিকার একটি হতদরিদ্র দেশ বুরকিনা ফাসো প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ত্রাওরের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে এক সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলের পর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে ত্রাওরে ঘোষণা করেন, বুরকিনা ফাসোকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করা হবে। সামাজ্যবাদের শিকড় উপড়ে ফেলা হবে। সেই সঙ্গে হতদরিদ্র মানুষকে দুমুঠো খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।
 ২০২২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫-এর জুলাই তিন বছরেরও কম সময়ে বুরকিনা ফাসোর দারিদ্র্য কিছুটা হলেও কমেছে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বাড়লেও ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৪ সালে চরম দারিদ্র্য ২ শতাংশ কমেছে।
২০২২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫-এর জুলাই তিন বছরেরও কম সময়ে বুরকিনা ফাসোর দারিদ্র্য কিছুটা হলেও কমেছে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বাড়লেও ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৪ সালে চরম দারিদ্র্য ২ শতাংশ কমেছে।
ইব্রাহিম ত্রাওরের নেতৃত্বে বুরকিনা ফাসোর এই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে শক্তিধর ফ্রান্সকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনায় তিনি বুরকিনা ফাসোসহ সমগ্র আফ্রিকার মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। জয় করেছেন সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোর মানুষের হৃদয়ও। তাইতো ত্রাওরের সাহসী পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারাও তাদের দেশ থেকে একে একে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি উচ্ছেদ করতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে মালি ও নাইজার থেকে ফরাসি ও মার্কিন সামরিক ঘাঁটি উচ্ছেদ করা হয়েছে। এসব ঘটনায় ত্রাওরে আফ্রিকায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই জনপ্রিয়তার শুরু হয় ২০২৩ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে আফ্রিকা-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে এক ভাষণের মধ্য দিয়ে। ওই ভাষণে আফ্রিকার নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘প্রতিবার সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের ঘোরানো ছড়ির ইশারায় পুতুলের মতো নাচা বন্ধ করুন।’ তাঁর ওই বক্তব্য রাশিয়ান গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়। ত্রাওরেকে আফ্রিকার নেতা হিসেবে তুলে ধরতে ওই প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব ঘটনায় ত্রাওরে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক আপসহীন সৈনিক হিসেবে।
ত্রাওরের অনুসারীরা তাঁকে বুরকিনা ফাসোর মার্ক্সবাদী বিপ্লবী আফ্রিকার চে হিসেবে পরিচিত টমাস সানকারার যোগ্য উত্তরসূরি বলে মনে করে। ত্রাওরে নিজেও বলেন, ‘সানকারা আমার নেতা।’ তাইতো তিনি সানকারার কবরের ওপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য একটি মেগাপ্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। বিবিসির এক প্রতিবেদনেও ত্রাওরেকে সানকারার উত্তরসূরি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কন্ট্রোল রিস্কের এক সিনিয়র গবেষক বেভারলি ওচিং বিবিসিকে বলেছেন, ‘ত্রাওরের প্রভাব অনেক। আমি কেনিয়া থেকেও রাজনীতিক ও লেখকদের বলতে শুনেছি, এইতো সেই মানুষ, যাকে আমরা খুঁজছিলাম।’
আফ্রিকার মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এরই মধ্যে তা প্রমাণিত। সর্বশেষ অর্থাৎ অতি সম্প্রতি নিজস্ব মুদ্রানীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। তিনি শুধু বুরকিনা ফাসো নয়, পুরো আফ্রিকার মুক্তি চান। চান সত্যিকার স্বাধীনতা। তিনি বলেছেন, ‘যে দেশের নিজস্ব মুদ্রা নেই, সেই দেশ কিসের স্বাধীন? আমরা আমাদের মুদ্রা ছাপব। আমরা স্বাধীন হব।’ উল্লেখ্য, পশ্চিম আফ্রিকার সাবেক ১৪টি ফরাসি ঔপনিবেশিক দেশের নিজস্ব মুদ্রা নেই। তারা ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী আমলের চালু করা সিএফএ মুদ্রা ব্যবহার করে। এই মুদ্রা ছাপা হয় প্যারিসে ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে। মুদ্রামানও ঠিক করে ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ব্যাংক। শুধু তা-ই নয়, রিজার্ভ জমা থাকে ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ব্যাংকে। এখানেই শেষ নয়, পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনও হয় ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাধ্যমে। এই ঔপনিবেশিক অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে বুরকিনা ফাসো নিজস্ব মুদ্রা ছাপাতে শুরু করেছে। এককথায় ত্রাওরে নিজের পথে হাঁটছেন। এই পথে আফ্রিকার দেশগুলোকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করছেন। এমনকি সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোর অভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছেন। প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বুরকিনা ফাসো, মালি ও ঘানাকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনের কাজ। সম্প্রতি তিনি আন্তর্জাতিক লা ফ্রাংকোফোনি থেকেও বুরকিনা ফাসোকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
ইব্রাহিম ত্রাওরে যে দুর্দান্ত সাহসী ও ঠাণ্ডা মাথার তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন তেজোদীপ্ত মানুষ, তার প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায়। ঘটনাটি হলো, ফ্রান্সের মালিকানাধীন দুটি স্বর্ণখনি জাতীয়করণের পর হঠাৎ করে ত্রাওরের ১৪ বছরের ছোট বোন আমানাতার স্কুল থেকে ফেরার পথে উধাও হয়ে যায়। এই ঘটনায় বাকরুদ্ধ ত্রাওরে গোয়েন্দাপ্রধানসহ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করে জানতে পারেন আমানাতার আসার পথের সব সিসি ক্যামেরা একসঙ্গে বিকল হয়ে যায়। এতে তার অপহরণের বিষয়টি তিনি নিশ্চিত হন। কিন্তু এই বিষয়টি তিনি চেপে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এটি কোনো সাধারণ অপহরণ নয়। প্রেসিডেন্টের বোন, এটি জেনেবুঝেই অপহরণ। তাই তিনি মুক্তিপণের দাবিতে টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর বাড়ির সব টেলিফোন কল বিশ্লেষণ ও ট্র্যাক করার মতো বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেন। যা হোক, তিন দিন পর ফোন আসে। ফোন ধরেন ত্রাওরে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয়, ‘তোমার বোন সুস্থ আছে, ভালো আছে। বোনকে সুস্থ অবস্থায় পেতে হলে স্বর্ণখনি জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। সেই সঙ্গে চীনের সঙ্গে ইউরেনিয়াম চুক্তির আলোচনাও বাতিল করতে হবে। সময় ৭২ ঘণ্টা। এরপর তোমার বোন আর দশজন সুন্দরী তরুণীর মতোই ইউরোপীয় পুরুষদের সেবা দেবে। বয়স কম অনেক দিন সেবা দিতে পারবে।’ এই কথা বলে ফোনের লাইন কেটে দেওয়া হয়। ফোনকল বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দারা ধরে নেন কলটি এসেছে আমস্টারডাম থেকে। ত্রাওরে সিদ্ধান্ত নেন তিনি তাঁর বোনসহ আফ্রিকান মেয়েদের উদ্ধারে এক সিক্রেট মিশন চালাবেন আমস্টারডামে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ১৮ জন গোয়েন্দার এক চৌকস দল পাঠানো হয় পর্যটকের বেশে। সেই সঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করে পুরো বিশ্বকে জানালেন তাঁর ১৪ বছরের ছোট বোন আমানাতার অপহৃত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাকে কোথায় রাখা হয়েছে। এর বেশি আর একটি কথাও নয়। উদ্ধার মিশন সফল হয় মাত্র ছয় দিনে। গোয়েন্দারা আমানাতারসহ ৪৭ জন আফ্রিকান তরুণীকে উদ্ধার করেন। সেই সঙ্গে বিপুল নথিপত্রসহ ২৩ জন মানব পাচারকারীকে ধরে ফেলেন। এই ঘটনায় ইউরোপে ছি ছি পড়ে যায়। আর আফ্রিকায় ত্রাওরে বিপুল প্রশংসায় ভাসেন। বুরকিনা ফাসোর মতো একটি দরিদ্র দেশ ইউরোপের একটি দেশে সিক্রেট মিশন চালাতে পারে, এটি যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।
এই হলেন ইব্রাহিম ত্রাওরে। সাম্রাজ্যবাদের ত্রাস তাঁর মজলুম জনতার প্রিয়জন। তাইতো তিনি আফ্রিকার মুক্তিকামী তরুণদের হৃদয় জয় করেছেন। এবার দেখা যাক, তিনি আফ্রিকার মানুষের মুক্তির লড়াইকে কত দূর এগিয়ে নিতে যেতে পারেন। যদি পারনে, তাহলে তিনিই হবেন আফ্রিকার সর্বকালের সেরা নেতা।
লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট
ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন কতটা কার্যকর
- ড. কবিরুল বাশার

পৃথিবীর উষ্ণতম অঞ্চলের দেশগুলোতে মশাবাহিত রোগে প্রতিবছর লাখ লাখ লোক আক্রান্ত হয় এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ মারা যায়। বাংলাদেশে ২০০০ সালে প্রথম ডেঙ্গুর বড় আঘাতের পর থেকে প্রায় প্রতিবছরই বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যায়। প্রায় প্রতিবছরই দেখা যায় আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সরকারি পরিসংখ্যানে রোগীর যে সংখ্যা দেখানো হয়, তা ঢাকার মাত্র ৭৭টি হাসপাতাল এবং অন্যান্য জেলার অল্পকিছু হাসপাতালের তথ্য।
পৃথিবীর ১২৯টি দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলেও এর ৭০ শতাংশই এশিয়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে যে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এবার ডেঙ্গুঝুঁকিতে থাকবে।
 পৃথিবীতে প্রতিবছর গড়ে পাঁচ লাখ মানুষ ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং এর মধ্যে ৪০ হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীব্যাপী মশা নিয়ন্ত্রণই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়।
পৃথিবীতে প্রতিবছর গড়ে পাঁচ লাখ মানুষ ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং এর মধ্যে ৪০ হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীব্যাপী মশা নিয়ন্ত্রণই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়।
এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নির্ভর করে ব্যক্তির পূর্ববর্তী ডেঙ্গু সংক্রমণের ওপর। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি আগে ডেঙ্গু ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে (seropositive), তাদের মধ্যে Dengvaxia প্রায় ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ কার্যকারিতা দেখিয়েছে। তবে যেসব ব্যক্তি আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়নি, তাদের মধ্যে ভ্যাকসিন গ্রহণের পর গুরুতর ডেঙ্গু ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ Dengvaxia শুধু আগে ডেঙ্গু আক্রান্তদের জন্য ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। এ জন্য এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের আগে সেরোলজিক্যাল পরীক্ষা করতে হয়, যা বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।Qdenga, যার বৈজ্ঞানিক নাম TAK-003, জাপানের ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Takeda Pharmaceutical Company-এর তৈরি একটি নতুন প্রজন্মের ডেঙ্গু ভ্যাকসিন। এটি Dengvaxia-এর তুলনায় অনেকটাই সহজ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক উপযোগী।
Qdenga-ও একটি লাইভ-অ্যাটেনুয়েটেড টেট্রাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, তবে এটি দুই ডোজে দেওয়া হয় এবং আগে ডেঙ্গু হোক বা না হোক, সেই বিবেচনা না করেই ব্যবহার করা যায়। এটি হলো এর সবচেয়ে বড় সুবিধা।
Qdenga-এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল মূলত লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার উচ্চঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে সম্পন্ন হয়। ফেজ-৩ ট্রায়ালে দেখা গেছে, ভ্যাকসিনটি প্রথম দুই বছরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রায় ৮০ শতাংশ কার্যকারিতা দেখিয়েছে। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, হাসপাতালভিত্তিক গুরুতর ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে এর কার্যকারিতা ছিল প্রায় ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত। এ ছাড়া এটি seronegative ও seropositive উভয় শ্রেণির মানুষের জন্যই নিরাপদ প্রমাণিত হয়েছে। ফলে এটি বৃহৎ পরিসরে প্রয়োগের উপযোগী। বর্তমানে Qdenga ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে অনুমোদনপ্রাপ্ত। ২০২৪ সালের মে মাসে WHO Qdenga-কে ‘prequalified vaccine’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা এর ক্রয় এবং ব্যবহারের পথ সুগম করে। Qdenga শিশু ও কিশোরদের (চার বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী) মধ্যে প্রয়োগযোগ্য। এর কোনো আগে serological পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই, যা বাংলাদেশের মতো দেশে এই ভ্যাকসিনকে বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে DENV-3 ও DENV-4 টাইপ ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হতে পারে। তা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার বিষয়ে আরো পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এ ছাড়া ভ্যাকসিনের মূল্য এবং সরবরাহব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।
বাংলাদেশে ডেঙ্গু ভ্যাকসিন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন—ভ্যাকসিনগুলোর দাম, প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ ও সরবরাহ চেইন, সঠিক বয়সভিত্তিক টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ ইত্যাদি। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও মশা নিয়ন্ত্রণ ও জনসচেতনতা না থাকলে সংক্রমণ পুরোপুরি বন্ধ হবে না। বিশেষ করে ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ ও অপরিকল্পিত নগরায়িত এলাকায় শুধু ভ্যাকসিন কার্যক্রম যথেষ্ট নয়, বরং এটি অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিপূরক হতে হবে।
ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভ্যাকসিন আমদানি এবং প্রয়োগ করবে কি না, সেটি নানা মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে। একজন পরিবেশ-জনস্বাস্থ্য গবেষক হিসেবে আমি মনে করি, এটির আমদানি এবং প্রয়োগের আগে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, যারা এটি প্রয়োগ শুরু করেছে, তাদের কাছ থেকে এর ফলাফল এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন।
সর্বশেষে বলা যায়, ডেঙ্গু ভ্যাকসিন বাংলাদেশের ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে, বিশেষ করে Qdenga যদি দ্রুত অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়। তবে এর সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা, লক্ষ্যভিত্তিক প্রয়োগ কৌশল, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত পদক্ষেপ এবং জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি। একই সঙ্গে জোর দিতে হবে মশার বংশবিস্তার রোধ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর। একমাত্র সম্মিলিত প্রয়াসই পারে ডেঙ্গুর মতো জটিল ও ক্রমবর্ধমান রোগকে টেকসইভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে।
লেখক : অধ্যাপক, কীটতত্ত্ববিদ ও পরিবেশ-জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
professorkabirul@gmail.com

