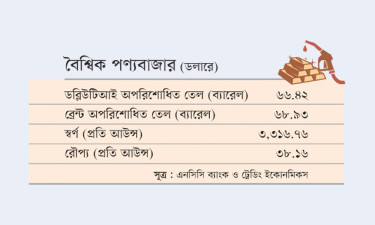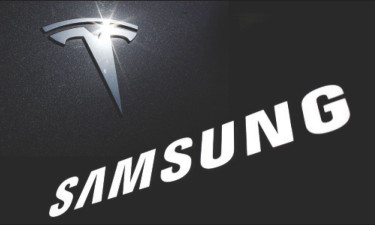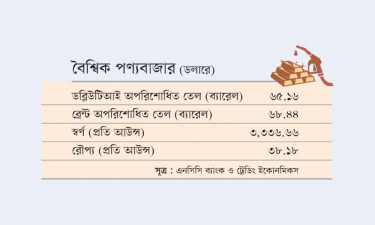বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষ করে মার্কিন ডলার সংগ্রহের যতগুলো মাধ্যম আছে, তার মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড (ওয়েজ আর্নার্স বন্ড) অন্যতম। কেননা দেশে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের অন্যান্য যেসব পন্থা আছে, যেমন—রপ্তানি আয়, বৈদেশিক রেমিট্যান্স এবং বৈদেশিক ঋণ, এর সবগুলোর বিপরীতে তাত্ক্ষণিক ব্যয় থাকে। অর্থাৎ এসব উৎস থেকে একদিকে ডলার সংগ্রহ করা হয় এবং অন্যদিকে সেই ডলার আমদানিমূল্য ও ঋণ পরিশোধসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় হয়ে যায়। সেদিক থেকে ওয়েজ আর্নার্স বন্ড কিছুটা ভিন্ন।
ডলার সংকটেও ওয়েজ আর্নার্স বন্ড নিয়ে বিড়ম্বনা
- নিরঞ্জন রায়

ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের মাধ্যমে সরকারের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। প্রথমত, এই বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় প্রবাসীরা তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠাতে আগ্রহী থাকে। দ্বিতীয়ত, এই বন্ডের আসল অর্থ যেহেতু মেয়াদপূর্তিতে পুনরায় ডলারে রূপান্তর করে বিদেশে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই অনেকেই, বিশেষ করে যেসব প্রবাসী স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাস করে, তারা এই বন্ডে বিনিয়োগ করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখায়।
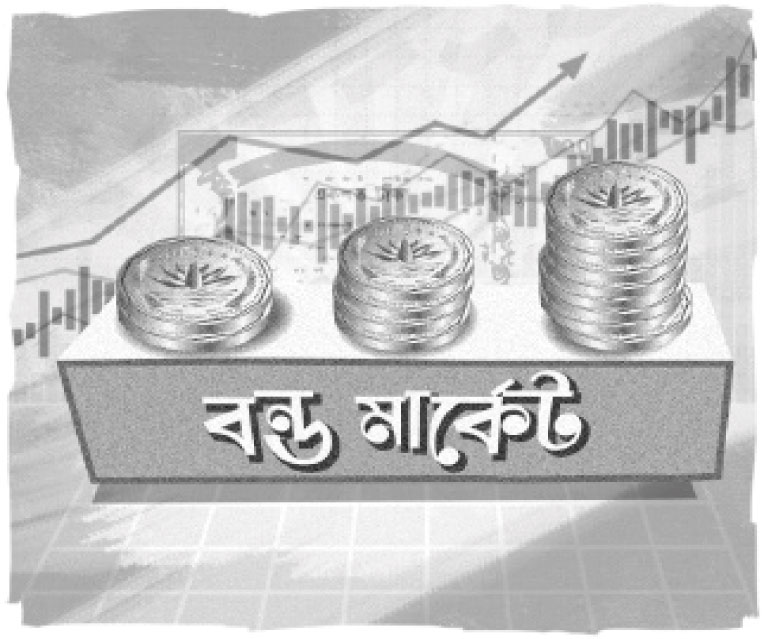 এ রকম একটি বিশেষ সুবিধাসংবলিত ওয়েজ আর্নার্স বন্ড যতটা জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল এবং যেভাবে ব্যাপক হারে এই বন্ডে প্রবাসীদের ডলার বিনিয়োগ করার কথা ছিল, তেমনটা হয়নি। এর অনেক কারণও আছে। প্রথমত, এটি যে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ এক বিনিয়োগ ব্যবস্থা, সে ব্যাপারে তেমন প্রচার-প্রচারণা নেই বললেই চলে।
এ রকম একটি বিশেষ সুবিধাসংবলিত ওয়েজ আর্নার্স বন্ড যতটা জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল এবং যেভাবে ব্যাপক হারে এই বন্ডে প্রবাসীদের ডলার বিনিয়োগ করার কথা ছিল, তেমনটা হয়নি। এর অনেক কারণও আছে। প্রথমত, এটি যে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ এক বিনিয়োগ ব্যবস্থা, সে ব্যাপারে তেমন প্রচার-প্রচারণা নেই বললেই চলে।
আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ডলারের বিনিময় মুল্য যখন ৮০ টাকা ছিল তখন সরকার একজন প্রবাসীর কাছ থেকে এক লাখ ডলার ক্রয় করে ৮০ লাখ টাকার ওয়েজ আর্নার্স বন্ড ইস্যু করেছে। এখন যখন সেই বন্ড মেয়াদ পূর্ণ করেছে তখন দেশে ডলারের বিনিময় মূল্য ১২০ টাকা এবং সে অনুযায়ী বন্ডের আসল অর্থ ৮০ লাখ টাকার বিনিময়ে ডলারের বর্তমান বিনিময় মূল্য অনুযায়ী ৬৭ হাজার ডলার। এই পাঁচ বছর সময়ে সরকারের এক্সচেঞ্জ গেইন হবে ১৩ হাজার ডলার, যা বর্তমান বিনিময় মূল্য অনুযায়ী ১৬ লাখ টাকা। বন্ডের পাঁচ বছর মেয়াদকালে সরকার টাকায় সুদ প্রদান করবে ৪৮ লাখ টাকা যদি বন্ডের ওপর সুদের হার ১২ শতাংশ হয়। বিনিময় লাভ বিবেচনায় নিলে সরকার ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের ওপর প্রকৃত সুদ প্রদান করবে ৩২ লাখ টাকা। পক্ষান্তরে যদি ওয়েজ আর্নার্স বন্ডে বিনিয়োগের পরিবর্তে সরকারি সঞ্চয়পত্রে এই ৮০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে রাখা হয় এবং সঞ্চয়পত্রের ওপর যদি সুদের হার হয় ১০ শতাংশ, তাহলে সরকারকে সুদ দিতে হবে ৪০ লাখ টাকা। অর্থাৎ এক লাখ ডলারের ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের ওপর প্রদত্ত প্রকৃত সুদ সমপরিমাণ সঞ্চয়পত্রের চেয়ে আট লাখ টাকা কম হবে।
পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে আলোচ্য উদাহরণে চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিবর্তে সরল সুদ ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে পরিমাণটা বেশি হবে, কিন্তু পার্থক্যের পরিমাণ এ রকমই থাকবে। এ কারণেই দেখা যায় সঞ্চয়পত্রের পরিবর্তে ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের ওপর সরকার প্রকৃত সুদ কম প্রদান করে থাকে। আলোচ্য উদাহরণে যে বিনিময় হারের পতন দেখানো হয়েছে তা খুবই অস্বাভাবিক, যা বিশেষ কারণ ছাড়া সাধারণত হয় না। যেমনব-এখন হয়েছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ডলার হার্ড কারেন্সি হয়ে যাওয়ায়। কিন্তু স্বাভাবিক সময়েও টাকার যে অবমূল্যায়ন ঘটে, সেটি বিবেচনায় নিলেও সরকার ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের চেয়ে সঞ্চয়পত্রের ওপর প্রকৃত সুদ অনেক বেশি প্রদান করে থাকে। এ কারণে প্রবাসীদের বিনিয়োগ করা ওয়েজ আর্নার্স বন্ড যত দিন পর্যন্ত পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া যায়, ততই সরকারের লাভ। এটি জানা সত্ত্বেও সরকার এই ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে। এখন থেকে বিনিয়োগের পর সর্বোচ্চ দুইবারের জন্য ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগ করা যাবে।
ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগের পথ বন্ধ করে দিলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। প্রথমত, দেশের ডলার সংকটের মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত ডলারের চাহিদা বাড়িয়ে দেবে এবং সংকট কিছুটা হলেও তীব্র হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ওয়েজ আর্নার্স বন্ড যখন পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে না, তখন বন্ডের বিনিয়োগকারীর সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে। বন্ডের অর্থ ডলারে রূপান্তর করে বিদেশে নিয়ে যাওয়া এবং এর ফলে দেশ থেকে ভালো অঙ্কের ডলার বিদেশে চলে যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে এই বন্ডের টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সরকারের এমন কী লাভ হবে তা আমাদের কাছে মোটেই বোধগম্য নয়। কেননা এতে সরকারকে প্রকৃত সুদ বেশি দিতে হবে, যা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, অনেক প্রবাসী যখন জানবে যে ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে, তখন তারা এই বন্ডে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এর ফলে দেশে ডলার আসা যে অনেকটা হ্রাস পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে বর্তমানে এই খাতে বিনিয়োগ করা ডলার ধরে রাখা যেমন সম্ভব হবে, তেমনি এই বন্ডে নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিত করে দেশের ডলার সরবরাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করার সুযোগ থাকবে।
এ রকম বাস্তবতায় বিশেষ করে দেশ যেহেতু ডলার সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঠিক সেই সময়ে ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত করার পদক্ষেপ মোটেই যুক্তিসংগত এবং বাস্তবসম্মত হয়নি। তা ছাড়া এতে সরকারের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। যদি তর্কের খাতিরে এক্সচেঞ্জ গেইনের মতো জটিল বিষয়টি সরিয়ে রেখে সোজাসুজি ধরে নিই যে উচ্চ সুদের হারই ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত করার পেছনে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সে ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের ওপর সুদের হার হ্রাস করে সঞ্চয়পত্রের ওপর প্রদত্ত সুদের হারের সমান করে দেওয়া যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো যে ওয়েজ আর্নার্স বন্ডের সুদ যেহেতু টাকায় প্রদান করা হয়, তাই এই বন্ডের ওপর এবং সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয়ের তেমন কোনো তারতম্য নেই। অবশ্য যারা নতুন ওয়েজ আর্নার্স বন্ডে বিনিয়োগ করবে, তাদের উৎসাহিত করার স্বার্থে শুরুতে উচ্চ সুদ প্রদান করলেও তৃতীয়বারের বেশি পুনর্বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রের সমান সুদ প্রদান করা যেতে পারে। মোটকথা যেকোনোভাবেই হোক না কেন, এই ওয়েজ আর্নার্স বন্ড পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত না করে অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ওয়েজ আর্নার্স বন্ড নতুনভাবে ক্রয় এবং পুনর্বিনিয়োগের পদ্ধতি যথেষ্ট সহজ করা প্রয়োজন। এমনটা করতে পারলে দেশ এবং প্রবাসী উভয়ই উপকৃত হতে পারবে। সেই সঙ্গে ডলার সংকট নিরসনে ওয়েজ আর্নার্স বন্ড কিছুটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আশা করি, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়টি ভেবে দেখবে।
লেখক : সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা
সম্পর্কিত খবর
ড. ইউনূসের তিন শূন্য তত্ত্ব ও যুবকল্যাণ
- ড. মো. ফখরুল ইসলাম

বাংলাদেশে তরুণ জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বড় জনশক্তি। কিন্তু বেকারত্ব তাদের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রস্তাবিত ‘থ্রি জিরোস’ বা তিন শূন্য তত্ত্ব হলো—শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বন নিঃসরণ। এখানে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে তরুণরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হতে পারে।
বিশ্ব যখন বৈষম্য, জলবায়ু সংকট ও বেকারত্বের সংকটে দিশাহারা, তখন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রস্তাবিত থ্রি জিরোস তত্ত্ব একটি আশাবাদের বাতিঘর মনে করা যেতে পারে। এই তত্ত্বের ভিত্তি মূলত একটি সামাজিক ব্যবসার কাঠামোতে দাঁড়িয়ে, যার উদ্দেশ্য মুনাফা নয়, মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান।
ড. ইউনূস মনে করেন, দারিদ্র্য দূরীকরণ কোনো দান-খয়রাতের বিষয় নয়, এটি সক্ষমতা ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতির মাধ্যমে সমাধানযোগ্য। মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি এর অন্যতম হাতিয়ার, যা গরিব মানুষকে ভিক্ষুক নয়, বরং উদ্যোক্তা করতে সাহায্য করে।
তিনি আরো মনে করেন, শূন্য বেকারত্ব ধারণা চাকরি নয়, উদ্যোক্তা তৈরি করে। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, কেবল প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ ও উৎসাহের।
জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, এটি বর্তমানের বাস্তবতা। বাংলাদেশ এই দুর্যোগের অন্যতম শিকার। অথচ আমরা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নই। ইউনূস অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, এমন একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই হবে পরিবেশবান্ধব সমৃদ্ধি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সবুজ কৃষি ও কার্বন নিরপেক্ষ সামাজিক ব্যবসা হতে পারে এর অন্যতম চালিকাশক্তি।
কথা হচ্ছে, এই তত্ত্ব কেন এখন জরুরি মনে করা হচ্ছে? কারণ ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের ১ শতাংশ ধনীর হাতে বৈশ্বিক সম্পদের ৪৪ শতাংশের বেশি জমা হয়েছে। একই সঙ্গে পৃথিবীতে প্রতি ১০ সেকেন্ডে একজন শিশু অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে, প্রতি মিনিটে একজন যুবক বেকারত্বে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করছে। এই প্রেক্ষাপটে থ্রি জিরোস তত্ত্ব কেবল একটি আদর্শিক আহবান নয়। এটি সময়োপযোগী প্রণীত এবং প্রয়োগযোগ্য একটি বিকল্প উন্নয়ন মডেল। তাই ইউনূস সেন্টারের মাধ্যমে ৫০টিরও বেশি দেশে সামাজিক ব্যবসার প্রকল্প চলছে।
বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা বড় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে। তা হলো শিক্ষিত বেকারত্বের ভয়াবহ বিস্তার। প্রতিবছর প্রায় ২২ লাখ নতুন কর্মক্ষম মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, যার বড় অংশই উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পাস। কিন্তু তাদের অনেকেই কোনো উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছে না। সরকারি চাকরি সীমিত, বেসরকারি খাতে অনিশ্চয়তা, আর নিজের কিছু শুরু করার সাহস ও সহায়তার অভাবে তরুণরা হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় ইউনূস প্রস্তাবিত এই তত্ত্বে বেকার তরুণরা আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।
ড. ইউনূস মনে করেন, বেকারত্ব কোনো ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, বরং এটি একটি কাঠামোগত সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। অথচ প্রতিটি তরুণের মাঝেই রয়েছে একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা, যাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিলে সে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে এবং অন্যদেরও দিতে পারে। সোশ্যাল বিজনেস কাঠামো এমন এক ধরনের ব্যবসা, যার লক্ষ্য মুনাফা নয়, সমাজের কোনো সমস্যা সমাধান। যেমন—স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ কিংবা ডিজিটাল সেবা। এমন ব্যবসায় লাভ পুনরায় বিনিয়োগ হয় সমস্যার সমাধানে, মালিক বা উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত মুনাফা তোলে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ গ্রাম থেকে এসেছে। তারা একদিকে যেমন বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো জানে, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়াও পেয়েছে। তাদের হাতে থাকা এই দ্বৈত জ্ঞানই হতে পারে সামাজিক ব্যবসার শ্রেষ্ঠ পুঁজি।
ড. ইউনূস এই মডেলকে ‘জিরো ক্যাপিটাল স্টার্টআপস বাই ইয়ুথ’ নামে ডেকে থাকেন। অর্থাৎ অনেক সময় মূলধন ছাড়াও উদ্যোগ শুরু করা সম্ভব, যদি চিন্তা ও ইচ্ছা থাকে। তবে এই সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়নে রয়েছে একাধিক চ্যালেঞ্জ। এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সোশ্যাল বিজনেস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সরকার ও ব্যাংকগুলোকে যুবকদের সামাজিক ব্যবসার জন্য বিশেষ ঋণ সহায়তা চালু করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্টার্টআপ হাব ও ইনকিউবেশন ল্যাব তৈরি করতে হবে এবং মিডিয়া ও সমাজে চাকরির বাইরেও কর্মজীবনের বিকল্প পথ তুলে ধরতে হবে।
তরুণরা যেন শুধু সিভি লেখার চিন্তায় না থেকে সমাধান লেখার ভাবনায় চলে। এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকার ও সমাজ সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতেই হবে। আমাদের উচ্চশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত লাখ লাখ তরুণ, যুবক চাকরির অভাবে হতাশ, সেখানে সামাজিক ব্যবসা ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশ এই চক্র ভাঙতে পারে।
লেখক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন
fakrul@ru.ac.bd
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তাপ ছড়াচ্ছে থাই-কম্বোডিয়া যুদ্ধ
- ড. সুজিত কুমার দত্ত

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। দেশ দুটির মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ ৮১৭ কিলোমিটার সীমান্ত। এর কিছু অংশ এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যা বারবার দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই পুরনো বিবাদ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যার ফলস্বরূপ ৩০ জনেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে এবং লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সীমান্ত বিরোধের শিকড় প্রোথিত রয়েছে ঔপনিবেশিক ইতিহাসে। ১৯০৭ সালে ফ্রান্স যখন কম্বোডিয়ার ঔপনিবেশিক শাসক ছিল, তখন তারা প্রথম এই অঞ্চলের একটি মানচিত্র তৈরি করে। সেই মানচিত্রটি দুই দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক জলবিভাজিকা রেখা বরাবর সীমান্ত নির্ধারণের একটি চুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।
এই বিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একাদশ শতাব্দীর একটি প্রাচীন মন্দির, প্রিসাহ ভিহার (থাইল্যান্ডে যা খাও ফরা ভিহার নামে পরিচিত)। বহু দশক ধরে ব্যাঙ্কক ও নমপেন উভয়ই এই মন্দিরের ঐতিহাসিক মালিকানা দাবি করে আসছে।
২০০৮ সালে কম্বোডিয়া যখন প্রিসাহ ভিহার মন্দিরকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করে, তখন উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। থাইল্যান্ড এটিকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হিসেবে দেখে।
ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আইনি রায় সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার বর্তমান সরকারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে উষ্ণ। এর একটি বড় কারণ হলো থাইল্যান্ডের সাবেক প্রভাবশালী নেতা থাকসিন সিনাওয়াত্রা এবং কম্বোডিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক দ্বিপক্ষীয় অনেক উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হয়েছে। তবে এই উষ্ণ সম্পর্ক সত্ত্বেও থাইল্যান্ডে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উত্থান দেখা যাচ্ছে, যা নতুন করে সংঘাতের জন্ম দিচ্ছে।
বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক অচলাবস্থা বিরাজ করছে। কম্বোডিয়া জাতিসংঘে একটি বৈঠক এবং যুদ্ধবিরতির আহবান জানিয়েছে। থাইল্যান্ড চায় দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পথকে আরো কঠিন করে তুলছে। আসিয়ান চেয়ার হিসেবে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এই সংকট নিরসনে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিচ্ছেন। যদি আসিয়ান এই সংকট কার্যকরভাবে সমাধান করতে না পারে, তবে এটি জোটের আঞ্চলিক প্রভাব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করতে পারে।
এই সংকট নিরসনে উভয় দেশকেই বুঝতে হবে যে সীমান্ত সংঘাত তাদের অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত বিদেশি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহ করে এবং সীমান্ত এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ব্যাহত করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আসিয়ানের উচিত উভয় পক্ষকে আলোচনার টেবিলে আনা এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা।
থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার জনগণের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে তাদের নেতাদের অবশ্যই জাতীয়তাবাদী আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। সীমান্ত কেবল একটি রেখা নয়, এটি দুই দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত। দুই দেশের উচিত তাদের অভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ খুঁজে বের করা। এটি কেবল থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার জন্যই নয়, বরং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্যও অপরিহার্য।
লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
datta.ir@cu.ac.bd
বাণিজ্যচুক্তি : ভিয়েতনাম পারলে আমরা নয় কেন
- নিরঞ্জন রায়

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই সমগ্র বিশ্বে এক অর্থনৈতিক ঝড় তুলে ফেলেছেন, যার কবলে পড়ে অনেক দেশের অর্থনীতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। এই ক্ষতির শঙ্কা থেকে বাদ যাচ্ছে না বাংলাদেশও। যেসব দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে, তাদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প নির্বিচারে উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করেছেন। এই শুল্ক আরোপের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে অনেক দেশ আমেরিকার বিরুদ্ধেও কিছু বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।
ট্রাম্পের এ রকম বাণিজ্যযুদ্ধ অপ্রত্যাশিত ছিল না মোটেই। অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে এ রকম কিছু একটা করবেন। বিশেষ করে চীনসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে ট্রাম্প উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করবেন, তা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল।
 ট্রাম্পের এ রকম নির্বিচারে শুল্ক আরোপের ফলে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার প্রভাবে ধনী-গরিব-নির্বিশেষে সব দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। তবে ধনী দেশগুলোর ক্ষতির ধরন এবং পরিমাণ ভিন্ন।
ট্রাম্পের এ রকম নির্বিচারে শুল্ক আরোপের ফলে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার প্রভাবে ধনী-গরিব-নির্বিশেষে সব দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। তবে ধনী দেশগুলোর ক্ষতির ধরন এবং পরিমাণ ভিন্ন।
এ কথা ঠিক যে ট্রাম্প একতরফাভাবেই এই বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেছেন। ফলে এই উচ্চহারের শুল্কের প্রভাব যে শুধু আরোপিত দেশের ওপর পড়েছে তেমন নয়, এর প্রভাব আমেরিকার অর্থনীতি এবং ভোক্তাদের ওপরও যথেষ্টই পড়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে আমেরিকার অর্থনীতিতে মন্দা নেমে আসা অস্বাভাবিক ছিল না। এ কারণেই ট্রাম্প উচ্চহারের শুল্ক আরোপের কার্যকারিতা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেন, যাকে অনেকেই বাণিজ্যযুদ্ধবিরতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই ৯০ দিনের বাণিজ্যযুদ্ধবিরতির মেয়াদ গত ৯ জুলাই অতিবাহিত হয়ে গেলে এর মেয়াদ আগস্টের ১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এরপর এই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আবারও বৃদ্ধি পাবে, নাকি অতি শুল্কহার কার্যকর হবে, তা দেখার জন্য আমাদের আরো কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।
ট্রাম্প প্রশাসনের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পেছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশ আলোচনার মাধ্যমে আমেরিকার সঙ্গে একটি গ্রহণযোগ্য বাণিজ্যচুক্তিতে পৌঁছতে পারবে। এর ফলে উচ্চহারের শুল্কের একটি সন্তোষজনক সমাধান হবে এবং বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট বাণিজ্য উত্তেজনা প্রশমিত হবে। কিন্তু যুক্তরাজ্য, চীন ও ভিয়েতনাম ছাড়া আর কোনো দেশই আমেরিকার সঙ্গে উচ্চ শুল্কহারের বিষয়টি সুরাহা করতে পারেনি। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের ব্যাপারটি একেবারেই ভিন্ন। কেননা আমেরিকার সঙ্গে যুক্তরাজ্যের আছে একান্ত বোঝাপড়া। ফলে ব্রিটেন খুব সহজেই ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে শুল্ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে পেরেছে। চীন অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে নয়, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আরোপিত শুল্কহার হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।
আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি বলতে যা বোঝায়, তা ভিয়েতনামই প্রথম করতে সক্ষম হয়েছে। এই চুক্তির কারণে আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকে পণ্য আমদানির ওপর শুল্কহার আগে আরোপিত ৪৬ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। এমনকি ভিয়েতনাম হয়ে অন্যান্য দেশের যে পণ্য রপ্তানি হবে, তার ওপরও শুল্কহার হ্রাস করে ৪০ শতাংশ পুনর্নির্ধারণ করেছে, যা আগে অনেক বেশি ছিল। ভিয়েতনাম হচ্ছে আমেরিকার অষ্টম বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার, যাদের সঙ্গে গত বছর ১৫০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার আছে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি, যার পরিমাণ প্রায় ১২৩ বিলিয়ন ডলার।
উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শুধু যে ভিয়েতনাম আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করে উচ্চ শুল্কহারের সন্তোষজনক সমাধান করেছে তেমন নয়। ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন যে ফিলিপিন্সের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার উচ্চ শুল্কহারের বিষয়টির একটি সন্তোষজনক সমাধান হবে। ইন্দোনেশিয়াও আমেরিকার সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শিগগিরই হয়তো এ রকম একটি চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত হবে এবং উচ্চ শুল্কহারের সন্তোষজনক সমাধান হবে।
ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার সফল বাণিজ্যচুক্তি এবং এর পাশাপাশি যদি ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন হয়েই যায়, তাহলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি মারাত্মক সংকটে পড়তে পারে। কেননা এই দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতিযোগী এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তখন বাংলাদেশের পরিবর্তে ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করতে উৎসাহিত হবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভিয়েতনাম আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক সমস্যার সমাধান করে বাণিজ্যচুক্তি করতে পারলে আমরা কেন পারছি না?
ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি আছে এবং ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে চীনের রপ্তানিকারকরা ভিয়েতনামের মাধ্যমে আমেরিকায় পণ্য রপ্তানি করে থাকেন। সেই ভিয়েতনামই সবার আগে আমেরিকার সঙ্গে সফল বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করে ফেলল। অথচ আমরা এখন পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে আলোচনা এবং পত্র চালাচালির মধ্যেই আটকে আছি। ফলে আমাদের দেশের বৃহত্তম রপ্তানি খাতটি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে বসেছে। কারণ ভিয়েতনাম যেভাবে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করেছে, আমরা সেভাবে অগ্রসর হতে পারিনি। শুধু সরকারি পর্যায়ে আলোচনা এবং গতানুগতিক চিঠি চালাচালির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এ জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—(১) দেশের ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিদের নিয়োজিত করা; (২) আমেরিকার যেসব বৃহৎ কম্পানি এবং ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠান পোশাক আমদানি করে, তাদের সহযোগিতা নেওয়া; (৩) প্রয়োজনে এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য লবিইস্ট ফার্ম নিয়োগ দেওয়া; (৪) বাংলাদেশের বাজারে আমেরিকার কিছু পণ্যের শুল্কমুক্ত বা অল্প শুল্কে আমদানির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং (৫) দেশে দ্রুত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এ রকম কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারলে ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়ার মতো আমরাও আমেরিকার সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তিতে উপনীত হতে পারি, যার মাধ্যমে আরোপিত শুল্কহার অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ হচ্ছে একটি কৌশলী পদক্ষেপ, যা কৌশলী আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে।
লেখক : সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা
Nironjankumar_roy@yahoo.com
রাজনীতিতে জনসমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর
- ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো পুরোপুরি ঐক্য দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর যথেষ্ট টানাপড়েন দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। তা ছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।
নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রধান কাজ।
নির্বাচন কখন হবে, কিভাবে হবে—এ বিষয়ে নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মতামত এবং অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনীতিতে তারা এখন বিশেষ ফ্যাক্টরে পরিণত হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র-তরুণদের এই দলটি আলাদা ধরনের গুরুত্ব বহন করছে বলে পরিষ্কার ধারণা করা যায়।
এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রায় ১১ মাস অতিবাহিত হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত নির্বাচনের যেমন সুস্পষ্ট রোডম্যাপ সরকারের পক্ষ থেকে আসেনি, ঠিক তেমনি কোনো রাজনৈতিক দলও তাদের জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক রোডম্যাপ যথাযথভাবে ঘোষণা করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো ভিশন আমাদের সামনে সুনির্দিষ্টভাবে উত্থাপিত হয়নি। এমনকি এনসিপি যে জুলাই পদযাত্রা করছে, সেটি জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলেও কম সময়ে সারা দেশের মানুষের সঙ্গে যথাযথ মিথস্ক্রিয়া করতে পারছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এরই মধ্যে জামায়াত একটি জাতীয় সমাবেশ করে আগামী দিনে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে। অন্যদিকে বিএনপিও নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে অপেক্ষাকৃত দ্রুততম সময়ে নির্বাচনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ আমরা জানি, যেকোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা। এ ক্ষেত্রে জনগণ যেভাবে চায়, ঠিক সেভাবেই তাদের কাজ করতে হয়।
নির্বাচনের দিন-তারিখ ঠিক হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তা-ও কিন্তু নয়। রাজনীতিতে টানাপড়েন বাড়তে থাকলে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাও বাড়তে থাকবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে সব পক্ষকে একটি যথাযথ এবং ন্যায্য দিকে হাঁটতে হবে। কারণ যথাযথ রাস্তায় হাঁটতে না পারলে কোনোভাবেই দেশে ইতিবাচক রাজনীতির সূত্রপাত হবে না। এ কারণে প্রয়োজন একটি উইন-উইন পরিস্থিতির। এ ক্ষেত্রে সব রাজনৈতিক পক্ষকেই বিশেষ ছাড় দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে রাজনীতির মাঠে থাকতে হবে। সব পক্ষ থেকে ছাড় দিতে না পারলে কোনোভাবেই উইন-উইন পরিস্থিতি আশা করা যায় না।
বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পাওয়া রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি শতাধিক নিবন্ধনহীন এবং ব্যক্তিনির্ভর দল রয়েছে। যেসব নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন জমা দিয়েছে, সেগুলোর অনেকগুলোরই কোনো অফিস নেই, আবার অফিস থাকলেও সভাপতির নিজের বাসার ড্রয়িংরুম অফিসের ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছি। এমনকি বেশির ভাগই প্রাথমিক যোগ্যতা পূরণ করতে পারেনি বলে নির্বাচন কমিশন চিঠি দিয়ে জানিয়েছে।
অনেক দল রয়েছে, যেগুলোর সভাপতির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় না। এ ছাড়া বিদ্যমান নিবন্ধিত অনেক দলই সাইনবোর্ডসর্বস্ব রাজনৈতিক দল। নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া আর কারো তেমন জনসমর্থন নেই। বাকি দলগুলোর তেমন একটা জনসমর্থন না থাকলেও দলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড রয়েছে। এদের তৎপরতা দেখা যায় শুধু নির্বাচন মৌসুম এলেই। নির্বাচনের আগে এই দলগুলোর কদর বেড়ে যায়। বড় দলগুলোর সঙ্গে জোটভুক্ত হওয়া, নির্বাচনে মনোনয়ন এবং ক্ষমতা ভাগাভাগির দর-কষাকষি চলে।
যেকোনো রাজনৈতিক দল বৈধ এবং সাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক দলগুলো জোট গঠন করেও ক্ষমতায় আসে এবং আসার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে বিদ্যমান নামসর্বস্ব দলগুলোর কোনো জনসমর্থন নেই।
আমরা আশা করব, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সত্যিকার অর্থেই জনগণের জন্য কাজ করবে। এমনকি সব দল এবং দলের নেতারা সহনশীল হবেন, সংযত হবেন। অতীত বা বিগত দিনগুলোর অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর কল্যাণের রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবেন, যাতে দেশ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ধারায় চলতে পারে, যাতে দেশে কোনো অপশক্তি মাথাচাড়া দেওয়ার মতো অবস্থা ভবিষ্যতে সৃষ্টি না হয়। রাজনীতিতে প্রতিহিংসা এবং পারস্পরিক টানাপড়েন যত কমিয়ে আনা যাবে, ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল হবে। এ ক্ষেত্রে সব পক্ষকে একটি যথাযথ এবং ন্যায্য দিকে হাঁটতে হবে। কারণ যথাযথ রাস্তায় হাঁটতে না পারলে কোনোভাবেই দেশে ইতিবাচক রাজনীতির সূত্রপাত হবে না।
রাজনৈতিক দলগুলোক মনে রাখতে হবে, ভোটের রাজনীতিতে বিজয়ী হওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হলো সাংগঠনিক ভিত্তি এবং জনসমর্থন। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত না হলে এবং জনসমর্থন না থাকলে সেই দল নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে না। প্রসঙ্গত বলতে হয় যে নতুন দলগুলোর উচিত সাধারণ মানুষের জন্য ব্যতিক্রম চিন্তা বা জনমুখী কর্মসূচি নিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বাস্তবতাবিবর্জিত রাজনৈতিক দর্শনের কারণেও অনেক দল মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না। ফলে জনসমর্থনও বাড়ে না, বরং হিংসা-বিদ্বেষ এবং হানাহানির পরিবেশ তৈরি হয়। আর মোটাদাগে ওই সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনের ফলাফল নেতিবাচক হয়।
লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়