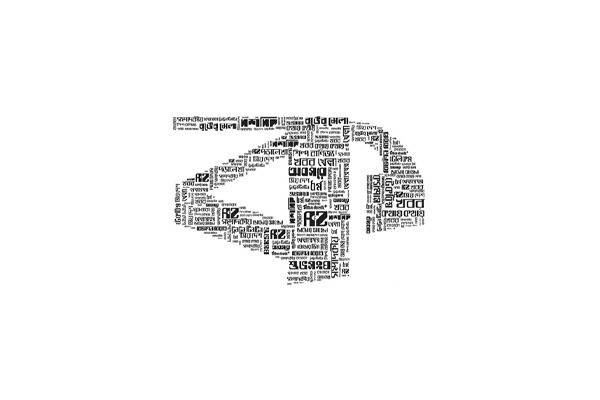বাংলাদেশের মানুষের জন্য একাত্তরের ৯ মাস ছিল কঠিন দুঃসময়, কিন্তু সেটি ছিল সম্মানের কালও বটে। কেননা বাঙালি তখন যুদ্ধক্ষেত্রে, মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যককে বাদ দিলে তখন ভিক্ষুক ছিল না দেশে, সবাই যোদ্ধা। যুদ্ধের সময়ে এবং তারপর কয়েক মাস সারা বিশ্বে বাঙালি যতটা সম্মান পেয়েছে, অতীতে তেমনটা কখনো পেয়েছে বলে ইতিহাস আমাদের জানায় না। কিন্তু এরপর আমরা যুদ্ধ ছেড়ে নেমে গেছি ভিক্ষায়, সম্মান যা ছিল ক্রমাগত খুইয়েছি।
কেউ থাকে যুদ্ধে, কেউ চলে ভিক্ষায়
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
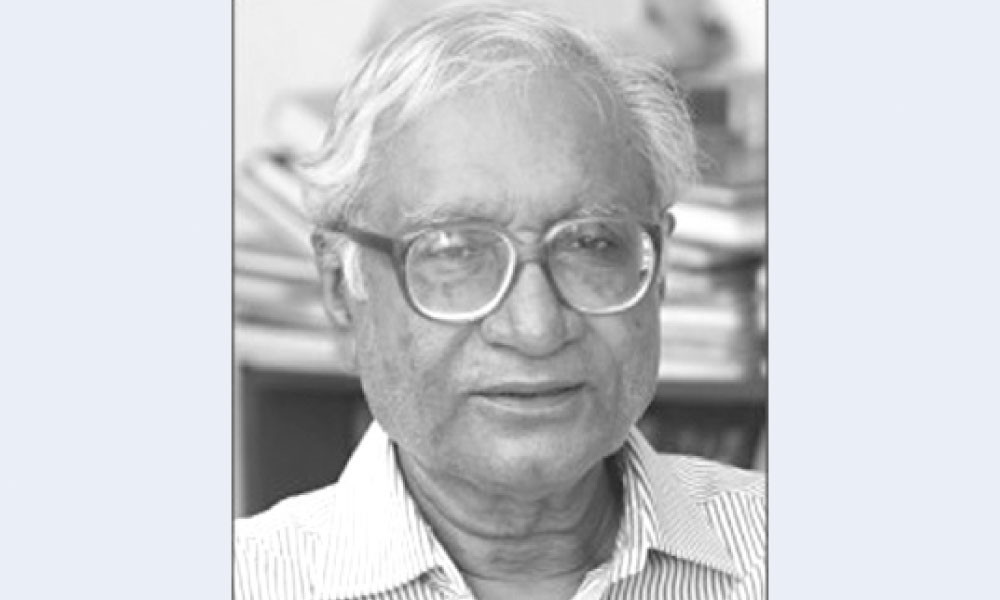
একাত্তরের দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা এখন পথের ভিক্ষুক, তাঁদের লাঞ্ছিত ও গৃহত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এ রকম খবর বাংলাদেশের অনেক এলাকায়ই তৈরি হয়েছে, ছাপা হয়েছে সংবাদপত্রে, কখনো কখনো সচিত্র আকারে। উল্টো সংবাদও পাওয়া গেছে। শুনেছি, সেদিনের বীর মুক্তিযোদ্ধা এখন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হয়েছেন।
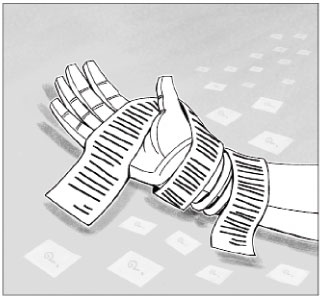 কিন্তু ব্যাপারটি তো কেবল এর বা ওর নয়, ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগতও এবং সমস্যাটি আসলে সেখানেই। স্বাধীনতা জিনিসটা ব্যক্তিগত নয়, লড়াইটা ব্যক্তির সুবিধার জন্য ঘটেনি, লক্ষ্য ছিল সমষ্টিগত। আশা ছিল জাতি হিসেবে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াব, মেরুদণ্ড থাকবে দৃঢ়, হব স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভর। হব সৃষ্টিশীল, পরিপূর্ণরূপে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। দিনে দিনে ওই মর্যাদা বাড়বে, কমবে না। স্বাধীনতার পর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যে ঘোষণা করেছিলেন, বাংলাদেশ মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করবে না। তাঁর সেই ঘোষণা যুদ্ধের ভেতর থেকেই বের হয়ে এসেছিল এবং সমর্থন পেয়েছিল সমগ্র জনগোষ্ঠীর। মার্কিন সাহায্য ছাড়া আমাদের চলবে না, আমরা খাব কী, পুঁজি কোথায়—এ ধরনের যেসব সন্দেহ ভিক্ষুকদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সেগুলো তখন কারো কারো মনের ভেতরে থাকলেও প্রকাশ্যে শোনা যায়নি। যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না। কেননা সময়টা তখন বিজয়ের।
কিন্তু ব্যাপারটি তো কেবল এর বা ওর নয়, ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগতও এবং সমস্যাটি আসলে সেখানেই। স্বাধীনতা জিনিসটা ব্যক্তিগত নয়, লড়াইটা ব্যক্তির সুবিধার জন্য ঘটেনি, লক্ষ্য ছিল সমষ্টিগত। আশা ছিল জাতি হিসেবে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াব, মেরুদণ্ড থাকবে দৃঢ়, হব স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভর। হব সৃষ্টিশীল, পরিপূর্ণরূপে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। দিনে দিনে ওই মর্যাদা বাড়বে, কমবে না। স্বাধীনতার পর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যে ঘোষণা করেছিলেন, বাংলাদেশ মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করবে না। তাঁর সেই ঘোষণা যুদ্ধের ভেতর থেকেই বের হয়ে এসেছিল এবং সমর্থন পেয়েছিল সমগ্র জনগোষ্ঠীর। মার্কিন সাহায্য ছাড়া আমাদের চলবে না, আমরা খাব কী, পুঁজি কোথায়—এ ধরনের যেসব সন্দেহ ভিক্ষুকদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, সেগুলো তখন কারো কারো মনের ভেতরে থাকলেও প্রকাশ্যে শোনা যায়নি। যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না। কেননা সময়টা তখন বিজয়ের।
তার পরও মার্কিন সাহায্য চলে এসেছে। কেবল মার্কিন নয়, পুঁজিবাদী বিশ্বেরও এবং এ রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে কোন সরকার কত বেশি বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ করতে পারে তার ওপরই ওই সরকারের সাফল্যের একটি বড় অংশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এভাবে জয়ের পরেই পরাজয় ঘটার আশঙ্কা দেখা দিল। বিজয়ী জাতি যুদ্ধের পথ থেকে সরে এগিয়ে গেল ভিক্ষার পথে। কী করা দরকার ছিল? দরকার ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কিন্তু সেটি সম্ভব হতো তখনই, যখন দেশের সব মানুষ প্রস্তুত হতো আত্মত্যাগে। তা আত্মত্যাগের জন্য মানুষ প্রস্তুত ছিল বৈকি। যুদ্ধে গেছে তারা ত্যাগের জন্যই, ভোগের জন্য নয়। কিন্তু ব্যর্থতা দেখা গেল নেতৃত্বে, নেতৃত্ব ত্যাগে প্রস্তুত ছিল না, প্রস্তুত ছিল ভোগের জন্য। প্রতিযোগিতা শুরু হলো ত্যাগের নয়, উপভোগের। বিলাসের।
আমরা সমষ্টির কথাই বলছি। কিন্তু সমষ্টি তো ব্যক্তি নিয়েই গঠিত। যুদ্ধের পরে দেখা গেল ব্যক্তি ব্যস্ত হয়ে গেছে সে কী পেয়েছে তার হিসাব নিতে। এই বোধের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোনো সংগতি নেই, বরং এ হচ্ছে ওই চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা এটি ভিক্ষুকের মনোভাব, যোদ্ধার নয়। যোদ্ধারা সবার স্বার্থ দেখেন, ভিখারি দেখে নিজের স্বার্থ। যুদ্ধে বিজয়ের পর দেখা গেল মানুষ ভিখারি হয়ে যাচ্ছে। বিদেশি সাহায্য ছাড়া আমাদের চলবে না—এই বোধটি যোদ্ধাদের বোধ নয়। ওই মনোভাব থাকলে যুদ্ধ হতো না, যাঁরা ওই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুদ্ধে গেছেন, তাঁরা প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন না। বিদেশি সাহায্যের লালসা প্রবল হলো, সঙ্গে থাকল ব্যক্তিগত লাভের লিপ্সা। দুটি অবশ্য ভিন্ন বস্তু নয়, একই তারা।
ব্যর্থতা নেতৃত্বেরই। বড় বড় নেতা যাঁরা, তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন না। বিজয়ের সম্ভাবনার বিষয়ে কেউ ছিলেন দোদুল্যমান, কেউ হতাশ। যুদ্ধের পর তাঁদের প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল যোদ্ধাদের নিয়ে। যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করতে চেয়েছেন, তাঁদের ট্রেনিং ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। সে ইচ্ছা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু নেতাদের আসল অস্বস্তি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়েই। ওই চেতনা শোষণবিরোধী, অথচ নেতৃত্বের লোভ তখন লুণ্ঠনে। বাহাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শত্রু রাজাকাররা নয়, কেননা তখন তারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। প্রধান শত্রু সেই নেতারা, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে যাঁরা লুণ্ঠন শুরু করেছিলেন, যেন নতুন হানাদার। কিন্তু তখন তো আর প্রতিরোধ নেই, যুদ্ধ থেমে গেছে, বিজয় অর্জিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিশ্চিত হতে পারেনি বিজয়টি কার। হানাদাররা পালিয়েছে সেটি ঠিক, সেটি একটি বিরাট স্বস্তি। কিন্তু শান্তি কোথায়, শান্তি পাওয়া যায়নি, সুখ তো নয়ই। তার পরের ইতিহাস তো সুখ-শান্তি বৃদ্ধির ইতিহাস নয়। জনবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব যুদ্ধবিজয়ী জাতিকে পরাজয়ের পথে ঠেলে দিয়েছে।
সত্য এটিও যে এই ভোগবাদিতা মৌলবাদকে উৎসাহিত করেছে। তা ছাড়া বঞ্চিত মানুষ দেখেছে সব সুখ কিছু লোক নিয়ে নিচ্ছে এবং বঞ্চনার এই বোধ থেকে তারা ধর্মের কাছে গেছে, গিয়ে প্রকাশ্যে যারা ভোগবাদী, তাদের তুলনায় নিজেদের উচ্চজ্ঞান করার সুযোগ পেয়েছে।
মৌলবাদ আজকের বাংলাদেশে মস্ত বড় সমস্যা। এর বিকাশে আরো যেসব উপাদান কার্যকর রয়েছে, তাদের একটি হচ্ছে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা। এ কাজ ধর্ম ব্যবসায়ীরা তো করছেই, জাতীয়তাবাদী বড় দলও করছে। মৌলবাদের পেছনে আরেকটি কারণ মানুষের আশ্রয়হীনতা। রাষ্ট্র তার মিত্র নয়। নিরাশ্রয় মানুষ ধর্মের কাছে যায় আশ্রয় ও বিচারের প্রত্যাশায়। আশ্রয় জিনিসটা যে কত দরকার তার একটি সাম্প্রতিক প্রমাণ পাওয়া গেছে রুশ দেশের জাতীয় সংগীতের পরিবর্তনে প্রতিফলিত মনোভঙ্গিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন একদা যে গানকে জাতীয় সংগীত করেছিল, সোভিয়েতের পতনের পর তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, কিন্তু মানুষ ওই গান ভোলেনি। ওই গানে আশ্রয়ের কথা ছিল, জনগণের পার্টি জনগণকে আশ্রয় দেবে—ছিল এই কথা। নতুন গান তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তাই পুরনো গানের সুরটিকে ফেরত আনা হয়েছে, কথাগুলো বদলে। আগে যেখানে ভরসা করা হয়েছিল পার্টির ওপর, এখন সেখানে ভরসা করা হচ্ছে ঈশ্বরের ওপর। ওই রকমই বটে, আশ্রয় দরকার হয় এবং সে আশ্রয় ঐহজাগতিক সংগঠনের কাছে না পেলে পারলৌকিক ঈশ্বরের কাছে যেতে হয়। মৌলবাদের তৎপরতার পেছনে এই হারানো এবং প্রাপ্তির ব্যাপারের কার্যকর ভূমিকাকে যেন না ভুলি।
যুদ্ধ কোথায় নেই? নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, কলহ সর্বদা চলছে। সর্বত্র চলছে। আছে গৃহে, রয়েছে সমাজে। মানুষ বাঁচার জন্য লড়ছে। একালের মূল যুদ্ধটি রাজনৈতিক। রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক কাল ধরে ওই দুই ধারা ছিল—একটি ভিক্ষার, অপরটি যুদ্ধের। ভিক্ষার রাজনীতি আবেদন-নিবেদনের, যুদ্ধের রাজনীতি আন্দোলনের।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গে প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। তার অঙ্গীকারটি ভিক্ষার ছিল না, ছিল যুদ্ধের, যে জন্য ওই আন্দোলনে বিভ্রান্তি আসেনি, তাকে বিভক্ত করা সম্ভব হয়নি। সে থেমে যায়নি মাঝপথে এবং পরিণতিতে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন বাংলাদেশের। কিন্তু আপসের প্রস্তাব যে আসেনি তা তো নয়, এসেছে এবং এসেছে একেবারে শুরুতেই। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সরকার কর্তৃক তড়িঘড়ি জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করা হবে কি হবে না—এই ঐতিহাসিক প্রশ্নে ক্ষমতালব্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভঙ্গ না করার। তারা ভয় পেয়েছে আন্দোলন চলে যাবে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, গোলযোগ বাধবে। ফলে সরকার নির্বাচন দেবে পিছিয়ে এবং নির্বাচন পিছিয়ে দিলে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারটি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ভিক্ষুকদের কথা, সন্দেহ কি! কিন্তু যোদ্ধারা শোনেননি। তাঁরা এগিয়ে গেছেন ওই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এবং পরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নয়, যুদ্ধের মধ্য দিয়েই দেশকে স্বাধীন করেছেন।
সত্তরে নির্বাচন হয়েছে, একাত্তরে যুদ্ধ। সাতচল্লিশে ব্রিটিশ শাসকরা যা করতে পেরেছিল, একাত্তরে পাকিস্তানি শাসকরা তা করতে পারেনি, অর্থাৎ পারেনি যোদ্ধাদের হটিয়ে দিয়ে আপসপন্থীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিয়ে প্রস্থান করতে। তবে ওই শাসকদের মুরব্বি যারা, সেই সাম্রাজ্যবাদীরা, তৎপর হয়ে উঠেছে যুদ্ধকে যত শিগগিরই পারা যায় থামিয়ে দিতে, যুদ্ধের নেতৃত্ব যাতে বামপন্থীদের হাতে চলে না যায় এবং বাংলাদেশ যাতে নতুন একটি ভিয়েতনামে পরিণত না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে। এর পরের ইতিহাস তো আমরা জানিই। যোদ্ধাদের উৎসাহিত করা হয়েছে ভিক্ষুকে পরিণত হতে।
সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধকে সমর্থন করেনি; তাদের আশঙ্কা ছিল এই রাষ্ট্র তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, চলে যাবে সমাজতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রের আদি সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য চিহ্নিত ছিল, সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র, যার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা তো রয়েছেই, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিও বিদ্যমান। যুদ্ধ শুরু হোক সাম্রাজ্যবাদীরা এটি চায়নি, শুরু হওয়ার পর চেয়েছে দ্রুত থেমে যাক এবং থেমে গেছেও। তার পরে তারা শাসকদের টেনে নিয়েছে কোলে। রাষ্ট্র চলে গেছে সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশ এখন একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র। তার মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো ঢাকায় নেওয়া হয় না, নেওয়া হয় অন্যত্র। আমলাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে, এনজিওগুলোও তাই। মাটির নিচে তেল-গ্যাসের খোঁজ পাওয়া গেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা চাচ্ছে সেটি গ্রাস করতে। সরকার এবং বিরোধীরা কেউই এ ব্যাপারে অসম্মত নয়। তারা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, কিন্তু তারা যোদ্ধাদের দল নয়, দল বিপরীত ধরনের মানুষদের। তারা দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি চায় না, চায় নিজেদের থলি ভরপুর করতে। রাষ্ট্রকে নিয়ে গেছে এমন জায়গায় যে ভিক্ষা ছাড়া তার চলে না।
কিন্তু তবু যুদ্ধ তো চলছে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো যা দেওয়ার এরই মধ্যে দিয়ে ফেলেছে, তারা আর কিছু দেবে না, রাষ্ট্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা এবং জনগণের জন্য অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়া। তারা পুঁজিবাদকে বিকশিত করছে, যে পুঁজিবাদ মানুষের মুক্তি আনবে না, আনলে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভেঙে বাঙালিকে বের হয়ে আসতে হতো না। জাতীয়তাবাদী বলে কথিত বড় দুই রাজনৈতিক দল চায় না যে রাজনৈতিক যুদ্ধটি চলুক। কেননা এই যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধেই।
মুক্তির ওই যুদ্ধকে আসলে দমন করাই হচ্ছে। দমনের কাজটি নীরবে চলছে। কেননা যুদ্ধটি প্রবল হয়নি। প্রবল হলেই নিপীড়ন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। যুদ্ধটি অবশ্যই বাম ধারার; না হয়ে উপায় নেই। এ ধারার খবর টেলিভিশন ও রেডিওতে আসে না, প্রশ্নই ওঠে না আসার; টেলিভিশন ও রেডিও সরকারি প্রচারযন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সংবাদপত্রেও এই আন্দোলনের খবর আসে না। উল্টো খবর দেওয়া হয়, বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে। কেননা সংবাদপত্রের মালিকরা ভিক্ষুক চান, যোদ্ধা চান না।
বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন চলছে। প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন যে জোরদার হচ্ছে না, তাতে আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, বরং কারণ আছে দুঃখিত হওয়ার। একাত্তরের যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে গেলে আমাদের জন্য তা যেমন ভয়ংকর ব্যাপার হতো, মুক্তির চলমান যুদ্ধে ব্যর্থতাও তেমনি বিপজ্জনক হবে। ভিক্ষা আর যা-ই হোক, মুক্তির পথ নয়।
সামনে যেতে হলে ঐক্য দরকার হবে, সাধারণ ও চিহ্নিত শত্রুর বিরুদ্ধে। স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে আছে ওই মৈত্রীতে, তার বাইরে কোথাও নেই। বাইরে কেবল সংঘর্ষ ও একাকিত্ব, কেবলই নত হওয়া; বলা চলে নরকবাস, যা নিশ্চয়ই আমরা চাইব না।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত খবর
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : চাওয়া-পাওয়ার দাগ-খতিয়ান
- তুহিন খান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রায় এক বছর উপলক্ষে জুলাই ও আগস্ট মাসজুড়ে বেশ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানসূচি ঘোষিত হয়েছে ইন্টেরিম সরকারের তরফে। কিন্তু এক বছরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব কতটা মেলানো গেল? জুলাইয়ের সুফল কার ঘরে কতটা উঠল?
গণ-অভ্যুত্থান নিজেই একটি বড় প্রাপ্তি। যে অভ্যুত্থানের ফলে আওয়ামী লীগের মতো একটি নিকৃষ্ট ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর পতন হলো, তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি এ দেশের জনগণের জীবনে খুব কমই আছে। এই অভ্যুত্থানের আগে-পরে দেশে যে বিপুল জনসচেতনতা ও সৃষ্টিশীল গণক্ষমতার উদ্বোধন আমরা দেখেছি, তরুণদের মধ্যে যে স্বচ্ছ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও দেশ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিতে দেখেছি, তা এককথায় মহাকাব্যিক।
গত বছর ৮ আগস্ট ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার ভারত পলায়নের পরিপ্রেক্ষিতে যে সরকারটি গঠিত হয়, তার ধরনটি ঠিক কী হবে, কী হলে আরো ভালো হতো, এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা আছে। অন্তর্বর্তী এই সরকারটি গঠিত হয়েছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই; আবার গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের কেউ কেউ এ সরকারের অংশ হয়েছেন।
জুলাইয়ের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্বর্তী সরকারের এই ধরন ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর অবস্থান—এই তিনের টানাপড়েন শেষমেশ যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় থিতু হয়েছে, তার আলংকারিক নাম : সংস্কার। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আগ থেকেই বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্ল্যাটফর্মের কারণে ‘রাষ্ট্র সংস্কার’ ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে সেটির প্রায়োগিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং কিভাবে ও কতটুকু হবে এই সংস্কার—সেটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন হয়েছে দেশে এবং সেসব কমিশন বড় বড় রিপোর্টও তৈরি করেছে।
রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবেই যে সামাজিক ফ্যাসিবাদ ও ধর্মীয় চরমপন্থা সুপ্তাবস্থায় প্রায় এক যুগ ধরে আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে উঠছিল, তা অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে নিঃশেষিত হয়নি, বরং নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী প্রবণতা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন শক্তিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি ও তার দেশি-বিদেশি এজেন্টরা এই প্রবণতাগুলোকে অনেক রংচং মেখে বাস্তবের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বিকট করে উপস্থাপন করার চেষ্টায় রত। জুলাইয়ের শক্তিগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন ও মেরুকরণও এই পরিস্থিতিটিকে বেশ ঘোলাটে করে তুলছে। সে ব্যাপারে সতর্ক থেকেও বলা যায় যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে।
‘মব’ শুনলেই অনেকে খেপে যান আজকাল, তার সংগত কারণও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সত্য কথা এটিই যে ৫ আগস্টের পর দেশে নানা রকম মব তৈরি হয়েছে। সামাজিক-নৈতিক পুলিশগিরি বাড়ছে। এসবের সঙ্গে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বা বিপ্লবী তৎপরতার যোগ সামান্য। ধর্মীয় চরমপন্থাও এই পরিস্থিতিকে একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করছে।
বিপ্লবী ছাত্র-জনতা ও সরকারের কাজ ছিল সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা এই নতুন প্রতিবিপ্লবী, হঠকারী ও ফ্যাসিস্ট তৎপরতাগুলোরও বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, যেখানে মোটাদাগে স্পষ্টতই তারা ব্যর্থ হয়েছে। এতে সমাজে সরকার ও অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের ব্যাপারে যে মাত্রারই হোক, একটি নেতিবাচকতা তৈরি হয়েছে।
৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ের একটি প্রধান জনদাবি ও গুরুতর কাজ ছিল বিচার ও আনুষ্ঠানিক রিকনসিলিয়েশন প্রসেস শুরু করা। কিন্তু এই দাবিটি বিদ্যমান কোনো রাজনৈতিক শক্তিই সততার সঙ্গে সামনে আনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। নির্বাচনী রাজনীতির হিসাব-নিকাশ, সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর টানাপড়েন, মামলা বাণিজ্যের পলিটিক্যাল ইকোনমি, ঘোলা পানিতে মাছ শিকারিদের নানা রকম অপতৎপরতা, বিচারহীন পুনর্বাসনের বিবিধ উদ্যোগ আর সরকারের অস্পষ্ট ও গতিহীন নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিচারের দাবিটির বহুলাংশ অপচয় হয়েছে। একটি ফ্যাসিস্ট সরকারকে উত্খাত করার পর অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা ও সামাজিক-রাজনৈতিক রিকনসিলিয়েশন নিশ্চিতে যে ধরনের ব্যাপক, বহুমুখী ও কুশলী প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা প্রয়োজন ছিল, সরকার সেটি করতে বেশ খানিকটা ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়।
অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলটিকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এক ধরনের কৌতূহল, আকাঙ্ক্ষা ও দরদ তৈরি হয়েছে। তবে এই আকাঙ্ক্ষা নিরঙ্কুশ নয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে ঢুকে পড়ায় বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর অনেক বিষয়ই আত্তীকৃত করতে হয়েছে দলটির, যা তাদের নানাভাবে বিতর্কিত করেছে। আবার এই দলটির গতি-প্রকৃতি কী হবে, তার কল্পনার বাংলাদেশটি ঠিক কেমন হবে—এসব বিষয়েও নানা ধরনের অনুমান তৈরি হয়েছে। এসব সত্ত্বেও পরিবর্তনকামী বা সংস্কারবাদীরা এখনো এই দলটির ওপর ভরসা রাখতে চাইছেন বলেই মনে হয়।
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এই হিসাব চলবে। কিন্তু জুলাইয়ে ঘটে যাওয়া মহাকাব্যিক অভ্যুত্থানটি আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা হাজির করেছে, তা অসামান্য। আমরা এর কতটা কাজে লাগাতে পারব, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে বাংলাদেশ যত দিন থাকবে, তত দিন মুক্তির এই অসামান্য সম্ভাবনা এ দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।
লেখক : কবি, অনুবাদক ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন
- ড. নিয়াজ আহম্মেদ

করোনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে যে ছেদ তৈরি হয়েছিল, তা এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এ ছাড়া গত বছরের গণ-আন্দোলনে তিন-চার মাস আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। বিশ্ব্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমাদের এইচএসসি নামক পাবলিক পরীক্ষা। কোনো কারণে এইচএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে আমাদের ভর্তি কার্যক্রমও পিছিয়ে যায়।
আমরা যদি জানুয়ারি মাসে এসএসসি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে এইচএসসি পরীক্ষা নিতে পারি, তাহলে জুলাই মাসে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যাবে।
উচ্চশিক্ষা যেহেতু বহু রকমের, সেহেতু এখানেও অনেক বিষয় রয়েছে। মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার বিষয়টি সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই তারা বেশ দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যদি একটি পরীক্ষায় ভর্তি নিতে পারত, তাহলেও সময় বাঁচত। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। আমাদের মানে শিক্ষকদের এখানে করণীয় রয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা প্রতিবছর একই পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা এবং এর কার্যক্রম সম্পন্ন করি। ফলে দ্রুত কার্যক্রম শুরু করতে সমস্যা নেই। ফলাফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, এক মাসের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা এবং সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে পুরো ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব।
আমাদের কাছে মনে হয়, সরকারের আন্তরিকতা এবং শিক্ষকদের সহযোগিতা এখানে মুখ্য বিষয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, কতটা সহজে এবং দ্রুত আমরা আমাদের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারি। আমাদের টার্গেট যদি থাকে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন ক্লাস শুরু করা, তাহলে টার্গেট অনুযায়ী কাজটি করতে হবে। একদিকে শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষা দেবে, অন্যদিকে আমরা ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করব। সরকার যদি পাবলিক পরীক্ষা আগে এবং দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে আমরাও দ্রুত ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারব। ধরুন, এখন এইচএসসি পরীক্ষা চলছে। আশা করা যায়, সেপ্টেম্বরে ফলাফল প্রকাশিত হবে। আমরা অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে পারি। তিন মাসে কি ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা যথেষ্ট নয়? আমাদের দরকার সরকারের ইচ্ছা এবং সবচেয়ে বড় দরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়, শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা। আমরা আশা করব, আগামী শিক্ষাবর্ষে যেন জানুয়ারি মাসেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়।
লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
nahmed1973@gmail.com
কজন জানে জুলাই সনদ কী
- গাজীউল হাসান খান

সমাজ ও বৃহত্তরভাবে রাষ্ট্র মেরামত কিংবা পরিবর্তনের জন্য যেসব কাঙ্ক্ষিত বা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, মূলত সেগুলোকেই সংস্কার বা ‘রিফর্ম’ বলা হয়। দেশের সংবিধান থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিকরা কিংবা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সেসব সংস্কারের উদ্যোগ নিতে পারেন। তবে শেষ পর্যন্ত জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেসব সংস্কার প্রস্তাবকে কার্যকর করতে হলে একটি আইনানুগ ভিত্তি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশে চব্বিশ সালের গণ-অভ্যুত্থান-উত্তর সময়ে অতীত স্বৈরাচারী কিংবা ফ্যাসিবাদী শাসন এবং আর্থ-সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার অবসানের জন্য দল-মত-নির্বিশেষে সবাই রাষ্ট্র মেরামতের একটি জোরালো দাবি উত্থাপন করেছে।
 এ কথা ঠিক যে বিগত জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থান কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না। তবু সেটি আমাদের বিগত ৫৩ বছরের স্বাধীনতা-উত্তর আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিরাট মাইলফলক। স্বৈরাচারী কিংবা ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণের কবল থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে একটি বিশাল পদক্ষেপ। সুতরাং কোনো বিবেচনায়ই সে অভ্যুত্থানকে খাটো করে দেখা যাবে না।
এ কথা ঠিক যে বিগত জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থান কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না। তবু সেটি আমাদের বিগত ৫৩ বছরের স্বাধীনতা-উত্তর আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিরাট মাইলফলক। স্বৈরাচারী কিংবা ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণের কবল থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে একটি বিশাল পদক্ষেপ। সুতরাং কোনো বিবেচনায়ই সে অভ্যুত্থানকে খাটো করে দেখা যাবে না।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান অধ্যাপক ড. ইউনূসসহ আমাদের রাজনৈতিক মহলের অনেকেই এরই মধ্যে গণ-অভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এতে তাঁদের অনেকের মধ্যেই বিগত ১১ মাসে ঘটে যাওয়া অনেক ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে অনেকে দায়ী করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের নেতা ও অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সাবেক নেতারা এরই মধ্যে বহুবার অভিযোগ করেছেন যে অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে সময়োচিতভাবে একটি ‘জুলাই সনদ’ ঘোষণার অভাবে রাজনৈতিক মহলে এখনো অনেক বিভ্রান্তি এবং ভবিষ্যৎ দিকদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তাদের নিজ নিজ দলের পতাকাতলে অবস্থান নিয়েছে। ভুলে গেছে সেই মহান গণ-অভ্যুত্থানের জাতীয় প্রেক্ষাপটটি। রাজনৈতিক ঐক্য কিংবা রাজনৈতিক কর্মসূচিগত সমন্বয়ের বিষয়টি। ফলে চারদিকে মাথা তোলার অবকাশ বা সুযোগ পেয়েছে পতিত আওয়ামী সরকারের দোসর কিংবা বশংবদরা। সে পরিস্থিতিতে ড. ইউনূস হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, ‘আমাদের একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বিফলে যেতে বসেছে। আমরা মুখে বলছি, সাবেক ফ্যাসিবাদী সরকারের প্রতিনিধিরা এখনো সর্বত্র বসে রয়েছে। আমরা তাদের সরাতে পারিনি। আমরা তাদের স্বভাব-চরিত্র বদলাতে পারিনি।’ এ অবস্থায় অনতিবিলম্বে সর্বক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারলে এবং সব জায়গায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার কিংবা পরিবর্তন সাধন করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে ক্ষমতার রাজনীতিতে কোনো নির্বাচিত সরকারই স্থিতিশীল হতে পারবে না। এতে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন, উন্নয়ন কিংবা সমৃদ্ধি আশা করা হয়েছিল, তা বিফলে যেতে বাধ্য হবে। এখানেই অতীতে সংঘটিত সব গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের মৌলিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য ছিল। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারটি ছিল গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী একটি ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক উদ্যোগের ফসল, কিন্তু তাতে অন্য অনেক কিছু থাকলেও ছিল না রাজনৈতিক দূরদর্শিতা।
ফরাসি বিপ্লব রাশিয়ায় সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক (বলশেভিক) বিপ্লবের মতো ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দশকে (১৭৮৯-১৭৯৯) ফ্রান্সে সংঘটিত সে বিপ্লব ছিল একটি ‘দশক স্থায়ী সামাজিক-রাজনৈতিক অভ্যুত্থান’। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সময়। সে অভ্যুত্থানের শুরুতেই অর্থাৎ ১৭৮৯ সালে তার নেতারা ফ্রান্সের নাগরিক কিংবা মানুষের অধিকার নিয়ে ফ্রেঞ্চ চার্টার নামে একটি সনদ ঘোষণা করেন। সে সনদই ফরাসি বিপ্লবের মৌলিক চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে। তাদের মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতি প্রকাশ করে। এর পাশাপাশি মানুষের মৌলিক অধিকার ও দায়দায়িত্বের পথনির্দেশ প্রদান করে। সেদিক থেকে পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশে সংঘটিত জুলাই-আগস্টের বিপ্লবও ছিল মূলত একটি গণ-অভ্যুত্থান। কিন্তু সে সফল অভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের নেতাদের কী প্রত্যাশা ছিল, সেগুলো তাঁরা একটি সনদ আকারে নিজেরা প্রকাশ করেননি। তাঁরা অপেক্ষা করেছেন এই দায়িত্বটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য, যাদের সঙ্গে সে গণ-অভ্যুত্থান কিংবা রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সে কারণেই জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কিত ‘জুলাই সনদ’ ঘোষণা কিংবা নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়টি অনিশ্চিতভাবে ঝুলে রয়েছে। জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের কোনো কিছু উদযাপনের ক্ষেত্রেই কোনো গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে না। এ রকম একটি রাজনীতিগত দোদুল্যমান অবস্থায় কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থান আমাদের জীবনে কী পরিবর্তন এনেছে? যদি কোনো পরিবর্তন না-ই হয়ে থাকে, তাহলে দেশে ফ্যাসিবাদের পতন বা তাদের উত্খাত করা হলো কিভাবে? কেন এত বিশাল গণ-আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের এত আত্মত্যাগ? অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান বলেছেন, ‘অতীতের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী কিংবা ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন বদলাতে আমরা রাষ্ট্র মেরামতসহ সর্বত্র সংস্কার সাধনের যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি, সেগুলো আমাদের প্রস্তাবিত জুলাই সনদে স্থান পেতে হবে।’ দল-মত-নির্বিশেষে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে প্রস্তাবিত ঘোষণাগুলো বাস্তবায়িত করতে হবে। কিন্তু কী সে প্রস্তাবিত ঘোষণা, তা এখনো জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক দলই জানে না। বিএনপিসহ বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দলের নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনায়ই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বসা হয়নি। কারা কারা হবেন এই প্রস্তাবিত সনদে স্বাক্ষরকারী? এ পর্যন্ত তারও কোনো হদিস নেই। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দেশি-বিদেশি আধিপত্যকে প্রতিরোধ করে আমরা কিভাবে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করব—প্রস্তাবিত সনদে আমরা সে ব্যাপারে সবার সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি চাই।
লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gaziulhkhan@gmail.com
বাবনপুরে জেগে আছেন শহীদ আবু সাঈদ
- ড. মো. ফখরুল ইসলাম

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে জুলাই ২০২৪ মাসটি এক অনন্য মর্যাদার দাবিদার। এই মাসে বারবার রক্ত ঝরেছে, শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতার আহ্বানে কেঁপে উঠেছে শাসকের প্রাসাদ। সেই উত্তাল জুলাইয়ের সূচনা ঘটেছিল রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) মাটি রঞ্জিত করে আবু সাঈদ নামের এক শিক্ষার্থীর রক্তে। পীরগঞ্জের বাবনপুর নামক গ্রামে একটি বাঁশের বেড়া দেওয়া কবরে তিনি শুয়ে আছেন নীরবে, নিঃশব্দে।
রংপুরে শিক্ষার বাতিঘর হয়ে উঠেছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের অব্যবস্থাপনা, নিয়োগ বাণিজ্য, রাজনৈতিক দখল ও অবমূল্যায়নের কারণে নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বারবার পরিণত হয়েছে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরিতে।
 জুলাই বিপ্লব তাই কেবল রংপুরের বা বেরোবির নয়।
জুলাই বিপ্লব তাই কেবল রংপুরের বা বেরোবির নয়।
এই শহীদ যেন আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, বাংলাদেশে ছাত্ররাই বারবার যুগ পরিবর্তনের সূচনা করেন। হোক তা ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার সংগ্রাম কিংবা স্বৈরাচারবিরোধী লড়াই। আমরা চাই, এই শহীদের রক্ত বৃথা না যাক।
জুলাই বিপ্লবের এই প্রথম শহীদের স্মরণে রাষ্ট্র কি আরো একটু নত হবে, নাকি আবারও চলবে এড়িয়ে যাওয়ার নীলনকশা? যদি তা-ই হয়, তবে আগামী দিনগুলো আরো অস্থির, আরো উত্তাল হবে।
‘যেখানে বাধাগ্রস্ত হবে, সেখানেই জুলাইকে তুলে ধরতে হবে’—এই চেতনা দেরিতে এলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রযন্ত্রের চেহারার ভেতরে, যা দিন দিন হয়ে উঠছে আরো দুর্বিনীত, অসহনশীল ও জনবিচ্ছিন্ন। যখন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পাস করার পর চাকরির জন্য ঘুরে বেড়ান, তাঁদের দাবি উপেক্ষা করে, বিরোধিতা করে, এমনকি দমন করতে গিয়েই সরকার তার আসল চেহারা উন্মোচন করে। ঠিক এখানেই জুলাই এসে দাঁড়িয়েছিল প্রতিবাদের ভাষা হয়ে। এটি কেবল একটি মাস নয়, এটি একটি ধারণা, একটি রাজনৈতিক চেতনা, একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার নাম, যা শেখায় জুলুমের বিরুদ্ধে চুপ থাকা মানেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। তাই যখনই কোথাও প্রতিবাদ বাধাগ্রস্ত হবে, যখনই মত প্রকাশের অধিকার পদদলিত হবে, তখনই জুলাইকে তুলে ধরতে হবে প্রতিরোধের এক ছায়াছবির মতো।
বাবনপুরে শায়িত জুলাই বিপ্লবের প্রথম শহীদ, তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করে রাখা যায় না। তাই তাঁর মৃত্যু আর দশটি মৃত্যুর মতো নয়, বরং এটি এক বিস্মৃত সময়কে জাগিয়ে তোলার মুহূর্ত, যেখানে জুলাই আবার ফিরে এসেছে জনতার পাশে দাঁড়াতে।
এখন বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে, কর্মক্ষেত্রে, সংবাদমাধ্যমে, এমনকি সংসদের ভেতরেও যদি অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেখানেই জুলাইকে তুলে ধরতে হবে। কারণ এই মাস শেখায় শুধু স্মৃতিচারণা নয়, স্মৃতি দিয়ে বাস্তব পরিবর্তনের দাবিও তোলা যায়।
তাই আমাদের দায়িত্ব এই শহীদের মৃত্যু যেন অন্ধকারে হারিয়ে না যায়। রাষ্ট্র যদি কখনো ন্যায়ের পথ ছেড়ে নিপীড়নের দিকে হাঁটে, তাহলে প্রতিটি গ্রামে বাবনপুরের মতো একেকটি জুলাই জন্ম নিতে পারে।
এমন সময় হয়তো আবারও প্রশ্ন উঠবে, জুলাই-জুলাই বলে এত মাতামাতি কেন? আমরা তখন উত্তর দেব, এর কারণ আমাদের প্রতিবাদের জায়গাগুলো একে একে নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে। আর যেখানে হাতে মুষ্টি তুলে পথে নেমে সমস্বরে চিৎকার করা নিষিদ্ধ, সেখানে জুলাই-ই হয়ে উঠতে পারে একমাত্র ভাষা।
শহীদ আবু সাঈদের মৃত্যু কেবল একটি গুলি বা একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল না। এটি একটি সাবধানবাণীও ছিল। বেরোবির পার্কের মোড়ের অদূরে যা ঘটেছিল, তা ছিল আসলে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। যেখানে কথা বলা মানেই অপরাধ, দাবি জানানো মানেই রাষ্ট্রদ্রোহ মনে করা হয়েছিল।
সেদিন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন রাষ্ট্র কী করেছিল? তারা কেন সেদিন তাঁদের দিকে বন্দুক তাক করল? সেদিন যে তরুণ শহীদ হলেন, তিনি যেন গোটা বাংলাদেশের হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তৎকালীন ক্ষমতাধরদের কাছে তা অনুধাবন করা কি খুব জটিল বিষয় ছিল?
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রতিবাদের ঐতিহ্য খুব গর্বের। ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন—সবখানেই ছাত্রসমাজ পথ দেখিয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালে এসেও ছাত্রসমাজের কণ্ঠ রোধ করতে গুলি ব্যবহার করতে হয়, এটি কি রাষ্ট্রের দুর্বলতা নয়? আগামী দিনে আমরা এ ধরনের আর কোনো রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা ও ভয় দেখতে চাই না।
জুলাই বিপ্লবের এই প্রথম শহীদ শব্দটি যেন আমাদের সবার কাঁধে নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। এর মানে, আরো অনেক শহীদ আসতে পারেন, যদি রাষ্ট্র তার দমননীতি থেকে ফিরে না আসে। যদি কথা বলার জায়গা, ভিন্নমতের জায়গা একে একে নিঃশব্দ হয়ে যায়, তাহলে শেষ ভরসা হয় রক্ত। বেরোবির ইংরেজি পড়ুয়া অকুতোভয় ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের তাক করা বন্দুকের নলের সামনে বুক উঁচিয়ে গুলি খেতে দ্বিধাহীন না থাকলে আজ কী করতাম আমরা, তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?
জন্ম নিলেই সবাইকে একদিন না একদিন নির্বাক হতে হয়। কিন্তু সবার কথা কি সব মানুষের অনন্তকালব্যাপী মনে থাকে? শহীদ আবু সাঈদ বাবনপুরে শুয়ে আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন, দেশের যেকোনো প্রয়োজনে যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাক থাকার দিন শেষ।
লেখক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন
fakrul@ru.ac.bd