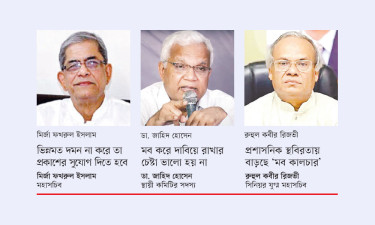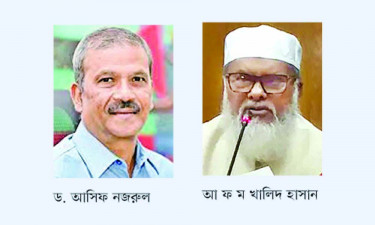আজকাল চিকিৎসক শ্রেণির সদস্যরাও দলবেঁধে হরতাল-অবরোধে শামিল হন। এক প্রকারের ট্রেড ইউনিয়নের সংস্কৃতি তাঁদের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। হরতাল-অবরোধ তাঁরা করছেন রোগীর অভিভাবকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে। সাংবাদিকদের রিপোর্টে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরা মারধরের ঘটনাও ঘটাচ্ছেন।
বারডেম, মিটফোর্ড এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার সাহেবদের ধর্মঘটের যে নমুনা দেখলাম, তাতে আমাদের এ কথা মনে হয়েছে, এখন ডাক্তারি আর আগের মতো মহৎ পেশা নেই। এখন ডাক্তারি নেহাতই অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য একটি ভালো পেশা। রোগীকে ফেলে ডাক্তাররা রাস্তায় নেমে পড়ে যেসব স্লোগান দিচ্ছেন, তাতে আমজনতার হতাশাই শুধু বৃদ্ধি পাবে। কোনো ডাক্তার ভুল চিকিৎসা করলে তো রোগী বা রোগীর অভিভাবকরা ক্ষিপ্ত হবেই।
অতি নিরীহ রোগীরা কোনো রকম উচ্চবাচ্য করে না। নালিশটা নীরবে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে ছেড়ে দেয়। তবে কোনটা ভুল চিকিৎসা বা কোনটা পেশাগত অবহেলা- এটা কে ঠিক করবে? যে ডাক্তার সাহেব ভুল চিকিৎসা করলেন, তিনি তো স্বীকারই করবেন না যে তিনি ভুল করেছেন। কথিত ভুল প্রকৃত অর্থে ভুল কি না সেটা শনাক্ত করতে পারত মেডিক্যাল ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
কিন্তু আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থায় এ পর্যন্ত ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা উদ্ঘাটন করে ডাক্তারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এমন উদাহরণ আমরা দেখিনি। আসলে নিয়োগদাতা কর্তৃপক্ষ কখনো তার অধীনে কর্মরত ডাক্তারকে ভুল চিকিৎসা-অপচিকিৎসার জন্য শাস্তি দেবে না। ওই কাঙ্ক্ষিত শাস্তি সনদ প্রদানকারী ডাক্তারদের কাউন্সিল বিএমডিসিও দেবে না। তারা যদি ভুল চিকিৎসা, অবহেলা এবং অপচিকিৎসার জন্য সনদপ্রাপ্ত ডাক্তার সাহেবদের শাস্তি দিতেন, তাহলে এত দিনে স্বাধীন বাংলাদেশে শত শত ডাক্তার জেল-জরিমানার সম্মুখীন হতেন। বিএমডিসির শাস্তির ক্ষমতা বোধ করি সনদ প্রত্যাহার পর্যন্তই। বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল বা বিএমডিসিও কার্যকর ছিল, যখন ডাক্তার উৎপাদনের সংখ্যাটা অনেক সীমিত ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে যাঁরা পাস করে বের হতেন, তাঁদের চিকিৎসা করার সনদ দিত বিএমডিসি। কিন্তু এখন মেডিক্যাল শিক্ষার অবস্থাটা কী? আমরা তো তদবিরের কাছে আত্মসমর্পণ করে যত্রতত্র মেডিক্যাল কলেজ খুলে সেগুলো থেকে এমবিবিএস ডাক্তার উৎপাদনের অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। এখন মেডিক্যাল শিক্ষার মান নিয়ে জনগণ উদগ্রীব। শিক্ষিত ডাক্তার আর অশিক্ষিত ডাক্তার বোঝার ক্ষমতা প্রায় রোগীরই নেই। ডাক্তার সাহেব ওই ওষুধই লিখছেন, যে ওষুধ লেখার জন্য ওষুধ কম্পানি বাড়তি অর্থ ব্যয় করছে। ওষুধ দরকার একটা, ডাক্তার সাহেব লিখছেন তিনটা। কারণ বেশি ওষুধ লেখার মধ্যে তাঁর স্বার্থ আছে। ফলে আজকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগেই রোগী একরাশ সন্দেহ মাথায় করে যায়। সন্দেহগুলো হলো- ডাক্তার সাহেব তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কি না, না শুনে-আধা শুনে অনেক ওষুধ লিখে দেবেন কি না, অনেক ল্যাবটেস্ট দিয়ে বলবেন, রিপোর্টসহ আগামী সপ্তাহে আসুন, এসব। যে রোগী যে ডাক্তারকে বিশ্বাস করল না, সেই ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে রোগীর রোগ ভালো হবে কি? ডাক্তার অনেক আছেন। তবে ভালো ডাক্তারের সংখ্যা অতি নগণ্য। অধ্যাপক পদের ডাক্তার হলেই যে ভালো ডাক্তার হবেন, তাও নয়। কারণ আজকে অধ্যাপকও ধরাধরি বা তদবির করে হওয়া যায়। অনেক সময় অল্প ডিগ্রির ডাক্তারও ভালো ডাক্তার, আবার অনেক বড় ডিগ্রির ডাক্তারও ওয়াকফ ডাক্তার। যা হোক, রোগীকেই বুঝতে হবে কে ভালো ডাক্তার, কে মন্দ ডাক্তার। রোগীকে মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে অন্যদের মতো ডাক্তার সাহেবদেরও বিচ্যুতি ঘটেছে। বিচ্যুতিটা বেশি ঘটেছে ওষুধ কম্পানিগুলোর অতি ওষুধ বিক্রি করে অতি মুনাফা করার প্রবণতা থেকে। ডাক্তার সাহেবরা ওষুধ কম্পানিগুলোর মুনাফা অর্জনের বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছেন। এটা তো সত্য, আমাদের ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন-হাসপাতাল-ল্যাবটেস্ট ইত্যাদি হলো রোগীকে আরো রোগী অথবা ভালো মানুষকে রোগী বানানোর বড় হাতিয়ার। এই তিন পক্ষ মিলে বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার নতুন রোগী উৎপাদন করছে। কি, বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাসটা হতো, যদি একটি স্বাধীন কমিশন করে বাংলাদেশে রোগী চিকিৎসার গোটা ব্যবস্থাটি পরীক্ষা করা যেত। ডাক্তারদের সম্পর্কে রোগীর অভিযোগ কী? অভিযোগ হলো তিনটি। এক. সময় নিয়ে ডাক্তার সাহেব রোগী দেখেন না বা রোগীর কথা শোনেন না। অনেক সময় না শুনেই ওষুধ লেখা শুরু করেন। দুই. তিনি বেশি ল্যাবটেস্ট দেন। তিন. তিনি ভুল চিকিৎসা করে রোগীর ক্ষতি করেছেন। অথবা ভুল চিকিৎসা ও অবহেলার জন্য রোগীর রোগ আরো বেড়েছে বা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে তদারকি করার জন্য আমাদের দেশে স্বাধীন কোনো কর্তৃপক্ষ আছে কি? ডাক্তার সাহেবরা যে স্বাধীনতা ভোগ করছেন, তাঁদের প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ওই রকম স্বাধীনতা বিশ্বের কোথাও নেই। বিশ্বের কোথাও রোগীকে এত ওষুধ খাওয়ানো হয় না। আপনারা যাঁরা সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক গিয়েছেন, রাস্তায়-অলিতে-গলিতে এত ওষুধের দোকান দেখেছেন কি? এত ব্যথার ওষুধ কোনো দেশে বিক্রি হয়? কিংবা এত গ্যাসের ওষুধ কোনো দেশের লোক সেবন করছে? আমাদের হাসপাতালগুলোর অবস্থা কী? রোগীরা কি সেখানে যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে? এত লোক দেশে রোগী হচ্ছে কেন- সেই প্রশ্নটাও কাউকে করতে দেখা যায় না। যে পদ্ধতিতে এবং যে কারণে দেশের মানুষ রোগী হচ্ছে, তাতে দেশের সব মানুষ রোগী হয়ে গেলেও অবাক হব না। কারণ হলো, যে ডাক্তার রোগীর রোগ সারাবেন, তিনি যদি রোগীকে আরো রোগী বানান, তাহলে দেশে রোগীর সংখ্যা কমবে কেন? সর্বত্র অর্থ ঢুকে পড়েছে, সবাই যেন অর্থের কাছে দাস হয়ে গেছে। ফলে রোগীর লোকেরা যতই ডাক্তার পেটান, তাতে কোনো শুদ্ধতা কোথায়ও আসবে না। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারত, সরকার যদি চিকিৎসা ও হাসপাতাল ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার জন্য একটা স্বাধীন কমিশন বা কর্তৃপক্ষ গঠন করত। এই কমিশনই নির্ধারণ করত কোনটা অবহেলা, কোনটা ভুল চিকিৎসা। ভুক্তভোগীরাও ওই কমিশনের কাছে গিয়ে নালিশ করতে পারত। ওই ধরনের কমিশন গঠন করতে নতুন করে আইন পাস করতে হবে। আইনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং প্রতিষ্ঠিত কমিশনই কেবল হাসপাতাল ও ডাক্তারি ব্যবসাকে তদারকির মধ্যে আনতে পারবে।
লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়