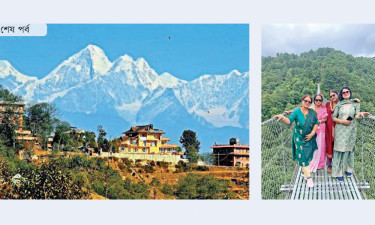দূর অতীতের গ্রিকরা যথার্থই বলেছিলেন, 'The good die young' ভালো মানুষরা তরুণ বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন। আসলে ভালো মানুষ বুঝি কখনোই জরাগ্রস্ত, কালজীর্ণ হতে পারেন না। তাঁরা মনে ও চেতনায় সব সময়ই তরুণ থাকেন। লোকসংগীতের কথায় তাঁদের বয়স বাড়ে না, বরং কমে।
নিটোলকালের মায়াবী কন্যা
ড. মীজানূর রহমান শেলী

২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতায় যখন তাঁর লোকান্তর ঘটে, তখন জাগতিক হিসাবের অঙ্কে তাঁর বয়স ছিল ৮২ বছর। কিন্তু তাঁর প্রয়াণের পরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য গুণগ্রাহীর মনে তাঁর যে ছবি উজ্জ্বল রেখায় বর্ণিল হয়ে ওঠে, তা চিরন্তন রোমান্টিকতায় ঘেরা এক তরুণীর। অতুলনীয়, অপূর্ব চিত্রনায়িকা হিসেবে তাঁর কর্মজীবন ছিল তুলনামূলকভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্য।
কিন্তু যে ক্ষণ থেকে তিনি সর্বসাধারণের চোখের আড়ালে চলে গেছেন তাঁর অপরূপা প্রতিকৃতি সেই ক্ষণের আদলেই চিরঞ্জীব রয়ে গেছে। তাই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে চিরতরে চলে যাওয়ার পরও সুচিত্রা সেন রয়ে গেছেন উনিশ শ পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের বাংলা ছায়াছবিজগতের রোমান্টিক রাজকুমারী। না, শুধু চলচ্চিত্রজগতেই নয়, সারা বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি ছিলেন রোমান্টিক মন ও মননের অবিসংবাদিত মহানায়িকা।
বাংলাদেশের পত্রিকান্তরে যথার্থই লেখা হয়েছে, 'গত শতাব্দীর পঞ্চাশ, ষাট আর সত্তরের দশক বাংলা চলচ্চিত্রজগৎ হয়ে রইল সুচিত্রাময় এবং অবধারিতভাবেই উত্তমময়।
এর পরের গল্প তো ইতিহাস। রোমান্টিক জুটি হিসেবে দাঁড়িয়ে যাওয়া সুচিত্রা-উত্তম এগিয়ে গেলেন শাপমোচন, সবার উপরে, সাগরিকা, শিল্পী, হারানো সুর, পথে হলো দেরী, সপ্তপদীর পথ ধরে। উত্তমকে ছাড়াও বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দীপ জ্বেলে যাই, অশোক কুমারের সঙ্গে হসপিটাল কিংবা সৌমিত্রের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা করে সুচিত্রা বুঝিয়ে দিলেন অভিনয়ের ক্যারিশমাটা জানা আছে তাঁর- শুধু উত্তম-সুচিত্রা রসায়নেই যা শেষ হওয়ার নয়। আর হিন্দিজগতে দিলীপ কুমার, দেব আনন্দ, অশোক কুমার, ধর্মেন্দ্র ও সঞ্জীব কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেও তো বুঝিয়ে দিলেন, তিনি চলচ্চিত্রজগতে আগন্তুক নন। টিকে থাকার জন্যই এসেছেন।
তাই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাণীচিত্রের জগতে সুচিত্রা সেন ছিলেন নিজেই নিজের অনুপম উপমা। কিন্তু বস্তুত তাঁর জীবন ও শিল্পকর্মের দ্যোতনা এবং আবেদন ছিল আরো বিশাল। যে কালে তিনি শিল্প-সংস্কৃতির আঙিনায় কেন্দ্রীয় এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, সেই কালেরই তিনি ছিলেন এক নিটোল ও অসাধারণ প্রতীক। উনিশ শ পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের বিশ্ব, উপমহাদেশ এবং দুই বাংলার জন্য এক তুফান-তাড়িত কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী রেশ তখনো শেষ হয়নি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান আর উপমহাদেশ এবং এর ফলে বঙ্গ বিভক্তির যন্ত্রণাসিক্ত, বেদনার্ত অভিঘাত যেমন জনজীবনকে, তেমনি সুচিত্রা সেনের জীবনকেও আঘাত করেছিল। স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর মা-বাবা, ভাইবোনসহ তাঁকে বাংলাদেশের আদি নিবাস পাবনা থেকে চলে যেতে হয়েছিল অপরিচিত কলকাতায়। তাই তাঁর জন্য যেমন, তেমনি পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের বাঙালির জন্যও সময়টা ছিল নতুন ধাঁচের জীবনের এবং উদ্ভিন্ন ও বিকশিত তারুণ্যের কাল। এ কথা তৎকালীন পূর্ব বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমনি ভারতের পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেও।
স্মরণ রাখা দরকার, উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে নব সৃষ্ট পাকিস্তানের দূরস্থিত প্রদেশ হিসেবে পূর্ব বাংলা, পরে পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ওপার বাংলা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল না। যাতায়াত বা যোগাযোগব্যবস্থা বিভক্তি ও এর থেকে সৃষ্ট তিক্ততার ফলে আজকের মতো সহজ ছিল না। রাষ্ট্র দর্শনের ভিন্নতার কারণে পাকিস্তান ও ভারতের যে তফাত, তা বাংলাকে প্রভাবিত করলেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুই দ্বীপে রূপান্তরিত করতে পারেনি। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ ও একাত্মতা প্রায় অক্ষুণ্ন ছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। ভারতীয় বাংলা ছবি এবং সেই সঙ্গে হিন্দি ছবিও পূর্ব বাংলার প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত দেখানো হতো। দর্শকরাও বিপুল সংখ্যায় সেসব জনপ্রিয় ও হৃদয়নন্দন ছায়াছবি দেখতে যেত। টেলিভিশন, ভিসিআর আর কেব্ল্ টিভির উপস্থিতি ছিল না তখন। তাই চলচ্চিত্র ছিল মধ্যবিত্তসহ বাঙালি জনসাধারণের প্রধান বিনোদন। সেই পটভূমিতেই পঞ্চাশের দশক থেকে সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম বাংলায় প্রবাসী সুচিত্রা অভিনীত ছবিগুলো দর্শকসাধারণের হৃদয় জয় করে নেয়। সেটা ছিল আমাদের কৈশোর, প্রথম এবং পরিণত তারুণ্যের কাল। সেই সময়ের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এবং পরিণত বয়স্করাও সুচিত্রা-উত্তমের নন্দিত জুটির ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। সুচিত্রা হয়ে ওঠেন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিমনস্ক পুরুষের স্বপ্নকন্যা, নারীদের রোমান্টিক যৌবনের আদর্শ প্রতীক। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ১৯৪৭ বা তার আগের উপমহাদেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাষ্ট্র বিভক্তির কারণে এই স্বপ্নের আবেশ ব্যাহত হতে পারেনি। মুসলিমপ্রধান বাংলার মানসে স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকলেও তা সুচিত্রা অভিনীত ছবিগুলোর আকর্ষণ ও আবেদন ম্লান করতে পারেনি। রোমান্টিকতার রাজকুমারী রূপ-লাবণ্যের প্রবল আকর্ষণ এবং তাঁর অভিনয় শৈলীর অপূর্ব আবেদনই শুধু নয়, বাঙালি জীবনের বিভিন্ন শ্রেণী, স্তর এবং অংশ নিয়ে যেসব অনবদ্য কাহিনী রুপালি পর্দায় ফুটে উঠত, তার সীমান্তজয়ী ও কালোত্তীর্ণ আবেদন সুচিত্রা অভিনীত চলচ্চিত্রের বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে কাজ করে। সেদিক দিয়ে তাঁর অভিনীত ছবিগুলোয় ছায়াছবির মাধ্যমে সুচিত্রা হয়ে ওঠেন দুই বাংলার সেই যুগের প্রাণভ্রমরা। তাঁর ছবিগুলো প্রজাপতি পাখায় পরিস্ফুটিত ছিল সে যুগের সরল ও সুন্দর মনোভঙ্গি ও মূল্যবোধ। সেগুলোর মধ্যে ছিল না মেকি চাকচিক্য, মমতারিক্ত অর্থলোভ এবং আড়ম্বর ও জৌলুস। সেই সরল নিটোল জীবনধারায় প্রাণভ্রমর যে হঠাৎ বিবাগী হয়ে যাবে তা কারো জানা ছিল না।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন :
'নিশীথ নীল পদ্ম লাগি
ভ্রমর যেথা হয় বিবাগী'
সুচিত্রা সেনের জীবনের শেষ অধ্যায় রহস্যাবৃত। ১৯৭০ সালে তাঁর শিল্পপতি স্বামী দিবানাথ সেনের মৃত্যুর পরও ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে যান। তাঁর স্বামী তাঁকে অভিনয়জীবনে সংশ্লিষ্ট হতে প্রথম দিকে সাহায্য-সহযোগিতা করলেও পরে এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য ও মতানৈক্য হয় বলে পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হয়। তা ছাড়া অসমর্থিত অনেক প্রতিবেদনই তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে বিঘ্ন ঘটার কারণ হিসেবে উত্তম কুমারের সঙ্গে সুচিত্রার কথিত ঘনিষ্ঠতার কথাও উল্লেখ করা হয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর বেশ আগে থেকেই সুচিত্রা পৃথকভাবে বসবাস করেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর শেষ ছবি 'প্রণয়পাশা' ফ্লপ করার পর তিনি আকস্মিকভাবে অভিনয়জীবনের ইতি টানেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি চলে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে। মহানগরী কলকাতার জনারণ্যেও তিনি জীবন কাটান নিঃসঙ্গ-নির্জন দ্বীপের মতো। একমাত্র পরিবারের লোকজন, হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং আধ্যাত্মিক গুরু ও সহযোগীরা ছাড়া কেউ তাঁর দেখা পাননি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর। এই প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে দুইবারই মাত্র তিনি জনসমাগমে পূর্ণ কোনো জায়গায় যান- একবার যখন সহকর্মী উত্তম কুমারের মৃত্যু হয়, আরেকবার যখন প্রয়াত হন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু। নির্জনবাসের কালে তিনি একান্তে আরাধনা করতেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রতে সক্রিয় ছিলেন বলেও জানা যায়।
এসবই সুচিত্রাকে পরিণত করে আরেক কুহেলিকাময়ী রহস্যাবৃত নারীতে। যেমন অতুলনীয় রোমান্টিক নায়িকা হিসেবে, তেমনি দৃঢ় সংকল্প এক সংসারী-তাপসী হিসেবে তিনি অনিঃশেষ বিস্ময়ের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। কী ছিল তাঁর শেষ প্রশ্ন, তা হয়তো কেউ কোনো দিনও জানবে না।
লেখক : চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, বাংলাদেশের (সিডিআরবি) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং আর্থসামাজিক ত্রৈমাসিক 'এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স'-এর সম্পাদক
সম্পর্কিত খবর