জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু প্রাপ্তি চেতনে ও অবচেতনে? গত এক বছরের সংস্কার একটি বহুল শ্রুত শব্দে পরিণত হয়েছে। মানুষ এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে কিভাবে দেখতে চেয়েছে। চব্বিশের মূল দর্শন ক্রীড়াঙ্গনের ক্ষেত্রে হলো নারী-পুরুষে বৈষম্যের অবসান, গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে সংগঠকদের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার। আর এটি অগ্রাধিকার নির্ণয় করে; কেননা সংস্কার তো একটি চলমান বিষয়, এটি ছাড়া তো ক্রীড়াঙ্গন অচল ও অকার্যকর হতে বাধ্য।
ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থান সুযোগ করে দিয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও স্বেচ্ছাচারিতা ও দমনমূলক ঐতিহ্য ভাঙার। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্রেফ একটি রেজিম চেঞ্জ নয়; এর দর্শন অন্য রকম। এর চেতনার পরিধি অনেক বড়। আমরা বারবার বলেছি, ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিবেকের সংস্কার।
মানুষ তো কেবল তার স্বপ্নের সমান। সে আশা করে, অপেক্ষা করে। বাস্তবতার জমিনে দাঁড়িয়ে যদি আমরা সঠিকভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে আত্মস্থ করতে পারতাম, তাহলে আগামী দিনে আমরা অনেক বেশি স্বপ্ন দেখতে পারতাম। তবে ক্রীড়াঙ্গনে একটি ঝাঁকুনি দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
ট্র্যাডিশনের বিপক্ষে দাঁড়ানো হয়েছে, এটি কম বিষয় নয়। ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক বডি গঠন করা হয়েছে। ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা আগের তুলনায় কমানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে—যাঁদের নিয়ে ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক বডি গঠন করা হয়েছে, তাঁরা আসলে কারা? কী তাঁদের ‘ব্যাকগ্রাউন্ড’? তাঁরা কি নিজ থেকে প্রো-অ্যাকটিভ হওয়ার মতো মানসিকতাসম্পন্ন?
ক্রীড়াঙ্গনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠকরা যদি খেলাকে ভালোবেসে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে সবাই মিলে লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে বিভিন্ন খেলা দারুণভাবে ‘সাফার’ করবে। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে কাজ করানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তো নেই।
সবাই তো প্রবল উৎসাহ নিয়ে, সবকিছু বুঝেশুনেই দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। অ্যাডহক কমিটি হয়েছে। এবার ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে সংস্কার সাধনের জন্য নতুন কমিটি করা হয়েছে। কাগজে দেখেছি, এই কমিটিতে স্থান হয়েছে এমন একজন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে চলে গেছেন। সেখানে বৈধভাবে তাঁর থাকার ব্যবস্থা আছে। আমরা চাচ্ছি ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের নামে খেলাধুলা যাতে স্থবির না হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময়ের জন্য বাধাগ্রস্ত না হয়।
বর্তমানে পুরো দেশে সার্বিক ক্রীড়াঙ্গনের অবস্থা মোটেই ক্রীড়াবান্ধব নয়। অপ্রিয় শোনালেও এটাই বাস্তবতা। ব্যক্তিস্বার্থ থেকে ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থকে বড় করে দেখতে না পারলে ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তনের সুফল পাওয়া যাবে না। জোড়াতালি আর ধামাচাপা দিয়ে ক্রীড়াঙ্গন চলবে না। এ ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলো আমলে রাখতেই হবে। ক্রীড়াচেতনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্রীড়াঙ্গনে আস্থা ও বিশ্বাসের বিকল্প নেই। মানুষ এখন ক্রীড়াঙ্গনকে অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছে। তারা ক্রীড়াঙ্গনের মধ্যে দেশকে দেখতে চায়। দেখতে চায় জাতিচরিত্রের প্রতিফলন। ক্রীড়াঙ্গনের সবকিছু স্পষ্ট হওয়া উচিত। আমরা অনেক বেশি আশা করেছি—ভাবা হয়েছে, আমরা একবারে সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলব। এটি কিন্তু সম্ভব নয়। সমস্যার পরিধি তো ব্যাপক। সবাই লক্ষণ নিয়ে ভাবছেন, মূলের দিকে তাকাচ্ছেন না। ক্রীড়াঙ্গন বোঝাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
ক্রীড়াঙ্গনে যেমন অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখার সুযোগ নেই, তেমনি সুযোগ নেই অতীতকে অস্বীকার করার। খেলার চর্চা একটি লম্বা সফর। এই সফরে আছে টিমের নিরলস চেষ্টা। আছে সফলতা, ব্যর্থতা আর সীমাবদ্ধতা। খেলার চর্চাকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, এটি দরকারি বিষয়। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন এবং সাফল্যের স্বাদ পেতে পারেন, যদি তিনি যা করছেন তার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও সত্যিকারের আন্তরিক হন।
একসময়ের ‘ঢাকা স্টেডিয়াম’-এর নাম বদল করে ১৯৯৬ সালে নতুন নামকরণ হয়েছে। এরপর আবার চলতি বছর (২০২৫) সেই স্টেডিয়ামের নামকরণ হয়েছে ‘জাতীয় স্টেডিয়াম’। এটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এই স্টেডিয়াম সুস্থভাবে ক্রীড়াচর্চার মাধ্যমে প্রাণচঞ্চল হচ্ছে কি না এটি গুরুত্বপূর্ণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো স্টেডিয়ামের সঠিক ব্যবহার, এর রক্ষণাবেক্ষণ। ‘মেইন সাবজেক্ট’ থেকে ‘ঐচ্ছিক সাবজেক্ট’ তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবেগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু আবেগ দিয়ে ক্রীড়াঙ্গন চলে না।
ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে শূন্যে বুলি আর আশ্বাসের বাণী শোনানোর দিন এখন আর নেই। সচেতনতা বেড়েছে। বেড়েছে সাদা-কালো বোঝার ক্ষমতা। এরই মধ্যে অনেক বেলা হয়ে গেছে। মানুষ এখন দেখতে চায় কল্যাণমুখী ক্রীড়াঙ্গন। দেখতে চায় ন্যায়ভিত্তিক সমতার ক্রীড়াঙ্গন। দেখতে চায় উপেক্ষা আর অবহেলার অবসান। ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের খেলা বন্ধ হওয়া দরকার। দরকার সুবিধাভোগীদের খপ্পর থেকে ক্রীড়াঙ্গনকে মুক্ত করা।
ক্রীড়াঙ্গনে সমস্যা হলো নীতিতে সমন্বয়হীনতা ও নেতৃত্বের অভাব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চিন্তার জগৎ সেই পুরনো দিকেই থেকে গেছে। জীবন কিংবা খেলাধুলা তো রূপকথার গল্পের মতো নয়। অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যেতে হবে। মেনে নিতে হবে। একে অপরকে দোষারোপ করে, একে অপরকে হিংসা করে বিরুদ্ধাচরণ ও অভিযোগ উত্থাপন করে তো সমস্যার সমাধান হয় না। প্রয়োজন যে খেলাই হোক না কেন, সেই খেলার স্বার্থে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ও ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে কাজ করা।
আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে হওয়া উচিত একটি উদ্দেশ্য নিয়ে টেকসই মডেল, যা কাঠামোগত সমস্যার সমাধান করে এবং সবার জন্য ক্রীড়াঙ্গন নিশ্চিত করবে। পদে পদে ক্রীড়াঙ্গনে সব সময় বড় বেশি অজুহাত। ক্রীড়াঙ্গনের ভালো চাইলে, ক্রীড়াঙ্গনকে যুগোপযোগী করতে হলে প্রয়োজন জিরো অজুহাত নীতিতে কাজ করা। আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে উদ্ভাবনী শক্তিটা সত্যি দুর্বল। একটি ধারণা আরেকটি ধারণার জন্ম দেয়। উদ্দেশ্য নিয়ে যখন উদ্ভাবন হয়, তখন তাতে আসে স্থায়ী পরিবর্তন। ক্রীড়াঙ্গনে সাময়িক আত্মতৃপ্তি বলতে কিছু নেই।
খেলাধুলায় নেতৃত্ব বিকাশে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। সার্চ কমিটি কাজ করতে গিয়ে সেটি লক্ষ করেছে। তবে সমস্যার সমাধানে তারা আশাব্যঞ্জক কাজ করতে পেরেছে, এটি বলার সুযোগ নেই। ক্রীড়াঙ্গনে উন্নয়নের সুফল পেতে হলে তৃণমূল থেকে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের সেদিকে নজর কম। খেলোয়াড় তো জন্মায় না, সৃষ্টি করতে হয়; আর সেটি একেবারে এন্ট্রি লেভেল থেকে। এই যে আমাদের নারী ফুটবলাররা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে দেশের মানুষকে গর্বিত করেছেন, পাশাপাশি ফুটবলে নতুন সম্ভাবনার বড় দরজা খুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন, এর পেছনে আছে একটি ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন মেয়েরা। কিভাবে ফুটবলে তৃণমূল থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন। দেশজুড়ে প্রাইমারি স্কুল পর্যায়ের ফুটবল মেয়েদের ক্রীড়াঙ্গনে এনেছে।
ক্রীড়াঙ্গনে দায় স্বীকার করে নেওয়ার সংস্কৃতির প্রয়োজন। ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিদিনের আলোচনা ও গল্পে স্বস্তি বিরাজ করুক। ক্রীড়াঙ্গনে বাস্তবতার পৃষ্ঠপোষকতা হোক। ক্রীড়াঙ্গন ঘিরে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার জগৎ বড় হোক।
লেখক : কলামিস্ট ও বিশ্লেষক। সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি, এআইপিএস এশিয়া। আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন। প্যানেল রাইটার, ফুটবল এশিয়া।

 আমাদের জমায়েত হওয়ার স্থান ছিল তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক ও হাবিব ব্যাংকের সামনে (এখনকার জনতা ব্যাংক ও কনকর্ড টাওয়ার)। স্বাধীনতার জন্য আবাল-বদ্ধৃ-বনিতা সবার মধ্যেই দেখতাম উন্মাদনা।
আমাদের জমায়েত হওয়ার স্থান ছিল তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক ও হাবিব ব্যাংকের সামনে (এখনকার জনতা ব্যাংক ও কনকর্ড টাওয়ার)। স্বাধীনতার জন্য আবাল-বদ্ধৃ-বনিতা সবার মধ্যেই দেখতাম উন্মাদনা।

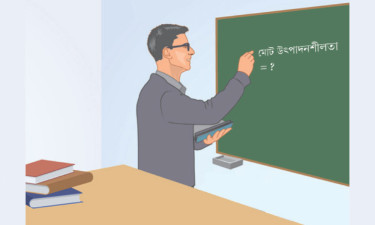
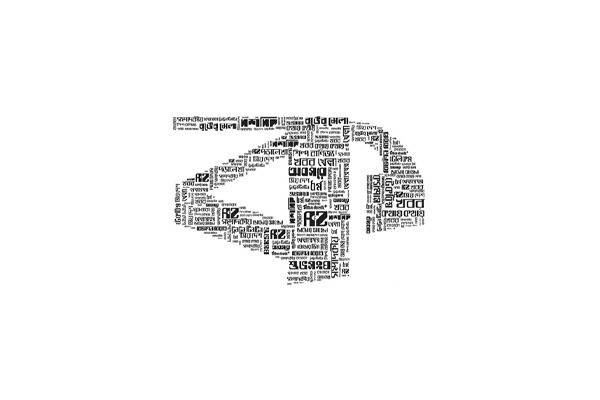



 এখানে ট্রাম্পের ভূমিকা অনেকের কাছেই হাস্যকর মনে হবে। তিনি যতই নিজেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক বলে প্রমাণ করতে চান না কেন, এটা কারো বুঝতে বাকি নেই যে মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে ইসরায়েলের কথাই শেষ কথা। তিনি কি এ কথা বুঝতে পারছেন না যে ইসরায়েল কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করে যাচ্ছে? এইতো কদিন আগে নেতানিয়াহু হোয়াইট হাউসে এসেছিলেন। ট্রাম্প ভেবেছিলেন যে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে সম্মত এবং এই সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তিনি নেতানিয়াহুর কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে শুধু একটি ঘোষণা দেবেন।
এখানে ট্রাম্পের ভূমিকা অনেকের কাছেই হাস্যকর মনে হবে। তিনি যতই নিজেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক বলে প্রমাণ করতে চান না কেন, এটা কারো বুঝতে বাকি নেই যে মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে ইসরায়েলের কথাই শেষ কথা। তিনি কি এ কথা বুঝতে পারছেন না যে ইসরায়েল কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করে যাচ্ছে? এইতো কদিন আগে নেতানিয়াহু হোয়াইট হাউসে এসেছিলেন। ট্রাম্প ভেবেছিলেন যে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে সম্মত এবং এই সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তিনি নেতানিয়াহুর কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে শুধু একটি ঘোষণা দেবেন।