ফেব্রুয়ারি মাস এলে দুটি ঘটনা ঘটে। একুশের চেতনা কারো কারো চিত্তে এমন চাঞ্চল্য তৈরি করে যে এই মাসে পুরোপুরি বাঙালি। বাংলায় কথা তো বলেনই, পারলে বাংলায় হাসেন। সম্ভব হলে বাংলায় কাঁদেন।
বাংলা চাই, ইংরেজি চাই, আরো চাই...
- মোস্তফা মামুন
অন্যান্য
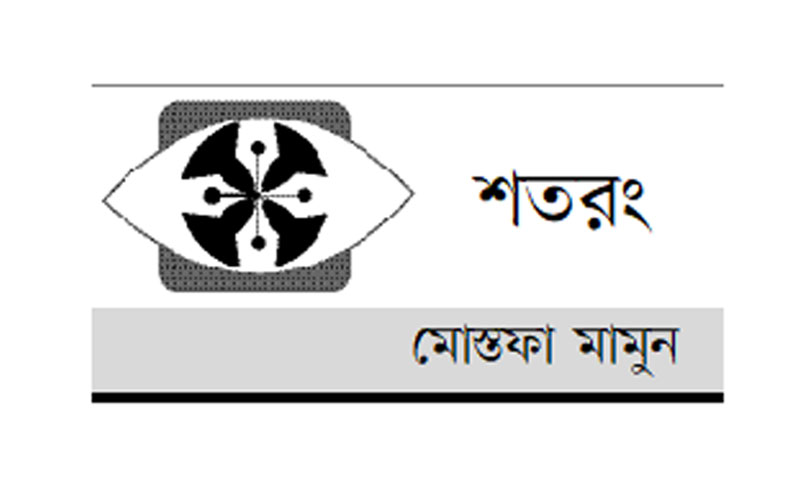
দ্বিতীয় পক্ষটা বুদ্ধিজীবীসুলভ উদাসীনতায় বলে, এ সবই বাড়াবাড়ি। এক মাসে বাংলা নিয়ে লাফালাফি কেন! বছর তো মাসের, তখন থাকেন কোথায়? এই ধরনের মৌসুমি বাংলাপ্রেমীর জন্য আজ বাংলার এই অবস্থা।
দুই মত চালু হওয়ার একটা কারণ প্রায় সব কিছুতেই আমাদের বহু মত।
যোগ্য মর্যাদা বিষয়টিও একটু গোলমেলে। আমার পরিচিত এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রনেতা সব সময় মনে করতেন, তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। যাঁদের মধ্যে এমন খুঁতখুঁত থাকে, তাঁরা সত্যিই সমস্যায় পড়েন। হয়তো কোনো জায়গায় তিনটি চেয়ার, দেখা গেল তাঁর চেয়ারটারই পায়া ভাঙা।
তো একবার আমরা ঠিক করলাম, তাঁকে একটা বিরাট সম্মান দেব। পুষিয়ে দেব বেচারার সারা জীবনের আফসোস। জন্মদিনের দিন রাত ১২টা ১ মিনিটে সারপ্রাইজ দিয়ে বিরাট কেক কাটা হলো। হাতে তুলে দেওয়া হলো উপহারের সুদৃশ্য প্যাকেট। তিনি এই সম্মান প্রাপ্তিতে আবেগাপ্লুত হয়ে গেলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘যা চেয়েছি তার চেয়ে বেশি পেয়েছি।’ এরপর প্যাকেটটা খুললেন। তাতে একটা বই। বইয়ের নাম, ‘যোগ্য মর্যাদা পেতে হলে যা করতে হয়!’
আমাদের এই নিষ্ঠুর রসিকতায় তিনি হতভম্ব। যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হলো, না অমর্যাদা করা হলো—বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।
আমাদের সব ক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদার বিষয়টাই এমন। কী রকম মূল্যায়ন পাওয়া উচিত এটা বেশির ভাগই বুঝতে পারি না বলে যোগ্য মর্যাদা নিয়ে হৈচৈ করি। তাতে বাড়ে বাড়াবাড়ি। এর চাপে আসল বিষয়টা হাঁসফাঁস করে। মূল শিক্ষাটা শিকেয় ওঠে।
এই ফেব্রুয়ারিতে বাংলার এত রব ওঠে; কিন্তু সেই গান, স্লোগান আর মুখস্থ সব বক্তৃতায়ই সব শেষ। অথচ একটি প্রজন্ম যে বাংলা শিক্ষায় নিরুৎসাহ হয়ে উঠছে, সে নিয়ে কোনো ভাবনা আছে! এই সামাজিক প্রবণতাও বিশ্লেষণ জরুরি—কেন বাক্যে কয়েকটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার স্মার্টনেসের সংজ্ঞা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে বাংলা শেখা মানে নিচের স্তরে রয়ে যাওয়া—এ রকম অসম্মানজনক তত্ত্বের চর্চা চলছে রীতিমতো। আর ওদিকে আমরা বাংলা-বাংলা ঢোল বাজাই। এই ঢোলটা তাই ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা গাড়ির হর্নের মতোই অসহ্য ও যন্ত্রণাময়। অথচ ফাঁকা আওয়াজ বাদ দিয়ে দরকার পুরো ভাষাশিক্ষা ভাবনাকে নতুন করে বিন্যস্ত করা।
আরেকটি গল্প বলি। বুঝতে সুবিধা হবে। মধ্যপ্রাচ্যের এক দেশে যাচ্ছিলাম। সঙ্গী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া চোস্ত ইংরেজিভাষী একজন। সেই সূত্রে যাত্রাপথে খুব খাতির পেল সে। এয়ারহোস্টেসদের সঙ্গে খাতিরও হয়ে গেল বেশ। কিন্তু সে দেশে পৌঁছার পর একটু সমস্যা। ওর এই কঠিন ইংরেজি স্থানীয় আরবরা খুব ভালো বুঝতে পারে না; বরং ওর চেয়ে আমার সাধারণ ইংরেজিতেই কাজ হয় বেশি। ‘আই গো’, ‘ইউ কাম’ দিয়ে কাজ হচ্ছে দেখে সে বেচারা হতবাক। একই ঘটনা ঘটবে আপনি যদি ইউরোপে যান। ইংল্যান্ড ছাড়া বাকি ইউরোপ ইংরেজি খুব একটা জানে না, জানলেও বলতে চায় না, সেখানেও ‘আই গো’, ‘ইউ কাম’ই বেশি কাজের। চীন-জাপান, লাতিন আমেরিকা বা আফ্রিকার ফ্রেঞ্চ-ইতালিয়ান কলোনিতে গেলেও ঘটবে একই ঘটনা। এই দেখে শিক্ষা হয়েছে—আমরা যে মনে করি, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লেই পুরো দুনিয়ার সবার সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে তাতে কত ভুল। সেই ভুলটা অনুভব করে পাল্টা চিন্তাও প্রবাহিত করা জরুরি। ইংলিশ মিডিয়াম যত না জরুরি, বিদেশের সঙ্গে তার চেয়ে বেশি জরুরি ইংরেজি ভাষাটাতে যোগাযোগ করার সাধারণ ক্ষমতা। আর সেটা খুবই সম্ভব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। সেখানে ‘স্পোকেন ইংলিশে’ গুরুত্ব দিলেই দূর হয়ে যায় অনেক বড় বাধা। ইংলিশ মিডিয়ামের প্রাবল্যে পরের প্রজন্ম যে দেশের সংস্কৃতিবিমুখ হয়ে যাচ্ছে সেই সমস্যা অনেকটাই দূর হয়। মা-বাবা যদি বুঝতে পারেন, সাধারণ স্কুল থেকেই তাঁর সন্তান প্রয়োজনীয় ইংরেজিটা শিখে নেবে; তাহলে ধারদেনা করে, খরচের পাহাড়ে ডুবে সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে ছুটবে না।
আমাদের শিক্ষায় ইংরেজি আছে। একটু বেশি ভালোভাবেই আছে। আমাদের ইন্টারমিডিয়েটে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে যে কঠিন গ্রামারের প্রশ্ন আসে এতে ইংরেজিভাষী দেশের অনেকেই ফেল করে বসবে। কিন্তু যারা এখানে অনেক অনেক নম্বর পায় তারাও দেখা যায় ইংরেজি বলতে গেলে মুখ শুকিয়ে মূক হয়ে যায়। কারণ আমরা ব্যাকরণে যতটা গুরুত্ব দিই ততটা গুরুত্ব নেই বলায় ও যোগাযোগে। ইংরেজির মতো গোলমেলে আরেকটা ব্যাপার আছে আরবির ক্ষেত্রে। যে মধ্যপ্রাচ্য সফরের কথা বলছিলাম সেখানকারই অভিজ্ঞতা। কোরআন শরিফ শিক্ষার সুবাদে আমাদের প্রায় সবাই কমবেশি আরবি পড়তে পারি। আরবিতে লেখা যত সাইনবোর্ড-বিলবোর্ড আছে সব দিব্যি পড়তে পারছি। পড়তে পারছি; কিন্তু বুঝতে পারছি না। আর তখন আরেকটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা নষ্ট করার আফসোসও হতে থাকল। প্রায় সবাই যেহেতু আরবি পড়াটা শিখে ফেলি, শিক্ষাব্যবস্থায় আরেকটু সমন্বয় করলে খুব সম্ভব আরবি ভাষাটাও পুরো শিখে ফেলা যায়। কিন্তু এখানেও খণ্ডিত এবং আংশিক শিক্ষা। তাই আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ শিখি, বলতে শিখি না। আরবি পড়তে জানি, অর্থ জানি না। আর এভাবে দ্বিতীয় ভাষা জানার অভাবে বৈশ্বিক যোগাযোগে যে সমস্যা সেই দায়টা গিয়ে পড়ে বাংলার ওপর। মনে করি, বাংলা মিডিয়ামে পড়ে এবং বাংলায় মেতে থাকি বলেই ইংরেজি শেখা হচ্ছে না। পিছিয়ে পড়ছি। কেউ ছোটে ইংলিশ মিডিয়ামে। যাদের সেই ক্ষমতা নেই তারাও বাংলার ওপর রেগে থাকে। ইংরেজি বা দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা সঠিক হলে তখনই বাংলা এই ভুল দায় থেকে মুক্তি পাবে। সমুন্নত থাকবে বাংলার গুরুত্ব ও মর্যাদা। ভাড়া করা ঢোল আর লাগবে না।
কারো কারো কাছে বিষয়টাকে ভারী লাগতে পারে। ভাষার এই ভার কমানোর জন্য তারাপদ রায়ের বিশাল সংগ্রহ থেকে একটা ভারতীয় কৌতুক শোনা যাক। এক ভদ্রলোক মারা যাওয়ার আগে ছেলেকে ধরলেন, ‘আমাকে সংস্কৃত শেখানোর ব্যবস্থা কর। কখন মরে যাই...’
ছেলে বলল, ‘জীবনে লাগল না। মরে গেলে সংস্কৃত লাগবে কেন?’
‘আরে স্বর্গের ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। সেটা না পারলে লজ্জার ব্যাপার হবে।’
ছোট ছেলে একটু দুষ্টুমি করে বলল, ‘বাবা, তুমি কী করে নিশ্চিত হলে যে স্বর্গে যাবে। নরকেও তো যেতে পারো।’
‘নরকে গেলে তো কোনো সমস্যা নেই। আমার হিন্দি তো জানাই আছে।’
হিন্দি তাহলে নরকের ভাষা! কৌতুকটার জাতীয়করণ করলাম না; কারণ এই ফেব্রুয়ারিতে বাংলার বিষয়ে আমাদের কেউ কেউ অতিরিক্ত আবেগী হয়ে যাই।
সেই আবেগপ্রবণদের জন্যও একটা গল্প আছে। আশির দশকে ইংল্যান্ডের এমসিসি দল এসেছে বাংলাদেশে খেলতে। ম্যাচ শুরুর আগে এমসিসির অধিনায়কের কাছে ভাষ্যকার জানতে চাইলেন, ‘হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্য পিস।’
অধিনায়ক একটু অবাক। এখানে পিস বা শান্তির প্রসঙ্গ আসবে কেন? তবু ভদ্রতা করে বললেন, ‘ইয়া। এভরিথিং ভেরি পিসফুল।’
ভাষ্যকার আঙুল দিয়ে মাঠের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, ‘নো নো, আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট পিস’।
এবার অধিনায়ক বুঝলেন। হেসে বললেন, ‘ও তুমি পিচের কথা বলছ। ভালো। ব্যাটিং-বোলিং দুটোর জন্যই..’
বুঝলেন তো, ভাষ্যকার ভদ্রলোক আঞ্চলিকতার কারণে চ-কে ছ বা স-এর মতো উচ্চারণ করেন। তাই পিচ বা উইকেট হয়ে যায় পিস।
এর শিক্ষা কী এটাই যে ঠিকমতো ইংরেজি শিখতে হলেও আগে দরকার সঠিক বাংলা শিক্ষা!
লেখক : সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক
সম্পর্কিত খবর
নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা পরিষ্কার হলো না
- এমরান কবির

আমাদের রাজনীতিতে সন্দেহ জিনিসটা নতুন কিছু না। কিছুদিন আগেও এই সন্দেহটা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল নির্বাচন ঘিরে। সরকার যখন সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করছিল না, তখনই এই সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপি প্রথমে ক্ষীণকণ্ঠে আওয়াজ তুলল সুনির্দিষ্ট তারিখের দাবি নিয়ে।
যে যাই-ই বলুক না কেন, এখন জনগণ কয়েকটি জিনিস চায়।
গত ১৩ জুন লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তারেক রহমানের বৈঠক শেষে ‘যৌথ বিবৃততিতে’ বলা হয়, ‘সব প্রস্তুতি শেষ করা গেলে ২০২৬ সালে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহে নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে বলে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন। সে ক্ষেত্রে ওই সময়ের মধ্যে সংস্কার ও বিচারের বিষয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতির প্রয়োজন হবে।’
এরই মধ্যে জুনের শেষ সপ্তাহে গণমাধ্যমের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, লন্ডন বৈঠকের কোনো প্রতিফলন নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে দৃশ্যমান না হওয়ায় এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচনের দাবি ও সমানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ আরো কিছু বিষয় নতুন করে সামনে আনার চেষ্টা হচ্ছে, যা জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্য বলে মনে করছে বিএনপি।
বিএনপির সন্দেহের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি, কারণ ও ভিত্তি রয়েছে। প্রথমোক্ত ‘ওই সময়ের মধ্যে সংস্কার ও বিচারের বিষয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতি’ দেখা যাচ্ছে না। আর তাত্ত্বিকভাবে বলা যেতে পারে, সরকার একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে অনির্দিষ্ট বিষয় দ্বারা শর্তারোপ করায় প্রথমোক্ত নির্দিষ্ট বিষয়টি অনির্দিষ্ট হয়ে গেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার তেমন কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হলে অবধারিতভাবেই জাতীয় নির্বাচন পেছাবে। আর তা যদি যথাযথভাবে সফল না হয়, তাহলে এর ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টায় কালক্ষেপণ হতে থাকবে। আর এর ভেতরে যদি নির্বাচনপদ্ধতিতে সংখ্যানুপাতিক হার ঢুকে যায়, তাহলে কোনোভাবেই ঘোষিত সময় অনুযায়ী নির্বাচন সম্ভব হবে না।
এরই মধ্যে গত ৩০ জুন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বৈঠক করেছেন। দেশবাসী ধারণা করছিল নির্বাচনবিষয়ক দিকনির্দেশনা থাকতে পারে ওই বৈঠকে। কিন্তু ১ জুলাই সিইসি সংবাদ সম্মেলনে জানালেন ওই বৈঠক ছিল ‘সৌজন্য সাক্ষাৎ’। নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা না হলেও ‘ফুল গিয়ারে’ চলছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। আর সেটি আগামী ‘ফেব্রুয়ারি অথবা এপ্রিল’-এ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে এতে নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা একটুও পরিষ্কার হলো না। জিনিসপত্র বিক্রির জন্য প্রায়ই কম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের অফার দিয়ে থাকে। সেখানে দেখা যায়, ছাড় দেওয়া হয়েছে ৫০, ৬০ বা ৭০ শতাংশ, যা লেখা থাকে বেশ বড় অক্ষরে। তার নিচেই ‘স্টার’ চিহ্ন দেওয়া থাকে কিংবা ছোট অক্ষরে লেখা থাকে ‘আপ টু’। স্টার চিহ্নের ব্যাখ্যা হিসেবে দেওয়া থাকে ‘শর্ত প্রযোজ্য’, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হিডেন (গুপ্ত) অবস্থায় থাকে। এখন সরকারের ঘোষিত ‘সংস্কার ও বিচারের পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন’ যদি ওই আপ টু বা স্টার চিহ্নের মতো থাকে আর তার ভেতরে যদি দুর্বোধ্য শর্ত থাকে, তাহলে তো সন্দেহের অবকাশ থাকেই। সরকারকে ওই স্টার চিহ্ন বা আপ টুকে খোলাসা করতে হবে।
একটি কৌতুক দিয়ে শেষ করি। কপি করা কৌতুক। কৌতুকে কোনো যুক্তি খোঁজাটাই যুক্তিহীন। একবার একটি বিমান ক্রাশ করে সবাই মারা গেল। কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল ওই বিমানের এক যাত্রী। সে একটি বাঁদর। তো বিমান ক্রাশের রহস্য উদঘাটনের জন্য বাঁদরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হলো। প্রথমেই জিজ্ঞেস করা হলো, বিমান ধ্বংসের আগে পাইলট কী করছিল? বাঁদর তো আর কথা বলতে পারে না। তাই দুই হাত এক করে মাথার নিচে দিয়ে মাথা কাত করে দেখাল। তার মানে হলো পাইলট ঘুমাচ্ছিল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কো-পাইলট কী করছিল। বাঁদর একই রকম ভঙ্গি করে দেখাল। ক্রু? বাঁদর একই ভঙ্গি করে দেখাল। যাত্রীরা? বাঁদর এবারও একই ভঙ্গি করে দেখাল। তার মানে সবাই ঘুম। বাকি থাকে বাঁদর। তাকে এবার জিজ্ঞেস করা হলো তুমি কী করছিলে? বাঁদরটি তখন দুই হাত দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরানোর অভিনয় করে দেখাল। তার মানে সবাই যখন ঘুমাচ্ছিল, তখন সেই বাঁদরটিই বিমান চালাচ্ছিল। আর তার পরিণতি বিমান ধ্বংস হয়ে সবার মৃত্যু।
সবাই ঘুমালে কিন্তু বিমান চালাতে পারে ওই রকম বাঁদর।
লেখক : কবি-কথাসাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক
নতুন আতঙ্ক জিকা ভাইরাস : করণীয় কী?
- অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার

সম্প্রতি চট্টগ্রামে দুই ব্যক্তির শরীরে জিকা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, এই সংবাদ দেশের জনস্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতোই জিকা ভাইরাসও এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায় এবং এটি আগামী দিনে আরেকটি বড় স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পরিণত হতে পারে।
চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা যায়, দুজন রোগীর শরীরে বেসরকারি ল্যাব এপিক হেলথ কেয়ারে পরীক্ষার মাধ্যমে জিকা ভাইরাস শনাক্ত হয়। আক্রান্তদের মধ্যে একজন নারী ও একজন পুরুষ, দুজনেরই বয়স ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে।
জিকা একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ভাইরাসটি প্রথম ১৯৪৭ সালে উগান্ডার ‘জিকা বন’-এ শনাক্ত হয়েছিল, সেখান থেকেই এর নামকরণ। এটি ফ্লাভিভাইরাস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপসর্গগুলোর মধ্যে দেখা যায়, হালকা জ্বর, ত্বকে র্যাশ বা ফুসকুড়ি, মাথা ব্যথা, চোখ লাল হওয়া (কনজাংকটিভাইটিস), অস্থিসন্ধি ও মাংসপেশির ব্যথা। সাধারণত এই উপসর্গগুলো দুই থেকে সাত দিন স্থায়ী হয়।
 বর্তমানে বাংলাদেশ ডেঙ্গু এবং কখনো কখনো চিকুনগুনিয়ার ভয়াবহতার মধ্যেই আছে। এর মধ্যে জিকার মতো নতুন ভাইরাসের আবির্ভাব হলে তা একদিকে স্বাস্থ্য খাতে চাপ, অন্যদিকে জনমনে আতঙ্কও বাড়াবে। তা ছাড়া ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা একই বাহকের মাধ্যমে ছড়ালেও এই তিনটির উপসর্গ আংশিকভাবে মিল থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।
বর্তমানে বাংলাদেশ ডেঙ্গু এবং কখনো কখনো চিকুনগুনিয়ার ভয়াবহতার মধ্যেই আছে। এর মধ্যে জিকার মতো নতুন ভাইরাসের আবির্ভাব হলে তা একদিকে স্বাস্থ্য খাতে চাপ, অন্যদিকে জনমনে আতঙ্কও বাড়াবে। তা ছাড়া ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা একই বাহকের মাধ্যমে ছড়ালেও এই তিনটির উপসর্গ আংশিকভাবে মিল থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশে এখনো জিকা ভাইরাস পরীক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধা নেই। যে কয়েকটি ল্যাবে এই পরীক্ষা করা যায়, তা সীমিত এবং ব্যয়বহুলও বটে। ফলে গ্রামীণ বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর বাইরে থেকে যায়। জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে এই পরীক্ষার সুযোগ সুলভ ও সহজলভ্য করা প্রয়োজন।
জিকা ভাইরাস সাধারণত এডিস ইজিপ্টাই ও এডিস অ্যালবোপিক্টাস নামক মশার মাধ্যমে ছড়ায়, যা একই সঙ্গে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ভাইরাসও বহন করে। এ ছাড়া যৌন সংস্পর্শ, রক্ত সংক্রমণ এবং মায়ের দেহ থেকে গর্ভস্থ শিশুর শরীরে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। এ কারণে এটি শুধু মশা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব নয়, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত আচরণেও পরিবর্তন আনা জরুরি।
তবে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা এই তিনটি রোগই এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। তাই মশার বিস্তার রোধ করাই হবে প্রথম এবং কার্যকর প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ। বিভিন্ন পাত্রে জমা পানি; যেমন—বালতি, ড্রাম, পার্কিং ও বেইসমেন্টে জমা পানি, নির্মাণাধীন ভবনে জমা পানি, ফুলের টব, ডাবের খোসা, ফ্রিজের নিচের ট্রে ইত্যাদি যেখানে পানি জমে, সেসব নিয়মিত পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় এই সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।
জনগণের মধ্যে জিকা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটি সেন্টারে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালানো যেতে পারে। ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়ার উপসর্গ থাকলেও যেন সন্দেহভাজন রোগীদের জিকা পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এই সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।
গর্ভবতী নারীদের মশার কামড় থেকে রক্ষা পেতে মশারি ব্যবহার, পূর্ণাঙ্গ পোশাক পরিধান ও ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে আরো সচেতন হতে হবে। এ ছাড়া জিকা ভাইরাস প্রবণ এলাকায় ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। সন্দেহ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জিকা শনাক্তকরণ পরীক্ষার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। শুধু রাজধানী নয়, বিভাগীয় শহর বা বড় জেলা হাসপাতালেও এই পরীক্ষা সহজলভ্য করতে হবে। করোনাভাইরাস শনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে পিসিআর প্রযুক্তি আনা হয়েছিল, যেগুলো জিকা শনাক্তকরণে ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য গবেষকদের জন্য এখনই সময় জিকা নিয়ে বিশেষ গবেষণা ও নজরদারি চালানোর। ভাইরাসটি স্থানীয়ভাবে ছড়াচ্ছে কি না, তা নির্ধারণ করা দরকার। সংক্রমণের উৎস ও গতিপথ বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যেসব দেশে জিকা ভাইরাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে, সেসব দেশের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।
জিকা ভাইরাস একটি বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হওয়ায় এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো; যেমন—WHO, CDC প্রভৃতির সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। এদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি জাতীয় নির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।
জিকা ভাইরাস এখনই বড় কোনো মহামারির রূপ না নিলেও এর উপস্থিতি আগাম সতর্কতা হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে ভবিষ্যতের বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে শুধু চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের নয়, সাধারণ জনগণকেও সচেতন এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সমন্বিত উদ্যোগ, গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রম এবং নাগরিক সচেতনতা—এই তিনটির সমন্বয়ে আমরা শুধু জিকা নয়, ভবিষ্যতের যেকোনো সংক্রামক রোগের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারব।
লেখক : কিটতত্ত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
professorkabirul@gmail.com
মানুষের অগ্রগতি মন্দকে পরাস্ত করেই ঘটে
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
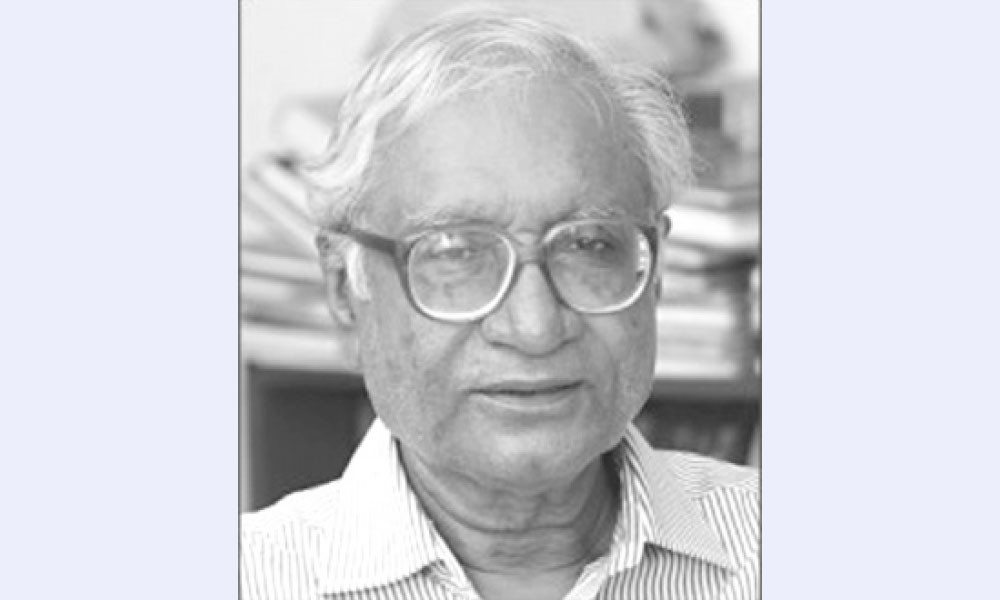
দেশের বর্তমান পরিস্থিতি যে মোটেই ভালো নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটিও অবশ্য সত্য যে অবস্থা কখনোই ভালো ছিল না। তবে এখনকার পরিস্থিতি বিশেষভাবে মন্দ মনে হচ্ছে কয়েকটি অতিরিক্ত কারণে। প্রথমত, মানুষ আশা করেছে ২০২৪-এর অভ্যুত্থান-পরবর্তী সর্বক্ষেত্রে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে, দেশবাসীর জন্য বয়ে আনবে সুদিন।
 মানুষ সমাজে বাস করে, সেখানে আজ কোনো নিরাপত্তা নেই। না আছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, না দৈহিক। রাষ্ট্র তার কর্তব্য পালন করতে পারছে না। উপরন্তু সে নিজেই একটি সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তার পুলিশ, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ কেউ নিরাপত্তা দেয় না, বরং মানুষের জন্য ভীতির কারণ হয়। অন্যদিকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সন্ত্রাস ঘটছে রাষ্ট্রের ঔদাসীন্যে, আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। সন্ত্রাসীদের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। পরিস্থিতি এগোচ্ছে অরাজকতার দিকে। সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক নৈরাশ্য। এই অরাজক পরিস্থিতির অভ্যন্তরে সমাজে যা ঘটছে তা হলো শ্রেণিকর্তৃত্বের আধিপত্য বৃদ্ধি। এই বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রেণিকে আগে আমরা মধ্যবিত্ত বলতাম, এখন তাকে বিত্তবান বলাই সংগত। কেননা মধ্যবিত্ত এখন আর অবিচ্ছিন্ন নেই, তার একাংশ নেমে গেছে নিচে, অন্য অংশ উঠেছে উঁচুতে। বিত্তবান এই শ্রেণিটিই এখন দেশের সর্বময় কর্তা। এরাই আমলা, এরাই ব্যবসায়ী; রাজনীতিও এরাই করে, শিল্প-সংস্কৃতিও রয়েছে এদেরই নিয়ন্ত্রণে, যদিও এদের সংখ্যা জনগণের তুলনায় শতকরা পাঁচজনের বেশি হবে না। এই শ্রেণির মধ্যে দেশপ্রেম নেই, এর সদস্যরা গণতন্ত্রেও বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, সরকারের রদবদল—সবকিছুর ভেতরে অব্যর্থ রয়েছে এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রেণির শক্তি সঞ্চয়।
মানুষ সমাজে বাস করে, সেখানে আজ কোনো নিরাপত্তা নেই। না আছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, না দৈহিক। রাষ্ট্র তার কর্তব্য পালন করতে পারছে না। উপরন্তু সে নিজেই একটি সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তার পুলিশ, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ কেউ নিরাপত্তা দেয় না, বরং মানুষের জন্য ভীতির কারণ হয়। অন্যদিকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সন্ত্রাস ঘটছে রাষ্ট্রের ঔদাসীন্যে, আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। সন্ত্রাসীদের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। পরিস্থিতি এগোচ্ছে অরাজকতার দিকে। সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক নৈরাশ্য। এই অরাজক পরিস্থিতির অভ্যন্তরে সমাজে যা ঘটছে তা হলো শ্রেণিকর্তৃত্বের আধিপত্য বৃদ্ধি। এই বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রেণিকে আগে আমরা মধ্যবিত্ত বলতাম, এখন তাকে বিত্তবান বলাই সংগত। কেননা মধ্যবিত্ত এখন আর অবিচ্ছিন্ন নেই, তার একাংশ নেমে গেছে নিচে, অন্য অংশ উঠেছে উঁচুতে। বিত্তবান এই শ্রেণিটিই এখন দেশের সর্বময় কর্তা। এরাই আমলা, এরাই ব্যবসায়ী; রাজনীতিও এরাই করে, শিল্প-সংস্কৃতিও রয়েছে এদেরই নিয়ন্ত্রণে, যদিও এদের সংখ্যা জনগণের তুলনায় শতকরা পাঁচজনের বেশি হবে না। এই শ্রেণির মধ্যে দেশপ্রেম নেই, এর সদস্যরা গণতন্ত্রেও বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, সরকারের রদবদল—সবকিছুর ভেতরে অব্যর্থ রয়েছে এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রেণির শক্তি সঞ্চয়।
রাজনৈতিক নেতৃত্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী। বলাই বাহুল্য যে এই নেতৃত্বও বিত্তবানদের দ্বারাই গঠিত। তারাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও পোশাকে রাজনীতি করে। তাদের ভেতর কলহ আছে, সংঘর্ষ প্রায়ই বাধে, যেমনটি ঘটে থাকে পারিবারিক সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইদের মধ্যে। রাজনীতি এখন লুণ্ঠনের লোভে মত্ত বিত্তবানদের অন্তঃকলহ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত দুর্বল। কারণ একদিক দিয়ে ক্ষমতায় থাকার কোনো প্রকার নৈতিক অধিকার এর নেই, অন্যদিক দিয়ে এই নেতৃত্ব একেবারেই অদক্ষ। নেতৃত্ব মোটেই সমাজসচেতন নয়, তবে পুরোপুরি আত্মসচেতন, মুনাফালোভী, ভোগলিপ্সু ও আত্মমর্যাদাহীন বটে। এরা যে সরকারে রয়েছে, সেটি অন্য কোনো যোগ্যতার কারণে নয়, নিছক বিত্ত ও ক্ষমতার বলে। দেশে এখন দুর্বলের প্রতি অসহনীয় দুঃশাসন চলছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, যাদের ভেতর রয়েছে দেশপ্রেম ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, তারা কী করতে পারি? স্বভাবতই প্রথম কাজ শত্রু কে, সেটি
নিরূপণ করা। শত্রু হচ্ছে সেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, যা বিত্তবানদের নির্মম ও অরাজক শাসনকে স্থায়ী করে রেখেছে। সংগত কারণেই শত্রু তারাও, এই ব্যবস্থার যারা রক্ষক ও বিশেষ সুবিধাভোগী।
দ্বিতীয় করণীয় এই বৈরী ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন করা। আন্দোলন যে নেই, তা নয়। আছে। প্রয়োজন তাকে বেগবান, গভীর ও ব্যাপক করা। সরকার বদলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না, হয়ওনি। সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার হবে, যে পরিবর্তনটা আসেনি। আমাদের সমাজ পুরনো ও জীর্ণ, কিন্তু সে আগের মতোই নিপীড়নকারী ও বৈষম্যমূলক। রাষ্ট্র এই সমাজকে পাহারা দেয় এবং সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করে।
রাষ্ট্র বদলেছে আবার বদলায়ওনি। কেননা রাষ্ট্র সেই আগের মতোই নির্যাতন করে। মানুষের অভ্যুত্থান ঘটেছে, যুদ্ধ হয়েছে মুক্তির লক্ষ্যে, কিন্তু সমাজ রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক আমলে যে রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেই রকমই। সাম্রাজ্যবাদ আগেও ছিল, এখনো আছে এবং আমাদের রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের হুকুমবরদার ও তল্পিবাহক বটে। তার নির্লজ্জ নমুনা তো আমরা দেখেই যাচ্ছি।
সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনকে অবশ্যই রাজনৈতিক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন বেশ জরুরি। এক. আন্দোলন কি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে এগোতে পারবে? মোটেই না। কেননা বুর্জোয়া দলই হচ্ছে বিত্তবানদের সংগঠন। না, বিত্তবানরা সমাজের জন্য কেবল যে বোঝা তা নয়, তারা দেশবাসীর শত্রুও বটে। আন্দোলন তো আসলে তাদের বিরুদ্ধেই, সেখানে তাই মৈত্রীর প্রশ্ন অবান্তর। আন্দোলন পাশাপাশি চলতে পারে, সেটি ভিন্ন ব্যাপার। দুই. রাষ্ট্রীয় সাধারণ নির্বাচনে সমাজ পরিবর্তনবাদী মানুষের ভূমিকা কী হবে। তারা ভোট দেবে, দুটি খারাপের মধ্যে যেটিকে কম খারাপ মনে করে তাকে সমর্থন করবে, কিন্তু নিজেরা নির্বাচনে প্রার্থী হবে কি? না, আপাতত নয়। অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, নির্বাচন তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে, যখন পেছনে তার আন্দোলন ছিল; যেমন—১৯৪৬, ১৯৫৪ ও ১৯৭০-এ। কিন্তু এমনকি সেসব তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনে জয়লাভ করেও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা গেছে তা নয়। এর কারণ নির্বাচনী বিজয়কেই চূড়ান্ত মনে করা হয়েছে এবং তার ডামাডোলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এখন তো দেশে বেগবান কোনো আন্দোলন নেই, সমাজ পরিবর্তনকামীদের পক্ষে এখন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া করুণ ও হাস্যকর ফল নিয়ে আসবে, যেমনটি বিগত একাধিক নির্বাচনে ঘটেছে। তিন. তথাকথিত সুধী বা নাগরিক সমাজের ভূমিকা কতটা কার্যকর হবে? স্পষ্ট করেই বলা যায়, মোটেই কার্যকর হবে না। সুধীসমাজ হচ্ছে ভদ্রলোকদের সমাবেশ এবং পুঁজিবাদী বিশ্ব কর্তৃক উচ্চমূল্যায়িত তথাকথিত আন্তর্জাতিক সমাজের মতোই তা ভুয়া। তাঁরা বিত্তবান শ্রেণিরই অংশ এবং বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে সংস্কারের মধ্য দিয়ে টিকিয়ে রাখাটাই তাঁদের অভিপ্রায়। সংস্কার মূল্যহীন নয়, কিন্তু সংস্কার আর সমাজের মৌলিক পরিবর্তন তো এক জিনিস হতে পারে না। সুধীসমাজ মৌলিক পরিবর্তন চায় না, চাইতে পারেও না। কেননা ওই ঘটনা ঘটলে তাদের প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ বিপন্ন হবে। তদুপরি দেশের ভদ্রলোক সমাজের কর্তাব্যক্তিরা যেভাবে শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তাতেই বিলক্ষণ বোঝা যায় যে তাঁদের তৎপরতা কোন লক্ষ্যে নিয়োজিত।
আন্দোলনটি হবে সমগ্র জনগণের। তার অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজ করবেন সচেতন মানুষ, যাঁরা দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক, যাঁরা বিশ্বাস করেন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করতে হবে, যে গণতান্ত্রিকতার প্রধান শর্ত হচ্ছে নাগরিকদের ভেতর অধিকার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা। তাঁদের একাংশ নিজেরা বিত্তবান শ্রেণির মানুষ হতে পারে, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তাদের অবশ্যই যেতে হবে শ্রেণিস্বার্থের সংকীর্ণ ও নোংরা সীমানা পার হয়ে সমষ্টিগত স্বার্থের এলাকায়। স্থির থাকবে লক্ষ্য, প্রচার করতে হবে বক্তব্য, সচেতন করতে হবে মানুষকে এবং সংগঠিত হতে হবে অঙ্গীকার নিয়ে। কাজ চলবে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে, প্রতিটি পেশায়, প্রতিষ্ঠানে, এমনকি পরিবারের ভেতরও। কাজটি হবে একই সঙ্গে অন্যায় প্রতিরোধের ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার। আর এসব যে আমরা করব, তা কোনো আধ্যাত্মিক সুখ বা নান্দনিক তৃপ্তি লাভের আশায় নয়, করব নিছক বাঁচার প্রয়োজনে।
অবস্থা এমন যে মনে হয় আমাদের কোনো আশা নেই। কেননা যা চোখে পড়ে তা হলো সমাজে আজ সবাই সবার শত্রু, পারস্পরিক মৈত্রীর সব সম্ভাবনাই বুঝি বা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। প্রকৃত সত্য কিন্তু ভিন্ন রকমের। সমাজের সমষ্টিগত মানুষই দেশপ্রেমিক এবং সেখানে গণতান্ত্রিক চেতনার যে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তা-ও নয়। অতীতে তারা গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, ভবিষ্যতে যে ঘটাতে পারবে না, তা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু এই মানুষরা বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন, তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না, তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদের ভেতরকার ঐক্যের অভাবই শত্রুপক্ষের প্রধান ভরসা।
সাহিত্যে যেমন, জীবনেও তেমনি, মন্দই চোখে পড়ে সহজে, সে-ই দৌরাত্ম্য করে, কিন্তু সব মন্দই নৈতিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল; নির্লজ্জ ও নৃশংস বলে তাকে পরাস্ত করা কঠিন অবশ্যই, কিন্তু মোটেই অসম্ভব নয়। মানুষের সংস্কৃতির যে অগ্রগতি, তা ওই মন্দকে পরাভূত করেই ঘটেছে; আমাদের দেশেও তেমনটিই ঘটবে বলে আশা করি।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চালের মূল্যবৃদ্ধি : ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও ব্যবসায়ীদের কারসাজি দায়ী
- ড. জাহাঙ্গীর আলম

বেশ কয়েক মাস ধরে চালের বাজার অস্থির। বোরো ধান কাটার সময় দাম কিছুটা কমেছিল। মৌসুম পার না হতেই আবার বাড়ছে চালের দাম। অথচ এ সময় চালের দাম স্থিতিশীল থাকার কথা, কিন্তু চালের বাজার চলছে উল্টো পথে।
অনেকেই মনে করেন, এটি অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি।
এবার দেশে চালের কোনো সংকট নেই। সরকারি পর্যায়ে চালের মজুদ আছে ১৩ লাখ ৮২ হাজার ৭৭৫ টন। গমসহ মোট খাদ্যশস্য আছে ১৭ লাখ ৬৮ হাজার ২৭৬ টন। এ ছাড়া ধানের মজুদ আছে দুই লাখ ২৪ হাজার ৭৪৫ টন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ১৩ লাখ পাঁচ হাজার টন চাল। গম আমদানি হয়েছে ৬২ লাখ ৩৫ হাজার টন। মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৫ লাখ ৪০ হাজার টন। চালের মোট সম্ভাব্য উৎপাদন ধরা হচ্ছে প্রায় চার কোটি ১৯ লাখ টন। গত পাঁচ বছরের মধ্যে চালের উৎপাদন, আমদানি ও মজুদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ছিল সর্বোচ্চ। এরপর এভাবে চালের মূল্যবৃদ্ধির কোনো কারণই নেই।
এরই মধ্যে বিশ্ববাজারে চালের দামে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। গত এক মাসে চালের দাম কমেছে ১০.১৮ শতাংশ। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে উৎপাদনকারী দেশগুলোতে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ায় এবং রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় চালের দর নিম্নমুখী হয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের পর বিশ্ববাজারে এখন চালের দাম সর্বনিম্ন। অথচ বাংলাদেশের বাজারে বাড়ছে চালের দাম।
ব্যবসায়ীরা বলছেন, তাঁরা এখন বেশি দামে ধান কিনেছেন, তাই চালের দাম পড়ছে বেশি। প্রকৃত প্রস্তাবে বড় মিলাররা ধান কিনে নিয়েছেন উৎপাদনের পরপরই। তখন ভেজা ধান প্রতি মণ বিক্রি হয়েছে ৯০০ থেকে এক হাজার ১০০ টাকা দামে। সরকার নির্ধারিত এক হাজার ৪৪০ টাকা দর কখনোই কৃষকদের দেননি ব্যবসায়ীরা। পরে যখন ময়ালে ধানের দাম বেড়েছে, তখন কৃষকদের হাতে বিক্রির মতো ধান নেই। ধান চলে গেছে ব্যবসায়ীদের গুদামে।
এবার দেশে বোরোর উৎপাদন বেশ ভালো হয়েছে। দেশের মোট চাল উৎপাদনে বোরোর হিস্যা প্রায় ৫৪ শতাংশ। অতএব, এই মৌসুমের গুরুত্ব বেশি। চলতি মৌসুমে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা দুই কোটি ২৬ লাখ টন অর্জন করা সম্ভব না হলেও গত বছরের দুই কোটি সাড়ে ১০ লাখ টনের তুলনায় অনেক বেশি হবে। কমপক্ষে দুই কোটি ১৪ লাখ টন হবেই। এটি আমাদের বার্ষিক খোরাকির অর্ধেকের চেয়েও বেশি। আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ আমন ধানের মৌসুম পর্যন্ত তাতে অনায়াসেই চলবে। অতএব, অদূর ভবিষ্যতে দেশে চালের কোনো সরবরাহ সংকট হওয়ার আশঙ্কা নেই। সামনের আউশ মৌসুমের উৎপাদন ভালো হলে এবার চাল আমদানির প্রয়োজন হবে না। বর্তমানে চালের দাম বাড়ছে অজুহাতে অনেকে চাল আমদানির পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে লাভবান হবেন চাল আমদানিকারক ব্যবসায়ীরা এবং বিদেশের চাল উৎপাদনকারী কৃষকরা। বাংলাদেশের কৃষকরা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ভোক্তারাও লাভবান হবেন না। অতএব, আগামী আউশ ও আমন ধানের নিরাপদ উৎপাদনের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত। বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধির মাধ্যমে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
ওদিকে চালের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে আলুর দামও বেড়েছে। প্রকারভেদে কেজিতে বেড়েছে পাঁচ থেকে ১০ টাকা। সবজিতেও স্বস্তি নেই। বিভিন্ন প্রকার সবজির দাম কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে। এতে বেশ অস্বস্তিতে আছেন ভোক্তারা। ঢাকা শহরে এখন পটোল বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি। করলা বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৮০ টাকা। বরবটির কেজি ১০০ থেকে ১২০ টাকা। বেগুন বিক্রি হচ্ছে মানভেদে ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজি। কাঁচা মরিচ ১৬০ টাকা কেজি। টমেটোর কেজি ১২০ থেকে ১৫০ টাকা। ডিমের দাম বেড়েছে ডজনে ১০ থেকে ২০ টাকা। মাছের দামও বেড়েছে। এভাবে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে বড় কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য। তাদের লাগাম টেনে ধরা উচিত। নিয়মিত বাজার মনিটরিং এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। বাজার পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পণ্যের যৌক্তিক মূল্য সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা উচিত। বাজার কারসাজির ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়াই উত্তম পদক্ষেপ। অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হওয়া উচিত উৎপাদন খরচ। এর সঙ্গে বিপণন খরচ ও মুনাফা যোগ করে নির্ধারিত হবে ভোক্তা মূল্য। আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হবে আমদানি মূল্য। অভ্যন্তরীণ খরচ ও ব্যবসায়ীর লাভ যোগ করে হবে ভোক্তা মূল্য। বিপণন শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরে তার ঘোষণা থাকা উচিত, যাতে কেউ চড়া দাম হাঁকিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে গরিব ভোক্তাদের।
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি। গত জুলাই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪ শতাংশ। নভেম্বরে ছিল ১৩.৮০ শতাংশ। গত মার্চে তা কমে দাঁড়ায় ৮.৯৩ শতাংশে। গেল জুনে তা আরো কমে ৭.৩৯ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। তবে চাল, আলু ও সবজির সাম্প্রতিক উচ্চমূল্যের কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরো শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেছে। এ ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাপনায় আরো দক্ষতা অর্জন করতে হবে। মনিটরিং জোরদার করতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ও সিন্ডিকেটের কারসাজি থামাতে হবে। বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ আরো দৃশ্যমান ও কার্যকর করতে হবে।
লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃষি অর্থনীতিবিদ। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ

