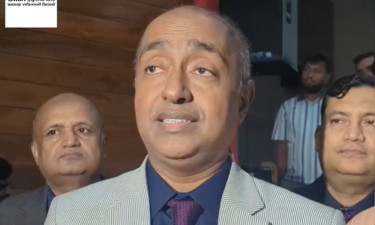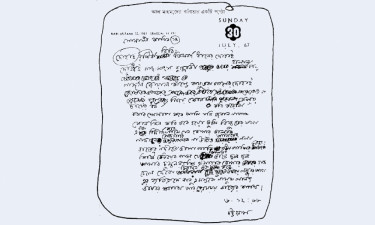প্রক্সিমিটি সেন্সর
মুখের সঙ্গে লেগে যাতে অযাচিত স্পর্শ না লাগে, সে জন্য ফোনে কথা বলার সময় নিজ থেকেই স্মার্টফোনের ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে যায়। একইভাবে ফোন পকেটে থাকলেও ডিসপ্লে থাকে বন্ধ বা কল শেষে চালু হয় ডিসপ্লে। আর এ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় ফোনের প্রক্সিমিটি সেন্সর। ডিসপ্লের সামনে কিছু আছে কি না বা কত দূরে আছে, নির্ণয় করে এ সেন্সর।
দুটি অংশে বিভক্ত এ সেন্সর—একটি ইনফ্রারেড সেন্ডার ও রিসিভার। ইনফ্রারেড সেন্ডারটি ইনফ্রারেড বা অবলাল রশ্মি ছুড়তে থাকে, আর রিসিভার সে রশ্মি কিছুতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে কি না লক্ষ করে। ডিসপ্লের কাছে কোনো বস্তু বা কানের সঙ্গে ফোন ধরলে সেন্ডার অবলাল রশ্মি পেতে শুরু করে আর ফোন জানতে পারে, ডিসপ্লের সামনে কিছু একটা আছে। ফলে ডিসপ্লে বন্ধ হয়ে যায়। এ সেন্সরটি অনেক সময় সমস্যা করে থাকে, বিশেষ করে সেন্সরের ওপর যদি স্ক্রিন প্রোটেক্টর বা গ্লাস লাগানো হয়, তাহলে সেটি উল্টাপাল্টা রিডিং দিতে থাকে। কখনো কখনো দেখা যায়, ফোনের ডিসপ্লে বন্ধ হচ্ছে না, অথবা কখনো ফোন শনাক্ত করে যে এটি এখনো পকেটেই আছে, তাই ডিসপ্লে চালু হতে চায় না। সাধারণত এই সেন্সরটি ইয়ারপিস বা সেলফি ক্যামেরার পাশে অবস্থান করে।
অ্যাক্সেলেরোমিটার ও জাইরোস্কোপ
ব্যবহারকারী কিভাবে ফোনটি ধরেছে—পোর্ট্রেট ভঙ্গি না ল্যান্ডস্কেপে, মূলত সেটি শনাক্ত করার জন্যই এই সেন্সর দুটি ব্যবহার করা হয়।
শুরুতে শুধু অ্যাক্সেলেরোমিটার ব্যবহার হলেও পরে ফোনে জাইরোস্কোপও ব্যবহার শুরু হয়। অ্যাক্সেলেরোমিটার ফোনটির নড়াচড়া এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি কোন দিকে কাজ করে, তা পরিমাপ করে। সেন্সরটির মধ্যে কিছু ক্রিস্টাল দেওয়া থাকে, যা ফোনের গতি এবং মাধ্যাকর্ষণের দিক পরিবর্তনের ফলে অল্পবিস্তর ভোল্টেজ উৎপাদন করে।
এটি মেপে বেশ কিছু তথ্য বের করা যায়। শুধু অ্যাক্সেলেরোমিটারের তথ্য থেকেই ফোনের গ্র্যাভিটি সেন্সর এবং পেডোমিটার কাজ করে।
অন্যদিকে জাইরোস্কোপ অনেকটা অ্যাক্সেলেরোমিটারের মতো কাজ করে; কিন্তু এটি গতি না মেপে ফোনের অবস্থান নির্ভুলভাবে শনাক্ত করে। অর্থাৎ ফোনটি কিভাবে হাতে ধরা, কোন ভঙ্গিতে কাত করা কিংবা কোন দিকে তাক করা, সে তথ্য জাইরোস্কোপ থেকে পাওয়া যায়। ফোনের ডিসপ্লে রোটেশন, গেইমে মোশন কন্ট্রোল, ভিআর কনটেন্টের জন্যও এ দুটি সেন্সর ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া ফোনটি ব্যবহারকারীর পকেটে বা হাতে আছে কি না এবং কতটুকু হাঁটা হয়েছে—সেসবও এ দুটি সেন্সর ব্যবহার করেই হিসাব করা হয়।
হল সেন্সর বা ম্যাগনিটোমিটার
বাজারের বেশির ভাগ ফোনই চৌম্বকক্ষেত্র মাপতে পারে, সেটি অনেক ব্যবহারকারীর কাছেই অজানা। সে কাজের জন্য ব্যবহার হয় ম্যাগনিটোমিটার, যা অনেক সময় ‘হল সেন্সর’ নামেও পরিচিত। চৌম্বকক্ষেত্র মাপার জন্য সেন্সরটির মধ্যে খুব পাতলা একটি লোহার পাত দেওয়া থাকে, যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন মেপেই চৌম্বকক্ষেত্র মাপা যায়। এই সেন্সরের প্রধান কাজ, ম্যাপ বা ন্যাভিগেশন অ্যাপগুলোতে উত্তর-দক্ষিণ দিকের নির্দেশনার তথ্য দেওয়া। এ ছাড়া চাইলে সরাসরি সেন্সরের তথ্য অ্যাপের মাধ্যমে দেখে চৌম্বকক্ষেত্রের মাপ নেওয়া যেতে পারে। আরো একটি কাজে সেন্সরটি প্রয়োজন, ফোনের ফ্লিপ কাভার খোলা বা বন্ধ হয়েছে কি না সেটি দেখার জন্য। ফ্লিপ কাভারের মধ্যে ছোট ম্যাগনেট দেওয়া হয়, যার অবস্থান ম্যাগনিটোমিটারের মাধ্যমে নির্ণয় করে ফোন লক-আনলক হয়ে থাকে।
ফেইস স্ক্যানার
স্মার্টফোন দুনিয়ায় নতুন আগমন ফেইস স্ক্যানারের। ইনফ্রারেড আলো ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের চেহারা শনাক্ত করে থাকে এ সেন্সর। ইনফ্রারেড আলো বেশ কয়েকটি স্পট আকারে ব্যবহারকারীদের মুখে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ফেলা হয়। স্পটগুলো মুখে কিভাবে পড়ছে, তা শনাক্ত করে ইনফ্রারেড ক্যামেরা। সে তথ্য দিয়ে ব্যবহারকারীর চেহারার থ্রিডি ম্যাপ তৈরি করা হয়, যার থেকে পাওয়া ‘এনক্রিপশন হ্যাশ’ তৈরি করে ফোনের নিরাপত্তা চাবি হিসেবে সেটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে অনেক ফোনে এ সেন্সরের বদলে শুধু সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করেই ফেইস স্ক্যান করা হয়, যা মোটেও নিরাপদ নয়।
লাইট সেন্সর ও কালার টেম্পারেচার সেন্সর
মোবাইলের আশপাশের আলো কী পরিমাণ আছে কিংবা রং বা তাপমাত্রা কত; সেটি নির্ণয় করার জন্য এ সেন্সরগুলো ব্যবহার করা হয়। ফোনের ডিসপ্লে কতটুকু উজ্জ্বল হবে, তা এ সেন্সরের ওপর নির্ভর করে। যত বেশি আলো সেন্সরে প্রবেশ করবে, তত বেশি ভোল্টেজ সেন্সরটি থেকে পাওয়া যাবে। চারপাশে যত বেশি আলো থাকবে, ডিসপ্লের উজ্জ্বলতা তত বৃদ্ধি পাবে। অন্ধকারে এর উল্টো দেখা যাবে। কালার টেম্পারেচার সেন্সর সব ফোনে এখনো দেখা যায় না, তবে ডিসপ্লের হোয়াইট ব্যালান্স বদলানোর জন্য এ সেন্সরের তথ্য ব্যবহার করা হয়।
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর
ব্যবহারকারীর আঙুলের ছাপ শনাক্ত করার জন্য এ সেন্সর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তিন ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ফোনে দেখা যায়—ক্যাপাসিটিভ, অপটিক্যাল এবং আল্ট্রাসনিক। ক্যাপাসিটিভ সেন্সরগুলোর পিঠে অল্প পরিমাণ ভোল্টেজ দেওয়া থাকে, যা ব্যবহারকারীর আঙুলের ছাপ অনুযায়ী পাল্টে যায়। তবে অল্পবিস্তর পানি বা অন্য পরিবাহী বস্তুও ক্যাপাসিটিভ সেন্সরে ভুল রিডিং দিতে পারে, ফলে এ সেন্সর এখন আর ব্যবহার করা হয় না। অপটিক্যাল সেন্সরগুলো সরাসরি ব্যবহারকারীর আঙুলের ছবি তুলে তার ছাপ শনাক্ত করে। তবে এ সেন্সরের ভুল রিডিং দেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকায় এটির ব্যবহারও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আল্ট্রাসনিক সাউন্ডের প্রতিফলন ব্যবহার করে আঙুলের ছাপ শনাক্ত করে আল্ট্রাসনিক সেন্সর, যা সবচেয়ে নির্ভুলভাবে কাজ করে।
ব্যারোমিটার
বায়ুচাপ মাপার জন্য ব্যবহার করা হয় ব্যারোমিটার। ক্ষুদ্র এ সেন্সরের মধ্যে বিশেষ অ্যালয় ব্যবহার করা হয়, যার ভেতর দিয়ে প্রবহমান বিদ্যুতের পরিমাণ বায়ুচাপের ওপর নির্ভর করে। বায়ুচাপের মাত্রা সাধারণত ফোনের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, তবে ব্যবহারকারী সমুদ্র সমতল থেকে কতটুকু উঁচুতে অবস্থান করছেন, সেটি মাপার জন্য বায়ুচাপের রিডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অল্টিমিটার হিসেবেই ব্যারোমিটার সেন্সর মূলত কাজ করে থাকে। ম্যাপ বা নেভিগেশন অ্যাপগুলো উচ্চতা মাপার জন্য এ সেন্সর ব্যবহার করে থাকে।
থার্মোমিটার
সেন্সরের মধ্যে থাকা অ্যালয়ের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত ভোল্টেজের পরিবর্তনের ভিত্তিতে তাপমাত্রার পরিমাপ করে থার্মোমিটার সেন্সর। একটি ফোনে একাধিক থার্মোমিটার সেন্সর দেওয়া হয় ফোনের নানা রকম সংবেদনশীল যন্ত্রাংশের তাপমাত্রা খেয়াল রাখার জন্য। প্রসেসর বা ব্যাটারি অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে ব্যবহারকারীকে সাবধান করার জন্য থার্মোমিটার সেন্সরগুলো কাজ করে। কিছু ফোনে আশপাশের তাপমাত্রা মাপার জন্যও থার্মোমিটার সেন্সর দেওয়া থাকে, তবে তার পরিমাণ খুবই কম।
হার্ট রেট ও অক্সিজেন সেন্সর
রক্তের রং এবং রক্তের প্রবাহ মেপে ব্যবহারকারীর হৃদস্পন্দন এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মাপার জন্য ব্যবহার হয় এ সেন্সর। কিছু ফোনে এ সেন্সরগুলো ব্যবহার হলেও মূলত স্মার্টব্যান্ড আর স্মার্টওয়াচেই এ সেন্সর বেশি দেখা যায়। ইনফ্রারেড রশ্মি চামড়া ভেদ করে রক্তনালির মধ্যকার রক্ত দেখাতে পারে, আর সেটি শনাক্ত করাই এ সেন্সরের কাজ। তবে যেসব ব্যবহারকারীর চামড়া ভারী বা গায়ের রং শ্যামলা, তাদের ক্ষেত্রে এ সেন্সরগুলো সঠিকভাবে কাজ করে না।