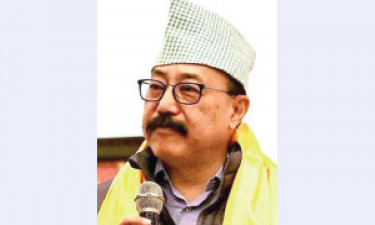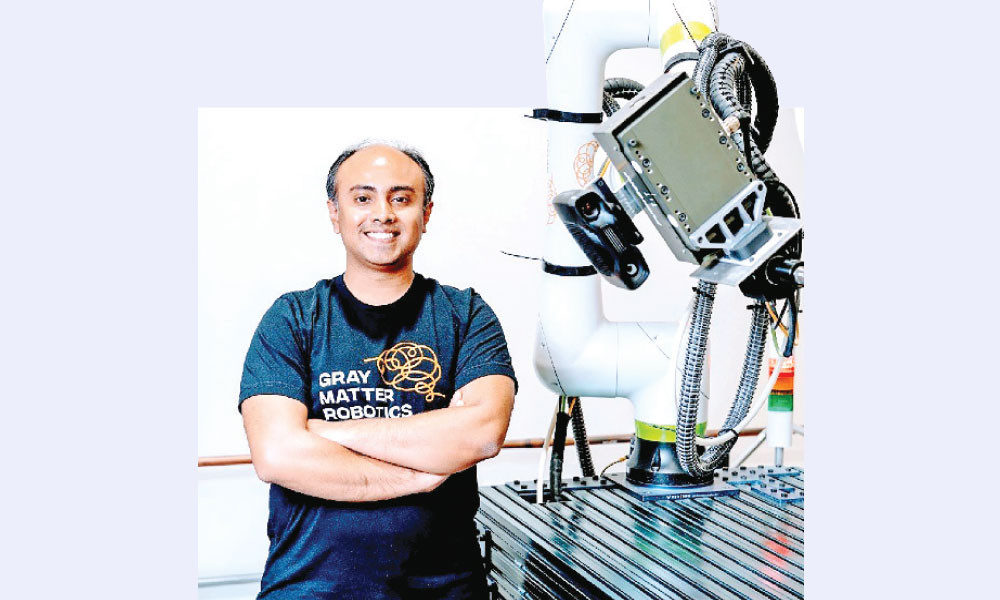কিন্তু তার চাচাতো বোন বা মামাতো বোনের মধ্যে বিয়ে হলে সন্তানের দুটি উইংয়ে এই অসুখটা চলে আসতে পারে। ফলে সেটা প্রকট হয় এবং তাদের সন্তানের অসুখ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।
প্রতিরোধের কথায় এলে এক নম্বর প্রতিরোধ হলো নিকটাত্মীয়কে বিয়ে করা যাবে না। দুই নম্বর প্রতিরোধ হলো, ধরুন কোনো পরিবারে একটি বাচ্চার এই অসুখ ধরা পড়েছে। পরে সেই মা আবার গর্ভবতী হলে তাঁর তিন থেকে চার মাস গর্ভকালীন গর্ভ থেকে ‘অ্যামনিওটিক ফ্লুইড’ বের করে আনতে হবে। সেখান থেকে আমরা সেই বাচ্চাটির ডিএনএ সংগ্রহ করব। ডিএনএতে দেখব সেখানে তার বড় ভাই বা বোনের সমস্যাটি আছে কি না! থাকলে তখন থেকেই শুরু হবে প্রতিরোধব্যবস্থা। জন্মের পরও এ রোগ নিরূপণ করা যায়। সে জন্য সেই মানুষটির ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখতে হবে তার সেই রোগ আছে কি না। যদি রোগটি পাওয়া যায়, তবে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা নিতে হবে! ফ্যাব্রি রোগ যত দ্রুত শনাক্ত করা যাবে এবং যত দ্রুত চিকিৎসা করা যাবে রোগের লক্ষণগুলো তত দেরিতে প্রকাশ পাবে। সে হয়তো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে না, তবে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।
বাংলাদেশে ফ্যাব্রি ডিজিজের প্রকোপ কী রকম? এ রকম কি হয় যে ফ্যাব্রি রোগ হয়েছে কিন্তু আমরা বুঝতেই পারিনি?
ফ্যাব্রি একটি বিরল জেনেটিক রোগ, যা ‘আলফা-গ্যালাকটোসাইডেজ এ’ নামক এনজাইম স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে। রোগটি দেহের বিভিন্ন অংশ, যেমন—ত্বক, চোখ, গ্যাসট্রোইন্টেস্টাইনাল সিস্টেম, কিডনি, হার্ট, ব্রেন এবং নার্ভাস সিস্টেমকে আক্রান্ত করে। মেডিসিননেট.কমের তথ্যমতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ৪০ হাজার পুরুষের একজন এ রোগে আক্রান্ত হয়। তীব্র ব্যথা, হাত-পায়ে পুড়ে যাওয়ার অনুভূতি, নাভি থেকে গোড়ালির ত্বকে ছোট, গাঢ় লাল দাগ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, গিরায় ব্যথা, তলপেটে অস্বস্তি ইত্যাদি হলো এ রোগের লক্ষণ।
ফ্যাব্রি রোগ বাংলাদেশেও আছে। আর এটা নিয়ে যেহেতু কেউ গবেষণা করে না, তাই কারো জানারও কথা নয়। কিন্তু ফ্যাব্রি রোগ অবশ্যই বাংলাদেশে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।
বাংলাদেশের ডাক্তার এবং গবেষকদের জন্য আপনার বার্তা!
আমরা (জাপানিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট) বিভিন্ন দেশের লাইসোসোমাল রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা দিই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের ড্রাই ব্লাড পাঠিয়ে থাকে। ‘ড্রাই ব্লাড’ হলো এক রনের কাগজে রক্তের কিছু শুকনো ফোঁটা। সেই রক্ত পরীক্ষা করে তাদের রোগ নিশ্চিত করে দিই। তারপর তারা সেই রোগগুলো নির্ধারণ করে চিকিৎসা দিতে পারে। মোট কথা, রোগটি কী তা জানা গেলে কিছু না কিছু চিকিৎসা তো চিকিৎসকরা করতেই পারবেন! কিন্তু রোগটিকে যদি চিহ্নিতই না করতে পারেন, তাহলে আপনি সে রোগের চিকিৎসা দেবেন কিভাবে?
ভারতের মতো এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, এমনকি কোরিয়াও আমাদের কাছ থেকে এসব পরীক্ষা করে নেয়। এর জন্য কিন্তু আমরা এক পয়সাও নিই না! সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ডাক্তাররাও এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।
ইয়ুভাল নোয়াহ হারারির ‘স্যাপিয়েন্সে ব্রিফ হিস্টোরি অব হিউম্যানকাইন্ড’ বইয়ে যেমনটা বলা হয়েছে, মানুষ ২০৫০ সালের মধ্যে অমরত্ব লাভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! তা ছাড়া ড. ইয়ান পিয়ারসনসহ অনেকেই এ সময়ের মধ্যে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ অমরত্ব লাভ করবে বলে ধারণা করছেন। একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে আপনার কাছে কি আদৌ এটা সম্ভব বলে মনে হয়?
বর্তমানে কিছু কিছু জায়গায় মানবদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে। অনেকে আশা করছেন প্রযুক্তির কল্যাণে আবার হয়তো তাঁরা বেঁচে উঠবেন। কিন্তু আমার কাছে এটা অবাস্তব বলে মনে হয়। মায়ের পেটে থাকা ভ্রূণের প্রাথমিক কোষগুলোই হচ্ছে এম্ব্রায়োনিক স্টেম সেল। এই এম্ব্রায়োনিক স্টেম সেলগুলো বিভাজিত হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হয়। আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে শরীর থেকে সাধারণ কোষ নিয়ে সেই কোষটিকে এম্ব্রায়োনিক স্টেম সেলে রূপান্তরিত করতে পারি। এই পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন জাপানের শিনইয়া ইয়ামানাকা। তাঁর পদ্ধতিটিকে অনুসরণ করে আমাদের ল্যাবেও এ কাজ করছি! এই এম্ব্রায়োনিক স্টেম সেল দিয়ে কোনো মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার জন্য চেষ্টা করছি। ধরুন, কোনো মানুষের একটি অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে। তখন গবেষণাগারে তার ত্বক থেকে টিস্যু নিয়ে এম্ব্রায়োনিক স্টেম সেল তৈরি করে তার সেই অসুস্থ কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করতে পারব। এ মুহূর্তে জাপানে বাণিজ্যিকভাবে এম্ব্রায়োনিক স্টেম সেল দিয়ে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির চিকিৎসা হচ্ছে।
এখন ধরুন, এভাবে আপনি একজন মানুষের সব অঙ্গ তৈরি করার মাধ্যমে গোটা মানবদেহটাই তৈরি করে ফেললেন। কিন্তু সেটিকে ‘চালু’ বা প্রাণ দেবেন কিভাবে? এ জন্য আমার মনে হয় এটা কখনো সম্ভব হবে না।
আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
বাংলাদেশের গরিব মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। দেশে যেসব রোগের পরীক্ষা সহজে করা সম্ভব নয় সেসব পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম ভূমিকা রাখতে পারতাম, তাহলে অনেক ভালো লাগত।
জেনেটিক রোগগুলোকে সহায়ক চিকিৎসা দিলে স্থায়ী কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। তাই এই আইপিএস গবেষণাকে নিয়ে যদি আরো বেশি গভীরে যেতে পারি, তবে রোগের স্থায়ী কোনো চিকিৎসা সম্ভব হবে। এই গবেষণাটিকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, সেখানে ওষুধ খেয়ে লাইসোসোমাল রোগের চিকিৎসা করা যাবে!

সম্মাননা হাতে ডা. আরিফ হোসেন
সংক্ষিপ্ত পরিচয়
ডা. আরিফ হোসেন গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। এগারো ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই সবার ছোট। বাবা ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মা ছিলেন গৃহিণী। মা চাইতেন আরিফ হোসেন বড় হয়ে বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার হবেন। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে শিশু বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। শিশু নিউরো-মেটাবলিক রোগের ক্লিনিক্যাল ফেলোশিপ করেন সেখান থেকেই। এই শিশু নিউরো-মেটাবলিক রোগবিশেষজ্ঞ বর্তমানে জাপানিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সিনিয়র রিসার্চার হিসেবে কাজ করছেন।
২০১৭ সালে নেচারের হিউম্যান জেনেটিকস সম্পর্কিত বিশেষ জার্নাল—‘জার্নাল অব হিউম্যান জেনেটিকসে’র সেরা তিন তরুণ বিজ্ঞানীর মধ্যে জায়গা করে নেন তিনি। নোয়েভ নামক একধরনের ছোট আকারের প্রোটিন দিয়ে ক্র্যাব্বে ডিজিজের চিকিৎসায় পৃথিবীতে তিনিই প্রথম সফল হন।
২০১৫ সালে এটি জার্নাল অব হিউম্যান জেনেটিকসে প্রকাশ পায়। পরে গবেষণাটি বিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলে জার্নাল অব হিউম্যান জেনেটিকসের বিশেষজ্ঞ প্যানেল তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করে।