রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, একইভাবে প্রতিটি ঘটনার পেছনে জনগণকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুখোমুখি করানোর প্রবণতা আমাদের ব্যস্ত রাখছে। এতে সামগ্রিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে সৃষ্টিশীল কাজে মনোনিবেশের সুযোগ। যাবতীয় অগঠনমূলক কাজের কালক্ষেপণে নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সময়।
যেখানে উন্নত বিশ্বের গবেষকরা মাথা ঘামাচ্ছেন আগামী দিনের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি, সেখানে আমাদের আনন্দ দুর্বৃত্তের স্বার্থ রক্ষায়। বলা হচ্ছে, কভিডের প্রতিক্রিয়ায় সারা পৃথিবীতে মানসিক স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়েছে তার কারণে আগামীতে যেকোনো সুস্থ ব্যক্তির জীবন ব্যাহত হলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে বৃহত্তর অর্থনৈতিক খাতে। বিশেষ করে উৎপাদনব্যবস্থা এবং মানবিক বিকাশ ব্যাহত হলে একটি দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধি তথা উন্নয়ন সূচকে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
সমাজ বিশ্লেষকরা আরো মনে করেন, কভিডের প্রাথমিক ধাক্কাটি এক অর্থে ভূমিকম্পের মতো। প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সাময়িক হলেও ভূমিকম্প দীর্ঘস্থায়ী হলে পুরো কাঠামো যেভাবে ভেঙে পড়ে, কভিডের পরবর্তী ধাক্কা হবে অনুরূপ। কভিডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্যে আঘাত এলে একজন ব্যক্তির মধ্যে হতাশা, অবসাদ, আত্মহত্যাপ্রবণতা, মানসিক অশান্তি, ধৈর্যচ্যুতি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকট হলে কাজের প্রতি অনীহা, উপার্জন হারানো, ব্যাংক লোন শোধ করতে না পারা ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলো উত্তরণে সফল না হলে কী ঘটতে পারে তা সহজে অনুমেয়। তাই অর্থনীতিতে অবদান রাখতে ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে নজর দিতে গবেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন।
অন্যদিকে আরেকটি বিষয়ে পৃথিবীতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তা হলো প্রযুক্তিগত দক্ষতার দ্রুত পরিবর্তন। এ বিষয়ে পৃথিবী ক্রমেই এগিয়ে চলেছে।
প্রতিটি উন্নত দেশ তার রাষ্ট্র পরিচালনার অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রতি মুহূর্তেই নিজেদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করছে। যার কারণে অ্যানালগ যুগের দাপ্তরিক কাঠামো এখন উন্নত পরিকাঠামোর দেশগুলো গ্রহণ করছে না। প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলতে পারলে প্রকারান্তে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে। এই পরিবর্তনের মাত্রা এতটাই দ্রুতগতিতে ঘটছে, যার সঙ্গে পাল্লা দিতে অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে হিমশিম খেতে হয়।
উদাহরণ হিসেবে বলতে হয়, ডিজিটাল ফরম্যাটে আমরা এখনো শতভাগ অভ্যস্ত হতে পারিনি, অথচ উন্নত বিশ্ব নিজেদের উন্নীত করে যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু জনগণের যাবতীয় চাহিদা মেটাবে তা নয়; একাধারে গৃহনির্মাণ, ব্যাংকিং লেনদেন, স্বাস্থ্যসেবা, নাগরিক সুবিধাদির দেখভাল করা ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও জনগণের মতামতকে বিশ্লেষণ করে সরকার গঠনে সহায়তা করার সক্ষমতা অর্জন করবে।
আপাতদৃষ্টে বিষয়টি আমাদের চোখে জটিল মনে হলেও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় যারা অভ্যস্ত তারা জানেন এটি শিগগির ঘটতে চলেছে।
আগামী এক দশকে পৃথিবীর এই পরিবর্তন আমাদের দেশে কেমন প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আধুনিক প্রযুক্তির উপরিকাঠামো ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত হলেও তা পুরোপুরি রপ্ত করতে পারিনি। শুধু মোবাইল ফোন, গাড়ি কিংবা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত বিনোদন উপকরণগুলো আমাদের নাগালের মধ্যে এলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিজেদের কল্যাণে ব্যবহারের ব্যুৎপত্তি কারিগরি জ্ঞান এবং মানবিক অভিরুচি আমাদের গড়ে ওঠেনি। যার কারণে সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহারের চেয়ে নেতিবাচক ব্যবহারের প্রবণতা সর্বত্র। এগুলো আমরা ব্যবহার করছি ব্যক্তিস্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে। এমনকি নিজ সংস্কৃতির শত্রু হিসেবে তাকে উপস্থাপন করতেও আমরা দ্বিধা করছি না।
একইভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও জনগণের সুবিধার্থে প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলো প্রণয়নে ‘গুড গভর্ন্যান্সের’ সুযোগ থাকলেও তার ব্যবহার সীমিত। জনগণের দাবি এবং অধিকার অগ্রাহ্য থাকায় অশান্তি-অসহযোগ স্বস্তি দিচ্ছে না।
আগামী দশকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুফল সামগ্রিক জীবনে উন্নতি ঘটাতে পারে তা জানা সত্ত্বেও তার জন্য টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে কালক্ষেপণ করা হবে বোকামি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন অবিমৃশ্যকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তার পরিণতি কেমন হতে পারে তার সাম্প্রতিক উদাহরণ যথেষ্ট।
ইতিহাসের পাতায় ফিরে গেলে দেখব, অতীতে এই অঞ্চল অর্থাৎ ভারতবর্ষ ছিল ইউরেশিয়ার সেলজুক তুর্কি-আব্বাসীয়-ফাতেমিদ-ইয়েমেনি-আফগান যোদ্ধাদের জন্য সোনার খনি। যার জের ধরে গজনির সুলতান মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০ খ্রিস্টাব্দ) একাই ১৭ বার উত্তর ভারত লুট করে যা পান নিজ দেশে নিয়ে যান। ধর্ম প্রচার তাঁদের প্রধান এজেন্ডা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দিল্লির দখলদার শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ, মোহাম্মদ ঘোরী, কুতুবুদ্দিন আইবেকদের মতো বখতিয়ার খিলজির মাথায়ও শাসনতন্ত্রের দণ্ড হাতে নেওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল ধর্মকে উপজীব্য করে।
বিশেষ করে বঙ্গদেশে ১২০১-০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙালিত্বের দিক বদলানোর ইতিহাস বুঝতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নেই। তখনো আমরা শোষিত এবং শাসিত হয়েছি, একবিংশ শতাব্দীতে নব্য বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নতুন ধারায় শোষিত হওয়ার উপলক্ষ তৈরি করছি নিজের অজ্ঞতায়।
দীর্ঘ পশ্চিমা শাসন এবং ঔপনিবেশিক পরিবেশে বসবাসের কারণে আমাদের অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণের যাবতীয় প্রস্তুতি স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পরও নিতে হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশে জাতির বিবেক ও মননের সক্ষমতা না থাকলে আগামী দশকেও সমূহ বিপদ।
লেখক : তথ্যচিত্র নির্মাতা, লেখক ও চিকিৎসক
mirajulislam1971@gmail.com


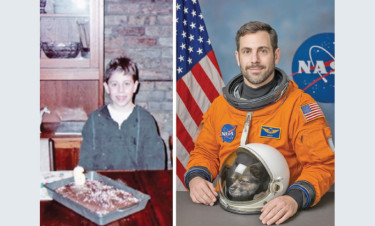





 বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সংকট ও অনাস্থার পরিবেশ নতুন নয়। অনাস্থার বেড়াজাল থেকে রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই বের হতে পারেনি। গণতন্ত্রের নামে এবং গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকারে রাজনৈতিক দলগুলো বারবারই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে এমনই এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে বিদ্যমান রাজনীতি।
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ইতিহাসে সংকট ও অনাস্থার পরিবেশ নতুন নয়। অনাস্থার বেড়াজাল থেকে রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই বের হতে পারেনি। গণতন্ত্রের নামে এবং গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকারে রাজনৈতিক দলগুলো বারবারই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সাম্প্রতিককালে এমনই এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে ঘুরপাক খাচ্ছে বিদ্যমান রাজনীতি।