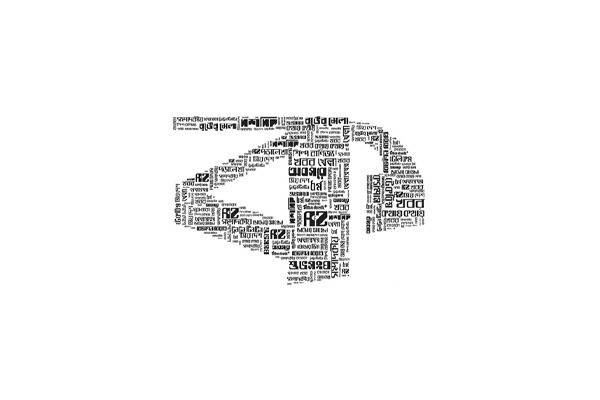নতুন সার্স কভ-২ বা করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের অনেক হিমশিম খেতে হয়েছে। কারণ আগের করোনাভাইরাস বা সার্স কভ-১ তথা সার্স মহামারির অস্তিত্ব তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেটা প্রাকৃতিকভাবেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য দ্রুততম সময়ে টিকা উদ্ভাবন করে বিজ্ঞানীরা এবার এক অত্যাশ্চর্য ভূমিকা পালন করেছেন।
৭০ শতাংশ টিকাদানের লক্ষ্য আমরা দ্রুতই অর্জন করতে পারব
- ডা. মুশতাক হোসেন
অন্যান্য
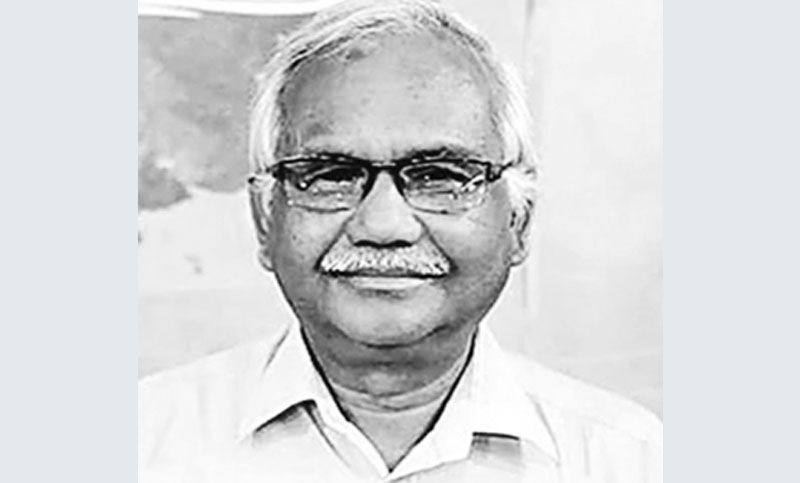
আবিষ্কৃৃত টিকাগুলোর উৎপাদনকারী দেশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যখন একের পর এক টিকার অনুমোদন দিতে থাকে, তখন থেকেই বাংলাদেশ টিকা আনার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। প্রধানত বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম থেকেই টিকার সমবণ্টনের ওপর জোর দিয়ে আসছিল।
শুরুতে টিকা উদ্ভাবনকারী দেশগুলোর বেশির ভাগই তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি ছিল না।
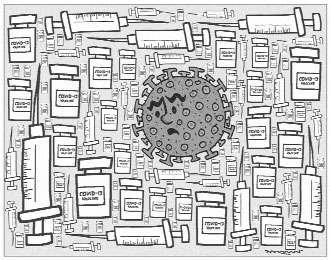 বন্ধ করে দেয়।
বন্ধ করে দেয়।আমরা এখন টিকা পাচ্ছি। কিন্তু কতটা ন্যায্যতার ভিত্তিতে পাচ্ছি সেটা একটা প্রশ্ন, যা সরবরাহকারীদের শর্তের কারণে আমরা জানতে পারছি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অতি উচ্চ আয়ের দেশগুলো উচ্চমূল্যে, মধ্যম আয়ের দেশগুলো মাঝারি মূল্যে এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলো সর্বনিম্ন মূল্যে টিকা পাওয়ার কথা। এখন বাস্তবে কী ঘটেছে সেটা হয়তো ভবিষ্যতে জানা যাবে। মানুষের মনে কৌতূহল আছে যে আমরা কি ন্যায্যতার ভিত্তিতে টিকাগুলো পেলাম বা আমাদের সরকার কতটুকু দর-কষাকষি করতে পেরেছে। তবে টিকা পাওয়াটা আমাদের জন্য খুব জরুরি। সে কারণেই হয়তো কৌতূহলটি গুরুত্ব পাচ্ছে না।
টিকা সংগ্রহের জরুরি কাজটা সরকার এখন করতে পারছে। আমরা অনুদানে কিছু টিকা পেয়েছি, কোভ্যাক্সের মাধ্যমেও পাচ্ছি। কোভ্যাক্সের মাধ্যমে আসা মডার্না ও ফাইজারের টিকার সংখ্যা অনেক। এই দুটি টিকা অনেক বেশি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয় এবং এটা বাংলাদেশ করতে পারছে। আমাদের এখন প্রধান কৌতূহল হয়ে উঠেছে টিকা প্রদানের হার এবং টিকা গ্রহণে মানুষের আগ্রহ।
প্রথমে যখন আমাদের টিকা আসেনি, তখন উচ্চ চাহিদা ছিল। মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা ছিল কেন টিকা আসছে না। কিন্তু টিকা আসার পর দেখা গেল নেতিবাচক প্রচারণার কারণে টিকার চাহিদায় ভাটা পড়েছে। এই প্রচারণাটা দেশে ছিল এবং দেশের বাইরেও ছিল। দুঃখজনকভাবে সেই ভাটার মধ্যেই ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে টিকা আসা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার চাহিদা বাড়ল। সেই চাহিদা বৃদ্ধির মধ্যেই এখন টিকা কার্যক্রম চলছে। এখন পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী টিকা দেওয়া হচ্ছে। তবে আরো চাহিদা বাড়া দরকার। আমাদের যদি দুই ডোজ এবং তিন ডোজ করে ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে হয়, তাহলে মানুষের চাহিদা ধরে রাখার পাশাপাশি টিকা সরবরাহের বর্তমান গতি অব্যাহত রাখতে হবে।
গতকাল সারা দেশে এক কোটি ডোজ নতুন টিকা দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগে একটা প্রচার ছিল যে প্রথম ডোজের টিকা আর দেওয়া হবে না। এই খবরটিই উল্টো মানুষকে টিকা নিতে আগ্রহী করে তুলেছে। তবে এটা ঠিক যে এই এক কোটি টিকা দেওয়ার পরও টিকা দিতে হবে আমাদের। যেহেতু ৭০ শতাংশকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
আশার বিষয় হচ্ছে, এখন বেশ চাহিদা লক্ষ করা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় দেখা গেছে টিকাকেন্দ্রগুলোতে লম্বা সারি। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। তবে একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, যেহেতু টিকাগুলো সারা বিশ্বেই শতভাগ কার্যকর নয়; কিন্তু গুরুতর অসুস্থতা কমায়, সে জন্য টিকা কর্মসূচি আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শতভাগ কার্যকর একটা টিকা হাতে না পাই।
সেই সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বিদ্যমান কভিড টিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি মেসেঞ্জার-আরএনএ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মডার্না ও ফাইজারের টিকা। তারা চেষ্টা করছে একটি সিঙ্গল ডোজ এম-এমআরএনএ টিকা নিয়ে আসার, যা একবার দিলে কভিড সংক্রমণ থেকে মুক্ত থাকা যাবে। এ জন্য বিদ্যমান টিকার আরো উন্নতি ঘটাতে হবে। এর মধ্যেই নতুন একটি আলোচনা হচ্ছে প্যান-সার্বিকোভাইরাস টিকা উদ্ভাবনের। প্রচলিত অর্থে এটাকে প্যান-করোনাভাইরাস টিকাও বলা হচ্ছে। শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাসকে সার্বিকোভাইরাস বলা হয়, যার একটি হচ্ছে সার্স কভ-২। আর সব ধরনের শ্বাসযন্ত্রের ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকাই হচ্ছে প্যান-সার্বিকোভাইরাস টিকা।
প্রস্তাবিত টিকাটি উদ্ভাবন করতে পারলে করোনাভাইরাসের যত রকম ভেরিয়েন্ট বা সাবভেরিয়েন্ট বের হোক না কেন, সব কটির বিরুদ্ধে সেটি কার্যকর হবে। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি ওয়েবিনার থেকে আশা করা হয়েছে মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাটি সফল হবে। এটা সফল হলে একই ধারাবাহিকতায় ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন টিকা বের হতে পারে। মোটকথা, যত রকম রেসপিরেটরি ভাইরাস মহামারি ঘটাতে পারে, সব কটির বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে প্যান-সার্বিকোভাইরাস টিকা। এমন যুগান্তকারী টিকা আবিষ্কারের পথে আছেন এখন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা।
বাংলাদেশের জন্য একটি সুখবর হচ্ছে, আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে মেসেঞ্জার-আরএনএ টিকা তৈরির প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে যাচ্ছি। এরই মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তারা এই প্রযুক্তি স্থানান্তরের একটি হাব তৈরি করেছে। আরো কিছু দেশে দিচ্ছে। বাংলাদেশ সেই তালিকায় আছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকা উৎপাদনের সক্ষমতা দেখেই বাংলাদেশের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এর পাশাপাশি আমার পরামর্শ হবে, আমাদের দেশে টিকা আবিষ্কারের যে প্রচেষ্টা চলছে সেটিকে আরো উৎসাহিত করা দরকার। আমরা যদি নিজেরা টিকা উদ্ভাবন ও উৎপাদন করতে পারি তা আমাদের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার প্রমাণ দেবে, দেশকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। এ ছাড়া এই টিকাটিও এম-আরএনএ টিকা। এটির বড় সুবিধা হলো এটি সাধারণ তাপমাত্রায়ই সংরক্ষণ করা যাবে। তবে এর কাজ চলছে ধীরগতিতে। অবশ্য কারণও আছে। উন্নত বিশ্বে কভিড টিকা তৈরির কয়েকটি ধাপ একসঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি টিকার পরীক্ষার ধাপগুলো একসঙ্গে করতে যাই, তাহলে দেখা যাবে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যারা প্রতিযোগী, তারা আমাদের টিকার বিরুদ্ধে নানা রকম প্রচারণা চালানোর সুযোগ পাবে। এই কারণে আমাদের টিকা আবিষ্কারক কর্তৃপক্ষ হয়তো কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। এটা আমার অনুমান। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেশে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নিয়ে কিছু মানুষের মধ্যে সন্দেহ আছে। এটা থাকা উচিত নয়। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করার বিষয়ে আমাদের রক্ষণশীল হলে চলবে না।
যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ যেভাবে বেড়েছে, তাতে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। আমাদের চাহিদা আছে, টিকার ঘাটতিও এই মুহূর্তে নেই। আবার মানুষের আগ্রহ আরো বাড়লে বেশি পরিমাণে টিকা আনাও কঠিন হবে না। কারণ সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা অনুষ্ঠানে দেখলাম এই মুহূর্তে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনকারীরা টিকা বেশি দিচ্ছে।
আমরা মনে হয়, ৭০ শতাংশ টিকাদানের লক্ষ্য আমরা দ্রুতই অর্জন করতে পারব। যতক্ষণ না সিঙ্গল ডোজের কোনো টিকা আসে আমাদের হয়তো সবাইকে তৃতীয় ডোজ এবং কারো কারো চতুর্থ ডোজও দিতে হতে পারে।
আমরা বিশ্বমারি কাটিয়ে উঠব সন্দেহ নেই। কিন্তু কভিড-১৯ বিশ্বমারি যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে সেটাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। সেটা হচ্ছে জনস্বাস্থ্যকে কেন্দ্রে রেখে আমাদের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিরাট বিরাট দামি যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ফাইভ বা থ্রি স্টারকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নয়, আমাদের কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য গ্রামাঞ্চলের মতো বড় বড় শহরেও এলাকাভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভিত্তিতে আমরা যদি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাই, তাহলে বাংলাদেশে করোনা মোকাবেলার যে ঘাটতি দেখা গেছে সেটা নিশ্চিতভাবে পূরণ হয়ে যাবে।
লেখক : উপদেষ্টা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)
সম্পর্কিত খবর
ন্যাটোর বর্ধিত প্রতিরক্ষা ব্যয় ও বৈশ্বিক উদ্বেগ
- ড. সুজিত কুমার দত্ত

সম্প্রতি পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য দেশগুলোর প্রতিরক্ষা বাজেট অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির বিষয়টি বিশ্ব উদ্বেগ নিয়ে দেখছে। ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশ নির্ধারণের ব্যাপারে একমত হয়েছে। এই সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত শুধু ন্যাটোর নিজস্ব ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কৌশলই নয়, বরং সমগ্র বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করতে যাচ্ছে।
ইউক্রেন যুদ্ধ ন্যাটোর সদস্য দেশগুলোকে তাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানোর এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থার প্রতি আরো বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন করেছে।
ন্যাটোর নতুন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০৩৫ সালের মধ্যে তাদের জিডিপির ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত মূল খাতে ব্যয় বা বিনিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।
ন্যাটোর এই পদক্ষেপ বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করবে, যার বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে। প্রথমত, ন্যাটোর সম্মিলিত সামরিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং শক্তিশালী সামরিক কাঠামো সম্ভাব্য আগ্রাসীদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে। ইউরো-আটলান্টিক অঞ্চলে ন্যাটোর উপস্থিতি আরো জোরদার হবে, যা এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করবে।
দ্বিতীয়ত, ন্যাটোর এই বিশাল প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি রাশিয়া, চীন এবং তাদের মিত্রদের তাদের নিজস্ব সামরিক ব্যয় আরো বাড়াতে উৎসাহিত করবে।
তৃতীয়ত, জিডিপির ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলোর জন্য একটি বিশাল আর্থিক বোঝা। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে পারে এবং জনসাধারণকে সামাজিক খাতে (যেমন—স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, অবকাঠামো) কম বরাদ্দ নিয়ে চলতে হতে পারে। এই ব্যয়ভার বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে যদি অন্যান্য দেশও একই পথে হাঁটে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
চতুর্থত, ন্যাটোর এই সামরিকীকরণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য নতুন উদ্বেগ তৈরি করতে পারে। উন্নত দেশগুলো যখন তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়, তখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন সহায়তা, মানবিক সাহায্য বা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া বৈশ্বিক মেরুকরণ বাড়লে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বড় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার শিকার হতে পারে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পঞ্চমত, ন্যাটোর এই পদক্ষেপ বিশ্বকে আরো বেশি সামরিক জোটকেন্দ্রিক ও মেরুকৃত করতে পারে। ন্যাটো একটি শক্তিশালী সামরিক জোটে পরিণত হলে এর বিপরীতে রাশিয়া-চীন অক্ষ আরো শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করবে, যা বিশ্বকে দুটি প্রধান সামরিক ব্লকে বিভক্ত করার দিকে ঠেলে দিতে পারে।
ন্যাটোর বর্ধিত প্রতিরক্ষা বাজেট বিশ্বকে এক নতুন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্তকে ন্যাটোর অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য মনে করা হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি অবশ্যই জাতীয় নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, তবে তা যেন বৈশ্বিক শান্তি ও সহযোগিতার মূল্যবোধকে ছাড়িয়ে না যায় তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এই মুহূর্তে সামরিক ব্যয়ের প্রবণতা থেকে সরে এসে কূটনীতি, আলোচনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর জোর দেওয়া পূর্বের চেয়েও বেশি জরুরি। ন্যাটোর এই সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক নিরাপত্তায় কী ধরনের নতুন সমীকরণ নিয়ে আসে, তা সময়ই বলে দেবে। তবে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল বিশ্ব গড়ার জন্য সব দেশেরই দায়িত্বশীল আচরণ এবং দূরদর্শী পদক্ষেপ প্রয়োজন।
লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
datta.ir@cu.ac.bd
জুলাই আন্দোলন : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
- সাঈদ খান

শুধু রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে—শুধু ভিন্নমত পোষণ করলেই—একটি রাষ্ট্র যদি তারই নাগরিকদের ধরে নিয়ে যায়, দিনের পর দিন বন্দি করে রাখে, নির্মম, নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অবর্ণনীয় নির্যাতনে হত্যা করে, তারপর নিথর দেহটি পর্যন্ত গোপনে গুম করে ফেলে, তাহলে প্রশ্ন উঠে এই বর্বরতা থেকে রাষ্ট্র কী আনন্দ পায়? রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি—এতটা নিষ্ঠুর কিভাবে হতে পারে? আয়নাঘরের ইতিহাস আমাদের সামনে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে—যেখানে প্রতিটি গুম, প্রতিটি নিষ্ঠুরতা আর প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানবতা বারবার হেরে গেছে রাষ্ট্রীয় পাশবিকতার কাছে। এই ভয়ংকর ইতিহাস থেকে কি আগামী দিনের সরকার ও তার নিরাপত্তা বাহিনী কোনো শিক্ষা নেবে? নাকি আগের মতোই নিষ্ঠুরতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে? তবে আমরা সেই খুনি রাষ্ট্র দিয়ে কী করব?
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান ছিল দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে জনতার এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। এটি ছিল গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম ও বৈষম্যহীন সমতার বাংলাদেশ গড়ার ডাক। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, সুশাসন এবং ন্যায্য সমাজ গড়ার প্রত্যাশা।
এই গণ-আন্দোলন হঠাৎ গড়ে ওঠেনি।
এই আন্দোলনের ফলেই গঠিত হয় একটি অন্তর্বর্তী সরকার।
৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর নতুন করে শুরু হয় হামলা-মামলা, সন্ত্রাস, খুন, নির্যাতনের ধারা।
গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনা ছিল বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া। কিন্তু আজও সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সংস্কার প্রশ্নেও অস্পষ্টতা দেখা দেয়। ‘সংস্কার’কে শুধুই একটি টিক দেওয়ার নীতিপত্রে পরিণত করে ধোঁয়াশাপূর্ণ করে তোলা হয়। নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় নিয়ে সংশয় ও বিভ্রান্তি বাড়ে।
২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করলেও তাদের প্রস্তাবনা ও রাজনৈতিক ভাষা সাধারণ মানুষের বাস্তবতা ও চেতনার সঙ্গে মেলেনি। ‘বাংলাদেশ’ নামবদলের চিন্তা, ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’-এর পরিবর্তে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’—এসব প্রচেষ্টা বিভ্রান্তি তৈরি করে। ‘দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র’, ‘রিসেট বাটন’, ‘নতুন সংবিধান’ ইত্যাদি ধারণা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাস্তবতাবিবর্জিত বলে অনেকে মনে করেন।
দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা আলাদা করা, উচ্চকক্ষ গঠন, ১৭ বছর বয়সে ভোটাধিকার—এসব প্রস্তাব সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজকে হুমকি, আর নেতাদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তারা হয়ে ওঠে শহুরে শ্রেণির কল্পনানির্ভর এক রাজনৈতিক কাঠামো।
অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিচারহীনতা, গুম-খুন অব্যাহত, মাজার ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা রক্ষায় এই সরকারের অবহেলা সমাজে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি করেছে। উগ্রবাদী গোষ্ঠী ও সহিংস কর্মকাণ্ড সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থতার জ্বলন্ত প্রমাণ। অভ্যুত্থানের পর ১১ মাস ধরে চলা মব কালচার, দমন-পীড়ন, প্রতিহিংসামূলক হামলা—এগুলো স্পষ্ট করে জনগণের বিজয়ের পরও শাসনযন্ত্রের ব্যর্থতা। স্বৈরাচার ও তাদের দোসরদের বিচার না হওয়ায় জনগণ বেআইনি পথে ঝুঁকছে। মানুষ বুঝতে পারছে, আন্দোলন সফল হলেও ক্ষমতা কাঠামোর বদল না ঘটলে কোনো অর্থ নেই।
এই পরিস্থিতিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, ‘নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই, নির্বাচনই একমাত্র বিকল্প।’ তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক, গ্রহণযোগ্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে পরিচালিত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আহবান জানান। তাঁর মতে, ‘গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি বৈধ, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রয়োজন।’
গণতন্ত্র শুধু একটি শাসনব্যবস্থা নয়; এটি মানুষের অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তার প্রতীক। গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো জনগণের মতামত এবং অংশগ্রহণ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে বহুবার বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পেছনে সাধারণ মানুষের যে ত্যাগ, তা শুধু সুশাসন এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করলেই সার্থক হবে।
২০২৪ সালের এই আন্দোলনের চূড়ান্ত অর্জন হতে পারে স্থায়ী রাজনৈতিক সমঝোতা, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা ও গণভিত্তিক সরকার। সংস্কার ছাড়া নির্বাচন নয় কিংবা আগে নির্বাচন তারপর সংস্কার—এই বিতর্কের বাইরে বাস্তবতা হলো : সংস্কার ও নির্বাচন উভয়ই জরুরি। কারণ জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত না হলে সুশাসন ও গণতন্ত্র টেকসই হয় না। ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করে জনগণই প্রধান শক্তি। তারা ভোট, মতপ্রকাশ ও আন্দোলনের মাধ্যমে নেতৃত্ব বদলায়, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করে।
এ জন্য নির্বাচনব্যবস্থায় প্রথমেই সংস্কার দরকার, যাতে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য ভোট হয়। সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী রোডম্যাপ ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব গড়া সম্ভব নয়। অতএব জনগণের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচিত, জবাবদিহিমূলক সরকার ও সংসদ গড়াই হবে অন্তর্বর্তী সরকারের যাবতীয় সংস্কার কার্যক্রমের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া সংস্কার কখনোই কার্যকর ও টেকসই হয় না।
জুলাই আন্দোলন আমাদের শেখায়—গণ-আন্দোলন যদি জনগণের দ্বারা গড়ে ওঠে, তবে তার ফসলও হতে হবে জনগণের হাতে।
লেখক : সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংগঠনিক সম্পাদক, ডিইউজে
উপকূলীয় জনজীবন রক্ষায় জরুরি উদ্যোগ প্রয়োজন
- বিধান চন্দ্র দাস

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেরও উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানকার কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। এই অঞ্চলের মানুষ চর্মরোগ, ডায়রিয়া এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত হচ্ছে।
গত বছর জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ‘লবণাক্ত মাটির বৈশ্বিক অবস্থা’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রায় ১৪০ কোটি হেক্টর ভূমি (মোট ভূমির ১০ শতাংশেরও কিছু বেশি) এরই মধ্যে লবণাক্ততার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আরো অতিরিক্ত ১০০ কোটি হেক্টর জমি জলবায়ু সংকট ও মানবিক অব্যবস্থাপনার কারণে ঝুঁকির মুখে পড়েছে।
সব থেকে বেশি জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় (৩৫.৭ কোটি হেক্টর)। এর পরে আছে আর্জেন্টিনা (১৫.৩ কোটি হেক্টর)।
 সাধারণভাবে ভূমির উপরিভাগ, মাটি বা শিলায় কিংবা নদী বা ভূগর্ভস্থ পানিতে স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ থাকলে সেই মাটি, শিলা, নদী বা ভূগর্ভস্থ পানিকে লবণাক্ত বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এই লবণ বলতে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড মিলে যে লবণ তৈরি হয় (সোডিয়াম-ক্লোরাইড : রান্নায় কিংবা খাবারে ব্যবহারযোগ্য) শুধু সেই ধরনের লবণ নয়। প্রকৃতপক্ষে লবণাক্রান্ত মাটি বা পানিতে একাধিক লবণ পাওয়া যায়। সাধারণত ১২ প্রকার লবণ দ্বারা জমি বা পানি লবণাক্ত হয়।
সাধারণভাবে ভূমির উপরিভাগ, মাটি বা শিলায় কিংবা নদী বা ভূগর্ভস্থ পানিতে স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণ লবণ থাকলে সেই মাটি, শিলা, নদী বা ভূগর্ভস্থ পানিকে লবণাক্ত বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এই লবণ বলতে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড মিলে যে লবণ তৈরি হয় (সোডিয়াম-ক্লোরাইড : রান্নায় কিংবা খাবারে ব্যবহারযোগ্য) শুধু সেই ধরনের লবণ নয়। প্রকৃতপক্ষে লবণাক্রান্ত মাটি বা পানিতে একাধিক লবণ পাওয়া যায়। সাধারণত ১২ প্রকার লবণ দ্বারা জমি বা পানি লবণাক্ত হয়।
কোটি কোটি বছর ধরে ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের ধারায় লবণ বা লবণের উপাদানসমূহ ভূতাত্ত্বিক স্তরসমূহে সঞ্চিত হয়েছে। প্রাকৃতিক (বৃষ্টি, নদী, বাষ্পীভবন, সমুদ্রতলের আগ্নেয় ছিদ্র, ভূগর্ভস্থ গ্যাস ও লাভা ইত্যাদি) এবং মানবসৃষ্ট (ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, খনিজ সম্পদ আহরণ, বনভূমি ধ্বংস ও ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ইত্যাদি) কারণে ভূতাত্ত্বিক স্তর থেকে এসব লবণ কিংবা লবণের উপাদান জলাশয় ও মাটির ওপরে এসে পড়ে। কোটি কোটি বছর ধরে পূর্বোল্লিখিত প্রাকৃতিকভাবে সমুদ্রবক্ষে লবণ জমা হওয়ার কারণে সমুদ্রের পানি বেশি পরিমাণে লবণাক্ত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সেই লবণাক্ত পানি নানা প্রক্রিয়ায় (জলোচ্ছ্বাস, পানির ঘনত্বে পার্থক্য, শূন্যতা পূরণ ইত্যাদি) সমুদ্রসংলগ্ন ভূমিতে ঢুকে লবণাক্ততা সৃষ্টি করে। সমুদ্র সংযোগহীন দেশগুলোতে ভূস্তরে মিশে থাকা লবণ নানাভাবে বিশেষ করে বৃষ্টি, নদীর স্রোত, সেচ (ভূগর্ভস্থসহ) ইত্যাদির মাধ্যমে জমিতে জমা হয়ে থাকে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক, শিল্পবর্জ্যের দ্বারাও জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হতে পারে।
খাদ্য নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক মাটির স্বাস্থ্যের ওপর বড় ধরনের হুমকির মোকাবেলায় এফএও তাদের ‘গ্লোবাল সয়েল পার্টনারশিপ’-এর মাধ্যমে ২০২১ সালে লবণাক্ত মাটিবিষয়ক এক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, ‘ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব সল্ট-অ্যাফেক্টেড সয়েলস (ইনসাস)’ গঠন করে। ‘গ্লোবাল সয়েল পার্টনারশিপ’ খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য লবণাক্ত মাটি ব্যবস্থাপনায় জরুরি ও সমন্বিত বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে। লবণাক্ত জমিতে লবণসহিষ্ণু ফসল ও হ্যালোফাইট (লবণপ্রিয় উদ্ভিদ) চাষ বৃদ্ধি করা এবং এসব ফসলের বাজার গড়ে তোলাসহ তাতে আর্থিক সহায়তা দানের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশে ২৬ লাখ একরেরও বেশি জমি লবণাক্ততার শিকার (এফএও, ২০২৪)। বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) থেকে বলা হয়েছে যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৮টি জেলার ৯৩টি উপজেলা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততায় আক্রান্ত। গত বছর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাটিতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ লবণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ০.০৫ মিলিসিমেন্স/সেন্টিমিটার ও ৯.০৯ মিলিসিমেন্স/সেন্টিমিটার (সরকার ও অন্যান্য, ২০২৪)। সাধারণত মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই অঞ্চলে সব থেকে বেশি লবণাক্ততা বিরাজ করে।
সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা সেখানকার কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করছে। দেশের দক্ষিণ-মধ্য-উপকূলীয় অঞ্চলে উচ্চ লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমিতে নিম্ন লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমির তুলনায় ৮০ শতাংশের বেশি পরিমাণ বোরো ধান কম উৎপাদন হতে পারে (ভূঁইয়া ও অন্যান্য ২০২৩)। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিরাজমান লবণাক্ততা সেখানকার জনস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকি তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ চর্মরোগ, ডায়রিয়া এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত হচ্ছে। মেয়েদের প্রজননগত সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে উচ্চ লবণাক্ততাযুক্ত পানীয়জল উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সৃষ্টি করছে (নাহিয়ান ও অন্যান্য, ২০১৮)।
বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের সময় জমি ও পুকুরে নোনা পানি ঢুকে পড়া, ভূগর্ভে নোনা পানির অনুপ্রবেশ, চিংড়ি চাষ, লবণ চাষ, নদীতে পলি জমা, নদীর স্রোত কমে যাওয়া ইত্যাদিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মিলিত অভিঘাত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধি এবং উজানে মিঠা পানির প্রবাহ পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাবের কারণে নদীর পানির লবণাক্ততা বাড়ছে বলে বলা হচ্ছে (বিশ্বব্যাংক, ২০২৫)।
এসআরডিআই থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত লবণাক্ততা রিপোর্টে লবণাক্ততা সমস্যা মোকাবেলায় ‘গবেষণা’ ও ‘উন্নয়ন’—এই দুটি উপ-শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো সুপারিশ করা হয়েছিল। রিপোর্টে পানি ও মাটি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন, লবণসহিষ্ণু ফসলের জাত উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থিত লবণ ধুয়ে ফেলা, মাটি ও পানির লবণাক্ততা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, অপ্রচলিত লবণসহিষ্ণু ফসলের সম্প্রসারণ, মৃত/মৃতপ্রায় নদী-খাল খননের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন সীমিত রাখা ইত্যাদিসহ মোট সুপারিশ সংখ্যা ছিল ২২টি।
‘লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র’ নামে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় এসআরডির একটি প্রতিষ্ঠান ২০০১ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে লবণাক্ততা মোকাবেলায় কাজ করছে। এরই মধ্যে এই কেন্দ্র থেকে কলস সেচ প্রযুক্তি, লবণাক্ত এলাকায় ডিবলিং পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ, খামার পুকুর প্রযুক্তি, দুই স্তর মালচিং পদ্ধতি ইত্যাদি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব কৌশলের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। জাভা (ইন্দোনেশিয়া)-র ‘সর্জন’ নামক একটি চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে জনপ্রিয় হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে উঁচু বেড এবং গভীর খাত পর্যায়ক্রমে তৈরি করা হয় এবং এর মাধ্যমে লবণাক্ততা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে বলে বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে। পানীয়জলের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পুকুর বালু ফিল্টার পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, লবণমুক্তকরণ ইউনিট স্থাপন, ভূ-উপরিস্থিত পানি শোধন প্লান্ট স্থাপন ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।
দেশের লবণাক্ততা মোকাবেলার জন্য এসআরডিআই-এর সুপারিশমালা ও উপরোক্ত কৌশলসমূহ একটি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশলও পরিবর্তন দরকার। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার লবণাক্ততা মোকাবেলার সামগ্রিক ও অভিযোজিত কৌশল বহু দশকের অভিজ্ঞতা ও সরকারের উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।
লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ইরানের পরমাণু স্থাপনায় আবারও মার্কিন হামলার শঙ্কা
- ড. ফরিদুল আলম

ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁদের মজুদ করা ইউরেনিয়াম সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না বা আদৌ এর কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে তাঁরা কিছু স্পষ্ট করেননি। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি কয়েক দশক পিছিয়ে দেওয়া গেছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা (আইএইএ) জানিয়েছে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচির খুব একটা ক্ষতি হয়নি এবং তারা কয়েক মাস বা তারও কম সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত সেন্ট্রিফিউজগুলো মেরামত করে নতুন করে ইউরেনিয়াম উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।
আইএইএ, ইরান বা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল, কাদের দাবি কতটুকু যৌক্তিক, তা পরিষ্কার নয়। তবে মার্কিন বিমান হামলার পর ইরানের পার্লামেন্ট তাদের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আইএইএকে আর কোনো ধরনের সহায়তা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সম্প্রতি দেশটির প্রেসিডেন্ট অনুমোদন দিয়েছেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যতই বলুন না কেন যে তাঁর দেশের বিমান হামলায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচি গুঁড়িয়ে দেওয়া গেছে, বাস্তবে তিনি যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তামুক্ত নন, এর আভাস পাওয়া গেছে তাঁর সাম্প্রতিক বক্তব্যে।
ইরানের পরমাণু সক্ষমতার বিষয়টি এখনো বহাল রয়েছে, এটি প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও ভেতরে ভেতরে যুক্তরাষ্ট্র খুব ভালো করে জানে যে তাদের এমন কিছু সক্ষমতা রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে যেকোনো ধরনের ক্ষতি তারা পুষিয়ে ওঠার সামর্থ্য রাখে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে যে ইরানের বর্তমান সরকারব্যবস্থা নিয়ে দেশটির ভেতরে ব্যাপক জন-অসন্তোষ থাকলেও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা যখন বিপন্ন হতে বসে, তখন ইরানিরা সবাই এক জাতীয়তাবাদী আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হয়। ইরানের সাবেক শাহর নির্বাসিত পুত্র রেজা শাহকে নিয়ে ইসরায়েল এবং পশ্চিমারা আবারও ইরানের ভেতরে সরকারবিরোধী আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে চাইলেও ইরানে ইসরায়েলের হামলা এবং প্রাণহানি নিয়ে তিনি ইসরায়েলের প্রশংসা করে সরকারবিরোধীদেরও রোষানলে পড়েছেন। পশ্চিমারা রেজা শাহকে সামনে নিয়ে ইরানে নতুন করে কোনো বিপ্লব সংগঠিত করতে চাইলে এ ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতা অনিবার্য। তবে ইরানকে আবারও ঘুরে দাঁড়ানো দেখাটাও তাদের জন্য এক চপেটাঘাতের শামিল। আর সে জন্যই ইরানের নীতিনির্ধারকরা পর্যন্ত এটি শঙ্কা করছেন যে আইএইএকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে না—এমন অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আবারও ইরানে হামলা করে বসতে পারে।
ইরানের অবস্থানকে সুবিধার মনে করছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্থিরতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নতুন সিদ্ধান্তে। গত ৪ জুলাই ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এই নিষেধাজ্ঞা ইরানের ওপর আগেকার নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম। এত দিন ধরে চাউর ছিল যে ইরানের তেল ও গ্যাস রপ্তানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থাকলেও শ্যাডো ফ্লিটের (গোপন জাহাজ) মাধ্যমে ইরান এই রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন করে জানা গেছে, ইরাকি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সালেহ আহমেদ সাঈদীর মালিকানাধীন বিভিন্ন কম্পানির মাধ্যমে ইরানের তেল ইরাকের তেলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আরব আমিরাত হয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে রপ্তানি হয়ে আসছে, যার মাধ্যমে বছরে ১০০ কোটি ডলারের বেশি আয় করছে ইরান। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ব্যবসায়ী সালেহর কম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, যেন ইরান এভাবে বাণিজ্য করে এর থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে তা সামরিক খাতে ব্যয় করতে না করে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করছেন, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি থেকে তাকে বিরত রাখতে হলে সর্বাগ্রে তার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের জায়গায় আঘাত করতে হবে। তবে এখানে একটি কথা থেকে যায়, যে ১০০ কোটি ডলার আয়ের কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে এটি ইরানের অর্থনীতিতে যে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তার পারমাণবিক সক্ষমতাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য, সেটি খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।
মোটকথা হচ্ছে, ইরান মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েলের স্বার্থের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এখন কথা হচ্ছে, ইরান যদি এমনটা মনে করে থাকে যে তারা আবারও সম্ভাব্য হামলা থেকে নিরাপদ নয়, সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতিরক্ষার ধরন কেমন হবে? এ ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কয়েকটি অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত, হরমুজ প্রণালি ঘিরে তারা তাদের কৌশলকে শাণিত করতে পারে, যেন পশ্চিমা বিশ্ব ইরানের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আগাম ধারণা পেতে পারে; দ্বিতীয়ত, তাদের নতুন করে আরো উন্নতমানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করে ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে; তৃতীয়ত, যুদ্ধাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইসরায়েলি প্রযুক্তির বিপরীতে নিজেদের প্রযুক্তি দুর্বল—এই বাস্তবতার আলোকে এটিকে আরো উন্নত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারা চীন ও রাশিয়ার সহায়তা নিতে পারে এবং চতুর্থত, রাশিয়ার সঙ্গে তাদের চলমান কৌশলগত সম্পর্ককে আরো কার্যকর করার পাশাপাশি চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে উন্নত করা এবং ইসরায়েলের যেমন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি শক্তি সর্বদা তাদের পাশে রয়েছে, ইরানকেও এমন পাশে থাকার মতো বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে হবে।
আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে গাজায় হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধের আপাত অবসান হতে চলছে বলে মনে হচ্ছে। এটি মানে এই নয় যে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। বরং হামাস, হুতি ও হিজবুল্লাহর মতো সংগঠনগুলোর দুর্বলতার এই সুযোগে ইরানকে আরো পর্যুদস্ত করার নতুন চেষ্টা করতে পারে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। তারা খুব ভালো করেই জানে এই সময়ে এসে তারা যদি ইরানকে ছাড় দেয়, তাহলে ইরান দ্রুতই আরো শক্তি সঞ্চয় করে তার প্রক্সিদের মাধ্যমে ইসরায়েলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। এসব যুক্তিতে ইরানে ফের হামলার শঙ্কা থেকেই যায়।
লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
mfulka@yahoo.com