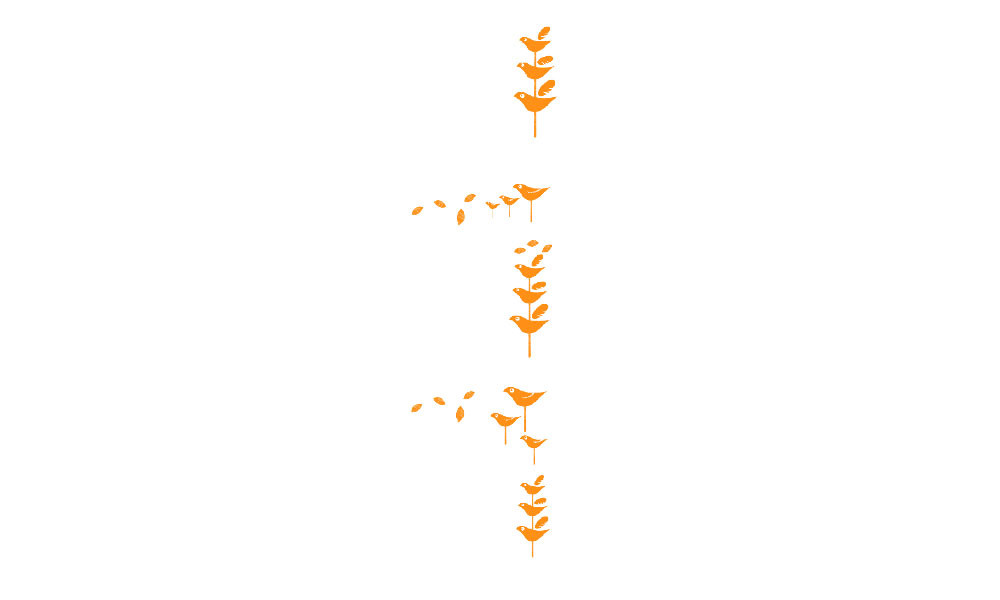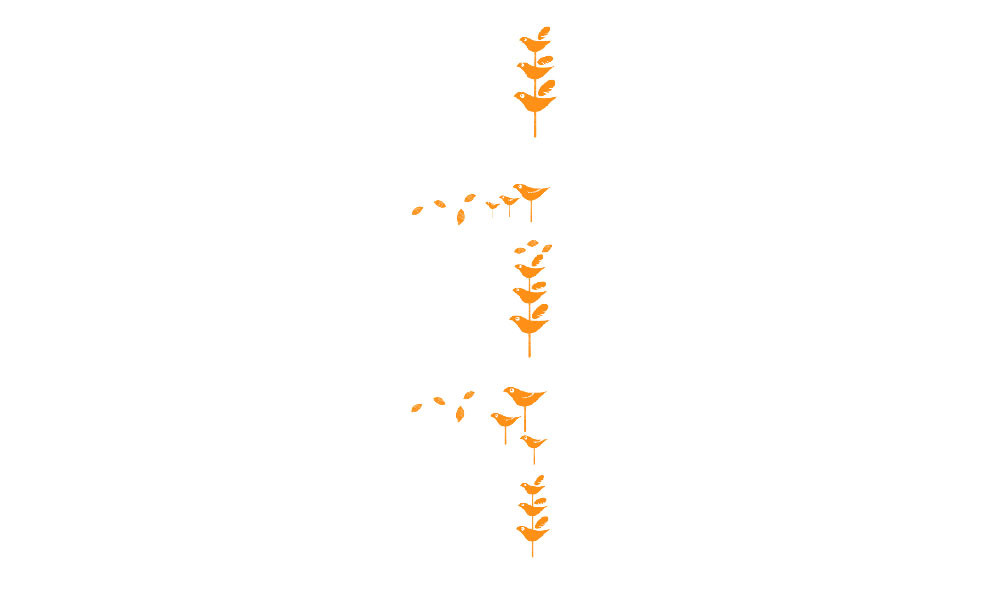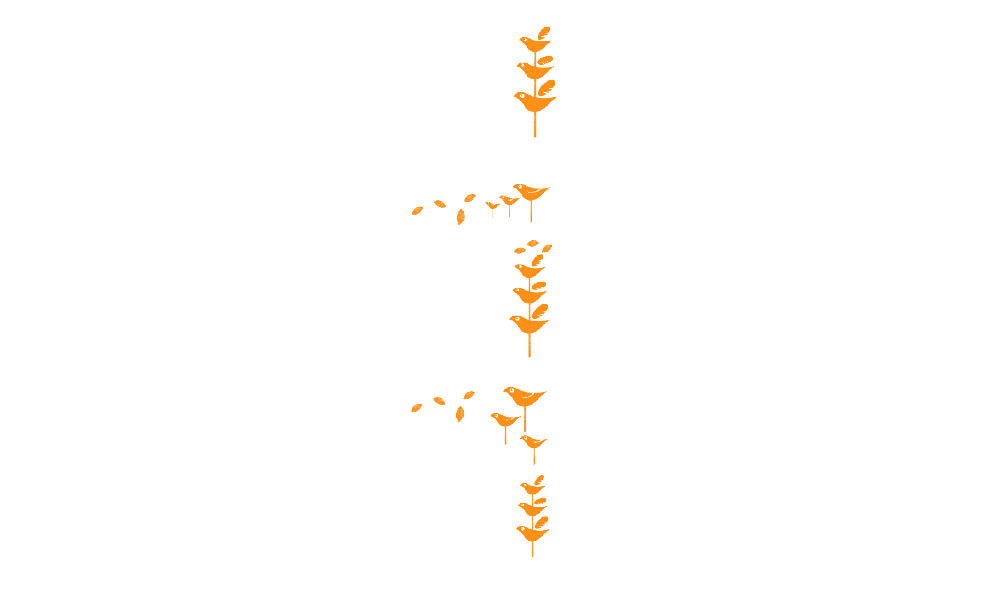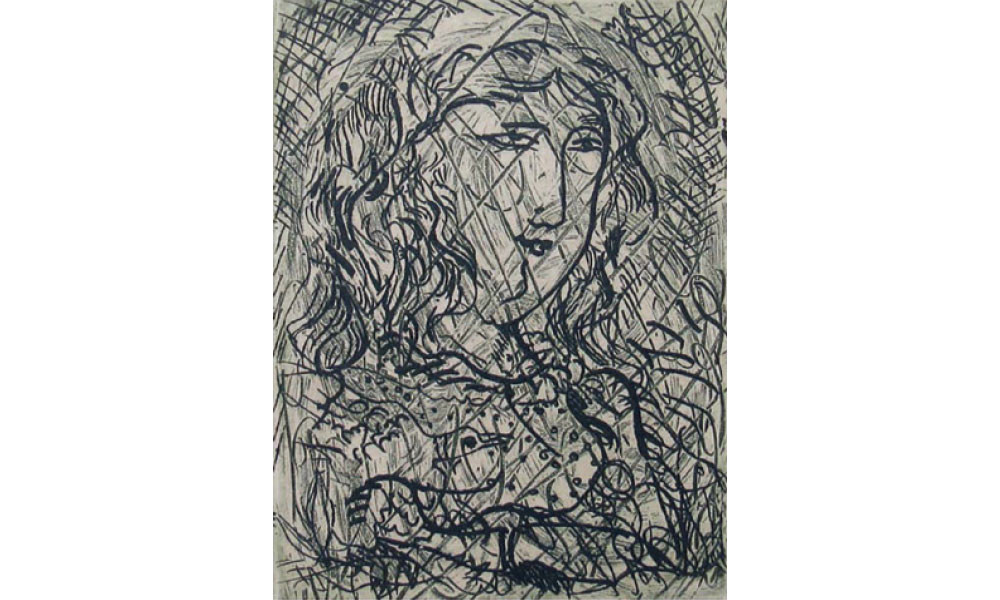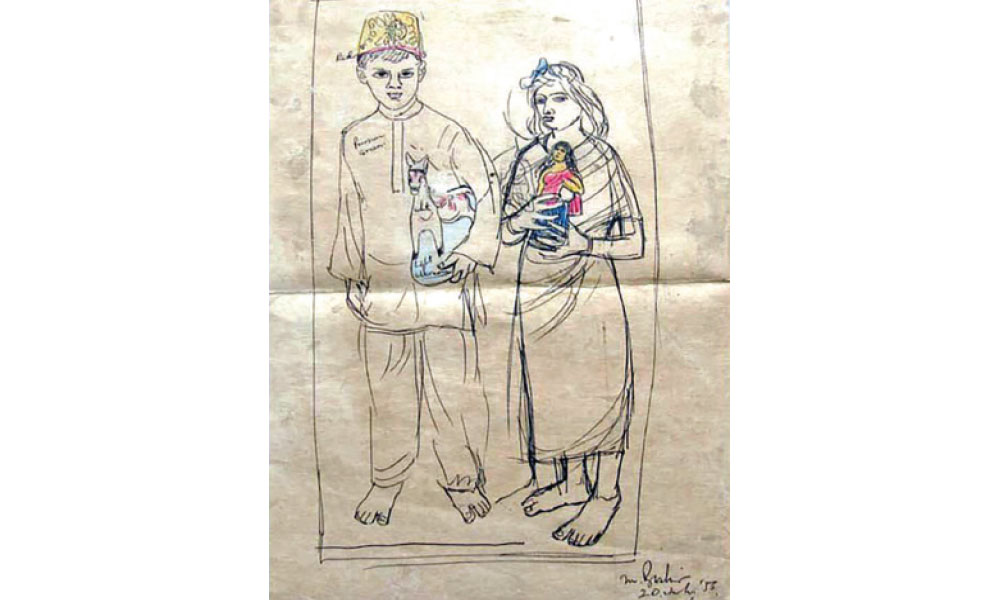সব বড় শহর। ইংল্যান্ড, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক। পৃথিবীর বড় বড় শহরের ফুটপাত ধরে হেঁটেছি। এর পেছনে ছিল জানার আগ্রহ, দেখার আগ্রহ।
শ্যামল : আল মাহমুদের নাম উচ্চারণের পাশাপাশি অনুচ্চারিত হয়েছে। সমালোচকরা বলেন যে কবি আল মাহমুদ তাঁর আগের চিন্তা-চেতনা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন।
আল মাহমুদ : এটা সত্য নয়। আমার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এসেছে পড়তে পড়তে। খ্যাতি, প্রতিপত্তি তো এমনি এমনি হয়নি। কষ্ট করতে হয়। আল্লাহ খ্যাতি, প্রতিপত্তি মানুষকে দেন। আমাকেও দিয়েছেন।
শ্যামল : যখন বাড়ি থেকে চলে এলেন ঢাকায়, তখন আপনি কি ধরে নিয়েছিলেন কবিতা লেখাই আপনার কাজ বা কবিতাই আপনার সব?
আল মাহমুদ : আমি তো কবি হতেই চেয়েছিলাম। মানুষ তো আমাকে কবি বলেই ডাকে। এটা আমার ভালোই লাগে। এর চেয়ে আর বড় প্রাপ্তি কী হতে পারে জীবনে। আমি যা হতে চেয়েছিলাম, তা-ই হয়েছি।
শ্যামল : কিভাবে এই আত্মবিশ্বাস জন্মালো যে কবি হতে পারবেন?
আল মাহমুদ : আমি দেখেছি। শিখেছি। প্রচুর পড়েছি। যাঁরা বড় কবি তাঁদের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেল।
শ্যামল : এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় আপনার কবিতা ছাপানোর কথা কি বলবেন? এরপর তো আপনাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তাই নয় কি?
আল মাহমুদ : শ্যামল, তুমি ঠিক বলেছ। বুদ্ধদেব বসু তো আমাদের সময়কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। যখন তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলাম ‘তোমার একটি বা দুটি কবিতা ছাপা যাবে মনে হচ্ছে।’ কবিতা ভবন। ব্যস, আমার তো আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা। পরের সংখ্যায় আমার তিনটি কবিতাই ছাপা হয়েছিল।
শ্যামল : আপনার সময়ের সমাজ আপনাকে কিভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল?
আল মাহমুদ : প্রথম তো ঢাকায় এলাম। পরিচিত লোকজন আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলাম।
শ্যামল : এখন পর্যন্ত আপনার সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ বলে ধরা হয় সোনালী কাবিনকে। এটি স্নাতক পর্যায়েও পঠিত হচ্ছে। আপনি পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতায় এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। তা হলো লিরিকধর্মিতা। যা আপনার কবিতাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে।
আল মাহমুদ : আমি মনে করি যে মানুষের জীবন তো লিরিক্যাল, মানে গীতিময়তায় আচ্ছাদিত। সেখানে গীতিময়তার যে অভ্যাস বাংলা কবিতার ভেতরে রয়েছে, সেটা অব্যাহত থাকবে। কবিতার মধ্যে গীতপ্রবণতা, মিল, অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস—এগুলো মানুষ পছন্দ করে। এটা হলো বাংলা কবিতার আধুনিক অবস্থান। এটাকে আরো পরিশ্রুত করে বইতে দেওয়া উচিত। এতে বাংলা কবিতার উন্নতি হবে।
শ্যামল : আপনি একবার বলেছিলেন, ‘কবিরা তো প্রকৃতপক্ষে কখনো হার মানে না। যত দিন সে বেঁচে থাকে, তত দিন সে লিখতে চায়।’ আপনি সারা জীবন কবিতা নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা আপনি কিভাবে পেলেন?
আল মাহমুদ : আমি সব সময়ই বলি, কবি হলো বিজয়ী মানুষ। সে হার মানে না। তার তো পরাজিত সৈনিক না। কবির আত্মা সব সময় অপরাজিত। এর জ্বলন্ত উদাহরণ নজরুল ইসলাম। আর আমি তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ওখানে ‘লালমোহন স্মৃতি পাঠাগার’ ছিল। অনেক মূল্যবান বই ওখানে পেয়েছি এবং পড়েছি। কলকাতায় কোনো বই প্রকাশ হলে সেটা একদিন পরই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওই পাঠাগারে পাওয়া যেত। এটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল আমাদের কাছে।
শ্যামল : আপনার সময়কালের উল্লেখযোগ্য কবি কাকে মনে করেন, এপার-ওপার বাংলা মিলিয়ে। কাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন?
আল মাহমুদ : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তারা আমার বন্ধু ছিল।
শ্যামল : মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনাদের লেখালেখির কী অবস্থা ছিল?
আল মাহমুদ : মুক্তিযুদ্ধ এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমরা দুঃখ, লাঞ্ছনা অতিক্রম করেছি। সেই সময়ে আমরা লেখাটা বন্ধ করিনি। আমরা কখনো লেখা বন্ধ করিনি। আমরা বন্ধ্যা ছিলাম না।
শ্যামল : ১৯৭৫ সালে আপনার প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘পানকৌড়ির রক্ত’ প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আবু রুশদ মন্তব্য করেছিলেন—‘বাংলাদেশে আল মাহমুদের সমতুল্য অন্য কোনো কবির হাত থেকে এতটা ভালো গল্প বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। এটা তার সাহিত্যকে গুরুত্বে ঈর্ষণীয় এক মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস।’ এটা আপনার জন্য একটা বড় প্রাপ্তি। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে ‘পানকোড়ির রক্ত’ গল্পে আপনি লিখেছেন, ‘নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে আমি সেখানে এক পেশাদার শিকারির মত হাঁটু গেড়ে বাগিয়ে বসলাম। ... একটি শ্যামবর্ণ নারীর শরীর নদীর নীলিমায় আপন রক্তের মধ্যে তোলপাড় করছে।’ আপনি কি সত্যি কখনো শিকার করেছেন এবং আবু রুশদের মন্তব্য সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে কি?
আল মাহমুদ : আমি বন্দুক নিয়ে সে সময় শিকার করতাম। আমার বন্দুকের লাইসেন্স ছিল। তবে বেশিদিন নয়, অল্প কয়দিন শিকার করেছিলাম। পরে এই পাখি মারা আমার ভেতর এক ধরনের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করল। আমি সেটা আর করলাম না। বন্দুকটা ত্যাগ করলাম। আবু রুশদের এই কথার বিচার তো তোমরা করবে। আমি আর কী করব!
শ্যামল : আপনার লেখা উপন্যাস ‘উপমহাদেশ’ কিংবা ‘কাবিলের বোন’কে আপনি সার্থক লেখা বলে মনে করেন।
আল মাহমুদ : আমি তো মনে করি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’র পরে আমার এই বইটা। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। খুবই উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এর আঙ্গিক, গঠনরীতি ও ভাষা। এখানে আমাদের মুসলমানদের উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ রকম একটি বই আমি আর দেখতে পাই না।
শ্যামল : আপনি নতুন কাব্যচেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে, নিজস্ব লেখার ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলা কবিতায় এক অগ্রপথিক। আপনার বিবেচনায় কবিতা আসলে কী?
আল মাহমুদ : আমার ধারণা হলো, ‘কবিতা মানুষের এক ধরনের দীর্ঘশ্বাসের মতো।’ এটাই আমার মনে হয় কবিতা।
শ্যামল : আপনি আপনার লেখায় সব সময় জীবন, মানুষ ও স্বদেশের কথা বলেছেন। সাহিত্য তো মানুষের জন্য। আপনার সৃষ্ট সাহিত্যকে কিভাবে বিশ্লেষণ কিংবা মূল্যায়ন করবেন?
আল মাহমুদ : তা তো অবশ্যই। আমার লেখার মূল্যায়ন আমার কাছে এই যে আমার লেখা বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার একটা স্তরে উন্নীত হয়েছে। এবং যাঁরা শিল্প-সাহিত্য চর্চা করেন, বাংলা ভাষায় তাঁদের প্রায় সবাইকে আমার রচনা আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা ব্যাপকভাবে আমাকে পড়েছিলেন। এটা আমার মনে হয় এবং সেই সময় আমার কিছু লেখা আমার অজান্তেই অনুবাদ করেছিলেন। এটা আমাকে বিস্মিত করেছিল। খুব বেশি না, তবে অনেক লেখাই তখন অনুবাদ হতে শুরু করে। এটা আমার জন্য অনেক বড় গৌরবের ছিল। কারণ, আমার কিছু লেখা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে—এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের বিষয় ছিল।
শ্যামল : আপনার স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাই, যিনি আপনার অগোছালো জীবনকে দারুণভাবে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর কথা কিছু কি বলবেন?
আল মাহমুদ : সত্যি কথা বলতে কি, আমার স্ত্রী ছিল আমার জীবনে আল্লাহর একটা করুণাবিশেষ। সে অবশ্য বেশিদিন বাঁচেনি। সামান্য কিছুদিন বেঁছেছিল। আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম। আমার সব ব্যাপারে তার একটা কর্তৃত্ব করার অধিকার বর্তে গিয়েছিল। সেটা আমি দিইনি। সে-ই এটা আদায় করে নিয়েছিল। এটা কত বড় কথা, তা বলে বোঝাতে পারব না। এরপর সে যখন মরে গেল, আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। এখনো আমি নিঃসঙ্গ জীবনে আছি।
শ্যামল : আপনি উপন্যাসও লিখেছেন। আপনার কি নিজের আত্মজীবনী লেখার কোনো পরিকল্পনা আছে?
আল মাহমুদ : যদিও বিচ্ছিন্নভাবে আমি আত্মজীবনী লিখেছি। ‘যেভাবে বেড়ে উঠি’ কিংবা ‘আয়নায় কবির মুখ’। কিন্তু একটা অখণ্ড আত্মজীবনী লেখার পরিকল্পনা আছে। সেটা আমি এখনো পারিনি করতে।
শ্যামল : আপনার উপন্যাসে আঙ্গিক ও ভাষার কথা জানতে চাই। এবং আরো জানতে চাচ্ছি, বর্ণনা ও বক্তব্যের যে সম্মিলন করা হয় উপন্যাসে তা। এটা কতটা জরুরি বলে মনে করেন?
আল মাহমুদ : উপন্যাস সৃষ্টি করতে হলে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হয়তো অনেকেই মানবেন না। আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি লেখায় মানুষের সৃজনক্ষমতাকে। এ জন্য একটা আঙ্গিক দরকার হয়। আমার উপন্যাসে আমি যে আঙ্গিক ব্যবহার করেছি, সেটা আধুনিকতম আঙ্গিক বলে মনে করি। যেই আধুনিক কৌশল আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে আমি তা-ই ব্যবহার করেছি।
শ্যামল : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটা কথা বলেছিলেন যে ‘ওই যে প্রথম একটা লেখা মাথার ভিতর ঢুকে গেছে, এখন যতই চেষ্টা করি ওই পথ থেকে বের হয়ে আসবো তা আর হয়ে ওঠে না।’
আল মাহমুদ : হ্যাঁ, সে তো আমার বন্ধু। আমার একটা ধারণা যে যদি মাথার ভেতর একটা উদ্দীপনা বা প্রেরণা উত্থাপিত হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে মাথা থেকে না নামানো যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নাই। It will brun you, এটা তোমাকে পোড়াবে; তোমাকে জ্বালাবে, তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। যখন তুমি কলম নিয়ে বসবে, সেটা গল্প হোক, কবিতা হোক কিংবা উপন্যাস হোক—যখন তুমি লিখে ফেলবে, তখন তুমি একটি সিগারেট জ্বালিয়ে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।