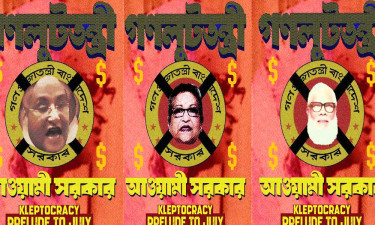রোগের ধরন
পোস্ট-পার্টাম মানে হচ্ছে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরবর্তী সময়। এই সময়ে একজন নারীর ডিপ্রেশনের উপসর্গ দেখা দিলে তাকে বলা হয় পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন। সাধারণত ১৫ শতাংশ মা এই রোগে ভুগে থাকেন। সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রথম দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে যেকোনো সময় এ রোগ শুরু হতে পারে।
মা দুঃখ ও হতাশায় ভোগেন। কখনো কখনো নিজেকে দোষী ভাবতে থাকেন। কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে পারেন না এবং কোনো কিছুতে উৎসাহ পান না। এমনকি বাচ্চার প্রতিও কোনো উৎসাহ থাকে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাচ্চার যত্ন-আত্তির ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে চরম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন, যা একসময় অবশেসনের পর্যায়ে চলে যায়।
কাদের বেশি হয়
১. পূর্বে যদি ডিপ্রেশনে ভোগার ইতিহাস থাকে, বিশেষ করে সন্তান জন্মদানের সময়
২. দাম্পত্য কলহ থাকলে
৩. পরিবার বা বন্ধুবান্ধব সহানুভূতিশীল না হলে
৪. সামপ্রতিক কোনো চাপে থাকলে
৫. বাচ্চার লালন-পালন কষ্টকর হলে
কেন হয়
সন্তান জন্মের এক সপ্তাহ পর সেক্স হরমোন এবং স্ট্রেস হরমোনের লেভেল ওঠানামা করে, যার ফলে মস্তিষ্কের যে অংশ আমাদের অনুভূতি ও সামাজিক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে, সেই অংশে বেশ পরিবর্তন হয় এবং উপসর্গগুলো প্রকাশ পায়।
লক্ষণ
১. বিষণ্ন অনুভূতি ও অশ্রু সংবরণ করতে না পারা
২. বাচ্চার ভালোমন্দ ও দায়দায়িত্ব চিন্তা করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া
৩. হতাশ হয়ে যাওয়া এবং নিজেকে অসমর্থ ও দোষী ভাবা
৪. খিটখিটে মেজাজ
৫. সব কিছুতে আগ্রহ ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, এমনকি নিজের মা হওয়ার ব্যাপারেও
৬. ক্ষুধামান্দ্য
৭. ঘুমের সমস্যা- দেরিতে ঘুম হওয়া আবার ঘুম থেকে উঠতে না পারা
৮. চরম ক্লান্তি
৯. ঘন ঘন মৃত্যুচিন্তা, কখনো কখনো আত্মহত্যার চিন্তা
১০. বাচ্চার যত্ন নিতে কষ্ট
এই উপসর্গগুলো সন্তান জন্মদানের দিন থেকে শুরু করে এমনকি তিন মাস পরও হতে পারে।
রোগ নির্ণয়
রোগ নির্ণয়ের জন্য এ রোগের ইতিহাসই যথেষ্ট।
এ ছাড়া এ রোগ নির্ণয়ের জন্য এডিনবার্গ পোস্ট-ন্যাটাল ডিপ্রেশন স্কেল ব্যবহার করা হয়। তবে অন্যান্য রোগ থেকে আলাদা করার জন্য রুটিন ল্যাবরেটরি টেস্টগুলো করা জরুরি।
চিকিৎসা
এ রোগের চিকিৎসা একজন গাইনোকলজিস্টের তত্ত্বাবধানে ও সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শে সমন্বিতভাবে হওয়া উচিত। এভাবে সমন্বিত চিকিৎসা নিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগী ভালো হয়ে যাবেন। চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে-
১. অ্যান্টি-ডিপ্রেশেন্ট ওষুধ : এসএসআরআই যেমন- ফ্লুক্সিটেন এবং এসএনআরআই যেমন- ভেনলাফেক্সিন ইত্যাদি দেওয়া হয় বিষণ্নতা দূর করার জন্য।
২. কগনেটিভ বিহ্যাভিউরাল থেরাপি- নিজেকে দোষী ভাবার প্রবণতা ঠিক করার জন্য।
৩. সাইকোডায়নামিক, ইনসাইট ওরিয়েন্টেড এবং ইন্টার-পারসোনাল সাইকোথেরাপি- এটা রোগীকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে এবং পূর্বের এমন কোনো ঘটনা উন্মোচন করতে ও বুঝতে সাহায্য করবে, যা তাঁর উপসর্গগুলোর জন্য দায়ী।
৪. কাপল থেরাপি- এটা মা-বাবাকে সাহায্য করবে নিজেদের অসম্মতির জায়গাগুলো বুঝতে এবং বাচ্চার যত্ন ও দায়দায়িত্ব কত ভালোভাবে পালন করা যায়, সে বিষয়ে একটা ঐকমত্যে পৌঁছতে।
৫. ব্রেস্ট ফিডিং- মা ও সন্তানের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করবে।
প্রতিরোধ
গর্ভবতী মায়েরা পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশনের ঝুঁকি কমাতে পারেন ভবিষ্যৎ মাতৃত্ব জীবনে যে পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসবে তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। অন্য মায়েদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে একটা শিশুর বাস্তবিক দৈনন্দিন প্রয়োজন ও যত্ন সম্পর্কে জানতে। সদ্যোজাত সন্তানকে প্রচুর সময় দেওয়ার ব্যাপারকে কখনোই অবহেলা করা যাবে না। জীবনসঙ্গী এবং অন্য যাঁরা সহানুভূতিশীল আত্মীয়স্বজন আছেন, তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারেও কোনো সংকোচ করা যাবে না।