সারা বিশ্বে প্রায় ১০ কোটির বেশি লোক বিভিন্ন ধরনের বিটা থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করে। প্রতিবছর প্রায় এক লাখ শিশুর জন্ম হচ্ছে জটিল থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে। বাংলাদেশে ৫০ লাখের বেশি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি ১৪ জনে একজন থ্যালাসেমিয়ার বাহক রয়েছে এবং ৭০ হাজারেরও বেশি শিশু এই থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত।
কালের কণ্ঠ-বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লি. গোলটেবিল— থ্যালাসেমিয়া রোগ : সচেতনতাই প্রতিরোধ
থ্যালাসেমিয়া : সম্মিলিত সচেতনতার বিকল্প নেই
- থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধ সম্ভব
অন্যান্য
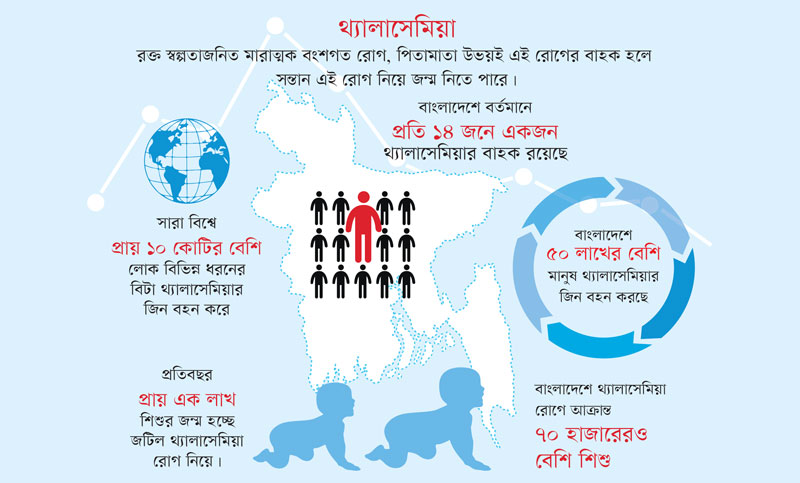
যাঁরা অংশ নিয়েছেন
স্বাগত বক্তব্য
ইমদাদুল হক মিলন
সম্পাদক, কালের কণ্ঠ ও পরিচালক, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ
সেশন সভাপতি
মোহাম্মদ এবাদুল করিম
সংসদ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
সম্মানিত অতিথি
অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ
উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
কাজী হাবিবুল বাশার
সাবেক অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ও নির্বাচক বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল
আলোচক
অধ্যাপক ডা. রোবেদ আমিন
পরিচালক, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
অধ্যাপক ডা. আবু জাফর মো. সালেহ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও কো-অর্ডিনেটর, হেমাটোলজি বিভাগ, ঢাকার এভারকেয়ার হসপিটাল
অধ্যাপক ডা. মাসুমা রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন
প্রফেসর ডা. মাসুদা বেগম
ডিন মেডিসিন অনুষদ ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান (হেমাটোলজি বিভাগ), বিএসএমএমইউ
ডা. মোহাম্মদ শরীফ
পরিচালক ও লাইন ডিরেক্টর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ড. ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার
ডিরেক্টর, হেলথ প্রগ্রাম, কেয়ার বাংলাদেশ
অভিজ্ঞতা বর্ণনা
ফারহিন ইসলাম
শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কাজী আশরাফ হোসেন
চেয়ারম্যান, ঘটক পাখি ভাই প্রা. লি.
প্রবন্ধ উপস্থাপক
খালেদা আক্তার সিনথিয়া
সহকারী ব্যবস্থাপক, অনকোলজি বিভাগ, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
সঞ্চালনা
তৌফিক মারুফ
ডেপুটি চিফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ
থ্যালাসেমিয়া ভয়ংকর হুমকি, তবে সতর্কতায় সুরক্ষা
মোহাম্মদ এবাদুল করিম এমপি
 থ্যালাসেমিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আলোচনার বিষয়। আজকে সময়ের দাবি সারা বিশ্বের জন্য থ্যালাসেমিয়া একটি ভয়ংকর হুমকি হিসেবে আসছে। এই হুমকি আসার আগেই আমরা আমাদের দেশকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি এ বিষয়ে বিজ্ঞদের মতামত জরুরি।
থ্যালাসেমিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আলোচনার বিষয়। আজকে সময়ের দাবি সারা বিশ্বের জন্য থ্যালাসেমিয়া একটি ভয়ংকর হুমকি হিসেবে আসছে। এই হুমকি আসার আগেই আমরা আমাদের দেশকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি এ বিষয়ে বিজ্ঞদের মতামত জরুরি।
থ্যালাসেমিয়া যে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, এটা আগে আমার ভাবনায় আসেনি। এই আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো এসেছে এগুলো কিভাবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে সরকারি লেভেলে কাজ করাতে সাহায্য করবে, এটা আশা করি ডিজি মহোদয়সহ সংশ্লিষ্টরা অবহিত করবেন।
অনেকের থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ নেই কিন্তু রোগের বাহক
অধ্যাপক ডা. রোবেদ আমিন
 বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩-৪ শতাংশ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। ১০ হাজার নবজাতকের মধ্যে ৩৩ শিশু থ্যালাসেমিয়ার রোগী। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করতে হলে দুটি পদ্ধতিতে এগোতে হবে। একটি পদ্ধতি হলো ডায়াগনস্টিক করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা। অন্যটি হলো প্রতিরোধ করা। ডায়াগনস্টিক চিকিৎসার আওতায় আছে হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রফোরেসিস পরীক্ষা। এটা খুবই ব্যয়বহুল। আর প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের কোথায় কোন রোগী আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনসিটি কর্নার করা হয়েছে। এটার উদ্দেশ্য হলো সেখানে যেসব রোগী যায় তাদের ভেতরে এ ধরনের সমস্যা থাকলে খুঁজে বের করা। অর্থাৎ একজন রোগী খুঁজে পেলে তার মা-বাবা কিংবা পরিবারের অন্যদের টেস্টের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অনেকে আছে লক্ষণ নেই, কিন্তু রোগের বাহক। পাশাপাশি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩-৪ শতাংশ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। ১০ হাজার নবজাতকের মধ্যে ৩৩ শিশু থ্যালাসেমিয়ার রোগী। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করতে হলে দুটি পদ্ধতিতে এগোতে হবে। একটি পদ্ধতি হলো ডায়াগনস্টিক করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা। অন্যটি হলো প্রতিরোধ করা। ডায়াগনস্টিক চিকিৎসার আওতায় আছে হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রফোরেসিস পরীক্ষা। এটা খুবই ব্যয়বহুল। আর প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের কোথায় কোন রোগী আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এনসিটি কর্নার করা হয়েছে। এটার উদ্দেশ্য হলো সেখানে যেসব রোগী যায় তাদের ভেতরে এ ধরনের সমস্যা থাকলে খুঁজে বের করা। অর্থাৎ একজন রোগী খুঁজে পেলে তার মা-বাবা কিংবা পরিবারের অন্যদের টেস্টের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অনেকে আছে লক্ষণ নেই, কিন্তু রোগের বাহক। পাশাপাশি প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।
বিয়ের রেজিস্ট্রিতে ব্লাড রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করতে হবে
প্রফেসর ডা. মাসুদা বেগম
 আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার ফলে থ্যালাসেমিয়া রোগটা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিবছর থ্যালাসেমিয়া দিবসে এটি গুরুত্ব পায়। পরে সবাই বিষয়টি নিয়ে একটু পিছিয়ে পড়ে। লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে ‘মীনা’ কার্টুন সমাজে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এই রোগ নিয়ে যদি মিডিয়া কথা বলে তবে সেটি সমাজে অনেক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি বিয়ের রেজিস্ট্রিতে থ্যালাসেমিয়া রক্তের রিপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক করা গেলে কাজে আসবে। পাশাপাশি সরকারি পরিচয়পত্রে ব্লাড গ্রুপের মতো হিমোগ্লোবিন ‘এ/বি’ নাকি থ্যালাসেমিয়া উল্লেখ থাকলে প্রতিরোধও অনেক সহজ হয়ে যাবে। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ বন্ধ করা, আর বিয়ে হয়ে গেলেও অনাগত বাচ্চাটা যেন আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার ফলে থ্যালাসেমিয়া রোগটা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিবছর থ্যালাসেমিয়া দিবসে এটি গুরুত্ব পায়। পরে সবাই বিষয়টি নিয়ে একটু পিছিয়ে পড়ে। লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে ‘মীনা’ কার্টুন সমাজে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এই রোগ নিয়ে যদি মিডিয়া কথা বলে তবে সেটি সমাজে অনেক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি বিয়ের রেজিস্ট্রিতে থ্যালাসেমিয়া রক্তের রিপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক করা গেলে কাজে আসবে। পাশাপাশি সরকারি পরিচয়পত্রে ব্লাড গ্রুপের মতো হিমোগ্লোবিন ‘এ/বি’ নাকি থ্যালাসেমিয়া উল্লেখ থাকলে প্রতিরোধও অনেক সহজ হয়ে যাবে। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ বন্ধ করা, আর বিয়ে হয়ে গেলেও অনাগত বাচ্চাটা যেন আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
হাজার হাজার বিয়ে দিয়েছি, কেউ কথা শোনেনি আশা করি এবার শুনবে
কাজী আশরাফ হোসেন
 আমি অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি—বিয়ের আগে আপনারা থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করে নিন, নইলে বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু আমার এ কথা তাঁরা শোনে না। আজকে এই আয়োজনের মাধ্যমে কালের কণ্ঠ এবং বিজ্ঞজনদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই আয়োজনের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা করায়। আশা করি, এবার মানুষজন শুনবে। কারণ এত বড় একটা বিষয় (থ্যালাসেমিয়া) নিয়ে সচেতনতা না থাকলে ভয়ংকর বিপদ হতে পারে। আমি হাজার হাজার বিয়ে দিয়েছি ঘটক হিসেবে, কিন্তু এটা (থ্যালাসেমিয়া) কেউ মানেনি। তারা বলে, আগে বিয়ে হোক, তারপর দেখা যাবে। আশা করি, এবার সবাই এটা শুনবে এবং মানবে। এটার মাধ্যমে অনেকের উপকার হবে, এটা আশা করি। যাঁরা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে এই আয়োজনটা করছেন তাঁদের আমার অফুরন্ত দোয়া রইল।
আমি অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি—বিয়ের আগে আপনারা থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করে নিন, নইলে বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু আমার এ কথা তাঁরা শোনে না। আজকে এই আয়োজনের মাধ্যমে কালের কণ্ঠ এবং বিজ্ঞজনদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই আয়োজনের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা করায়। আশা করি, এবার মানুষজন শুনবে। কারণ এত বড় একটা বিষয় (থ্যালাসেমিয়া) নিয়ে সচেতনতা না থাকলে ভয়ংকর বিপদ হতে পারে। আমি হাজার হাজার বিয়ে দিয়েছি ঘটক হিসেবে, কিন্তু এটা (থ্যালাসেমিয়া) কেউ মানেনি। তারা বলে, আগে বিয়ে হোক, তারপর দেখা যাবে। আশা করি, এবার সবাই এটা শুনবে এবং মানবে। এটার মাধ্যমে অনেকের উপকার হবে, এটা আশা করি। যাঁরা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে এই আয়োজনটা করছেন তাঁদের আমার অফুরন্ত দোয়া রইল।
থ্যালাসেমিয়ায় সচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে যুক্ত করতে হবে
ইমদাদুল হক মিলন
 থ্যালাসেমিয়া রক্তের এবং বংশগত একটি রোগ। আমাদের সবার সচেতনতাই পারে থ্যালাসেমিয়া থেকে রক্ষা করতে। এ ছাড়া যেকোনো রোগ বা দুর্যোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় সচেতনতা। এখন আমরা যে বিশ্ব করোনা মহামারিতে আছি, এর প্রায় দেড় বছর পার করছি। এটার বেলায়ও লক্ষ করছি, মানুষের সচেতনতাই প্রধান প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করেছে। সচেতনতাই মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছে বা করছে। থ্যালাসেমিয়ার বিষয়েও সচেতনতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই। আর এই সচেতনতা কিভাবে তৈরি করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে নানাভাবে আরো বেশি যুক্ত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের অনেক মিডিয়া রয়েছে। এ জায়গাগুলোতে যদি আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে বোঝাতে পারি এটা কিভাবে আপনাকে রক্ষা করবে, তাহলে যেকোনো রোগের ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সম্ভব। কারণ আমি মনে করি কোনো রোগ হওয়ার আগে যদি সচেতন হওয়া যায় এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। তাই বলব, সচেতনতা অতি জরুরি। আর আমরা মিডিয়ার পক্ষ থেকে সচেতনতা তৈরির কাজটি নিয়মিত সব সময় করে থাকি। বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই তারা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের বরাবরই যুক্ত করেন।
থ্যালাসেমিয়া রক্তের এবং বংশগত একটি রোগ। আমাদের সবার সচেতনতাই পারে থ্যালাসেমিয়া থেকে রক্ষা করতে। এ ছাড়া যেকোনো রোগ বা দুর্যোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় সচেতনতা। এখন আমরা যে বিশ্ব করোনা মহামারিতে আছি, এর প্রায় দেড় বছর পার করছি। এটার বেলায়ও লক্ষ করছি, মানুষের সচেতনতাই প্রধান প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করেছে। সচেতনতাই মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছে বা করছে। থ্যালাসেমিয়ার বিষয়েও সচেতনতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নেই। আর এই সচেতনতা কিভাবে তৈরি করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে নানাভাবে আরো বেশি যুক্ত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের অনেক মিডিয়া রয়েছে। এ জায়গাগুলোতে যদি আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে বোঝাতে পারি এটা কিভাবে আপনাকে রক্ষা করবে, তাহলে যেকোনো রোগের ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সম্ভব। কারণ আমি মনে করি কোনো রোগ হওয়ার আগে যদি সচেতন হওয়া যায় এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। তাই বলব, সচেতনতা অতি জরুরি। আর আমরা মিডিয়ার পক্ষ থেকে সচেতনতা তৈরির কাজটি নিয়মিত সব সময় করে থাকি। বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই তারা এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের বরাবরই যুক্ত করেন।
রোগীর চিকিৎসা সহজ করতে হবে
কাজী হাবিবুল বাশার
 এমন অসুখ খুব কম আছে, যেটা শতভাগ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখন যাঁরা আক্রান্ত আছেন তাঁদের চিকিৎসাব্যবস্থা কিভাবে আরো সহজ করা যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে। তবে সব পর্যায়ে সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সবার প্রত্যাশা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সবারই সামাজিক দায়িত্ব আছে। আমরা প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে যদি সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে সেটা দ্রুত প্রতিরোধ করা সম্ভব। খেলোয়াড় যাঁরা আছেন তাঁরাও যদি কথা বলেন, তাহলে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।
এমন অসুখ খুব কম আছে, যেটা শতভাগ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখন যাঁরা আক্রান্ত আছেন তাঁদের চিকিৎসাব্যবস্থা কিভাবে আরো সহজ করা যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে। তবে সব পর্যায়ে সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সবার প্রত্যাশা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সবারই সামাজিক দায়িত্ব আছে। আমরা প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে যদি সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে সেটা দ্রুত প্রতিরোধ করা সম্ভব। খেলোয়াড় যাঁরা আছেন তাঁরাও যদি কথা বলেন, তাহলে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।
বিভাগীয় মেডিক্যাল কলেজে থ্যালাসেমিয়া ইউনিট করা হলে এ রোগ কমে যাবে
ডা. মোহাম্মদ শরীফ
 ২০০৮ সালের পর থেকে বর্তমান সরকার মা ও শিশু মৃত্যুর হারের দিকে ব্যাপক নজর দিয়েছে। ফলে এখন মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকে কমে এসেছে। স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন এনজিও গুরুত্বসহ কাজ করছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাজে নতুনত্ব নিয়ে আসতে হবে। আমরা স্বাস্থ্যের সঙ্গে পুষ্টি নিয়ে কাজ করছি। এ ছাড়া অটিজম একটি বড় সেক্টর ছিল যে সেক্টরটি নিয়ে কেউ কাজ করেনি। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সে সেক্টরটি নিয়ে চমৎকারভাবে গর্বের সঙ্গে কাজ করছেন। আমি দীর্ঘ সময় ধরে পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজ করছি। আমার মনে হয় সততার সঙ্গে গুরুত্ব সহকারে কাজ করলে সব কিছুই করা সম্ভব। সরকারের এই সেক্টরে এমন একটি অবস্থা এসেছে, এ সেক্টরে বরাদ্দে যে টাকা দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু আমরা খরচ করতে পারি না। আমাদের বিভাগীয় পুরনো মেডিক্যাল কলেজগুলো আছে এগুলোতে যদি থ্যালাসেমিয়ার জন্য আলাদা ইউনিট খোলা যায় তাহলে এ রোগগুলো অনেক কমে যাবে বলে মনে করি। তাই আমার পক্ষ থেকে বলার হলো বিয়ের আগে দুজনেরই ব্লাড টেস্টসহ থ্যালাসেমিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
২০০৮ সালের পর থেকে বর্তমান সরকার মা ও শিশু মৃত্যুর হারের দিকে ব্যাপক নজর দিয়েছে। ফলে এখন মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকে কমে এসেছে। স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন এনজিও গুরুত্বসহ কাজ করছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কাজে নতুনত্ব নিয়ে আসতে হবে। আমরা স্বাস্থ্যের সঙ্গে পুষ্টি নিয়ে কাজ করছি। এ ছাড়া অটিজম একটি বড় সেক্টর ছিল যে সেক্টরটি নিয়ে কেউ কাজ করেনি। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সে সেক্টরটি নিয়ে চমৎকারভাবে গর্বের সঙ্গে কাজ করছেন। আমি দীর্ঘ সময় ধরে পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজ করছি। আমার মনে হয় সততার সঙ্গে গুরুত্ব সহকারে কাজ করলে সব কিছুই করা সম্ভব। সরকারের এই সেক্টরে এমন একটি অবস্থা এসেছে, এ সেক্টরে বরাদ্দে যে টাকা দেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু আমরা খরচ করতে পারি না। আমাদের বিভাগীয় পুরনো মেডিক্যাল কলেজগুলো আছে এগুলোতে যদি থ্যালাসেমিয়ার জন্য আলাদা ইউনিট খোলা যায় তাহলে এ রোগগুলো অনেক কমে যাবে বলে মনে করি। তাই আমার পক্ষ থেকে বলার হলো বিয়ের আগে দুজনেরই ব্লাড টেস্টসহ থ্যালাসেমিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
রোগীর প্রতি সমাজের সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে
ফারহিন ইসলাম
 আমার মা-বাবা দুজনই ডাক্তার। এর পরও আমার যেদিন থেকে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়েছে সেদিন থেকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পারিবারিক সহযোগিতার পাশাপাশি একটু সামাজিক সাপোর্ট প্রয়োজন। এর মানে আর্থিক কোনো সাপোর্ট নয়। একজন রোগী হিসেবে আমি মনে করি আক্রান্ত রোগীদের একটি কার্ড থাকা প্রয়োজন। তাহলে হাসপাতালে গেলে রক্ত ও ওষুধ পাওয়ার মতো সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া ডাক্তার কিংবা মা-বাবার ধারণা থাকে আক্রান্ত রোগী বেশিদিন বাঁচবে না। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি এখনো বেঁচে আছ?’ এমনকি স্কুলে ভর্তির সময় এই রোগের কথা আমাকে লুকাতে হয়েছে। আমি চাই এগুলো পরিবর্তন হোক। এ জন্য প্রতিরোধে যেমন সচেতনতা প্রয়োজন, তেমনি সমাজের আচরণ ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া রোগের একমাত্র কারণ বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে। এ জন্য বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি। আর যদি বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে হয়েও যায়, আগত সন্তান যেন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত না হয় এ জন্য ভ্রূণ পরীক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগী আছে।
আমার মা-বাবা দুজনই ডাক্তার। এর পরও আমার যেদিন থেকে থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়েছে সেদিন থেকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পারিবারিক সহযোগিতার পাশাপাশি একটু সামাজিক সাপোর্ট প্রয়োজন। এর মানে আর্থিক কোনো সাপোর্ট নয়। একজন রোগী হিসেবে আমি মনে করি আক্রান্ত রোগীদের একটি কার্ড থাকা প্রয়োজন। তাহলে হাসপাতালে গেলে রক্ত ও ওষুধ পাওয়ার মতো সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া ডাক্তার কিংবা মা-বাবার ধারণা থাকে আক্রান্ত রোগী বেশিদিন বাঁচবে না। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি এখনো বেঁচে আছ?’ এমনকি স্কুলে ভর্তির সময় এই রোগের কথা আমাকে লুকাতে হয়েছে। আমি চাই এগুলো পরিবর্তন হোক। এ জন্য প্রতিরোধে যেমন সচেতনতা প্রয়োজন, তেমনি সমাজের আচরণ ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া রোগের একমাত্র কারণ বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে। এ জন্য বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি। আর যদি বাহকের সঙ্গে বাহকের বিয়ে হয়েও যায়, আগত সন্তান যেন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত না হয় এ জন্য ভ্রূণ পরীক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ হাজার থ্যালাসেমিয়া রোগী আছে।
বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা জরুরি
অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ
 থ্যালাসেমিয়া এমন একটি রোগ, যা রক্তশূন্যতা তৈরি করে। দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়ার মধ্যে মেজর যেটা সেটা বেশি জটিল, মাইনরটা তেমন জটিল নয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ব্যক্তি বেশি দুর্বল থাকে, সেটা অনেকে প্রথম দিকে বুঝতে পারে না। প্রস্রাবও ডার্ক হয়, শরীরের গ্রোথও দেরিতে হয়। এ ছাড়া মুখের হাড়গুলো একটু ব্যতিক্রম হয়। এ লক্ষণগুলো যদি দেখা যায়, তাহলে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময় রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে থ্যালাসেমিয়ার থ্রেডটা আছে কি না। যদি মা-বাবার থ্যালাসেমিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু জন্মের পরই সন্তানের হয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ট্রিটমেন্টের চেয়ে জরুরি হলো বেশি আয়রন যাতে না হয়। ব্লাড ট্রান্সমিশন একমাত্র চিকিৎসা। রোগীর রক্তের সরবরাহ কমে যায়, তাই রক্ত তাকে দিতে হয়। আর এসব সচেতনতার জন্য মিডিয়ার একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। আর ‘বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন’—এ কথা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি, এখনো কিন্তু এটা হয়নি। আমাদের হিমোগ্লোবিন থ্রেড, থ্যালাসেমিয়া, এইডস, হেপাটাইটিস-বি আছে কি না এগুলো বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে জানা জরুরি। অন্যথায় সন্তানের মাধ্যমে ছড়াবে। তাই বিয়ের আগে দুজনেরই রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। সম্প্রতি একটি ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে স্টেমসেল ট্রান্সপ্লান্ট। এটা করলে থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বড় কথা আমরা সচেতন হব। রক্তশূন্যতা আছে কি না এবং কী কারণে হলো পরীক্ষা করব। এ ছাড়া থ্যালাসেমিয়া রোগীর যদি রক্ত লাগে তার জন্য রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আমাদের মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।
থ্যালাসেমিয়া এমন একটি রোগ, যা রক্তশূন্যতা তৈরি করে। দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়ার মধ্যে মেজর যেটা সেটা বেশি জটিল, মাইনরটা তেমন জটিল নয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ব্যক্তি বেশি দুর্বল থাকে, সেটা অনেকে প্রথম দিকে বুঝতে পারে না। প্রস্রাবও ডার্ক হয়, শরীরের গ্রোথও দেরিতে হয়। এ ছাড়া মুখের হাড়গুলো একটু ব্যতিক্রম হয়। এ লক্ষণগুলো যদি দেখা যায়, তাহলে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময় রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে থ্যালাসেমিয়ার থ্রেডটা আছে কি না। যদি মা-বাবার থ্যালাসেমিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু জন্মের পরই সন্তানের হয়। থ্যালাসেমিয়া হলে ট্রিটমেন্টের চেয়ে জরুরি হলো বেশি আয়রন যাতে না হয়। ব্লাড ট্রান্সমিশন একমাত্র চিকিৎসা। রোগীর রক্তের সরবরাহ কমে যায়, তাই রক্ত তাকে দিতে হয়। আর এসব সচেতনতার জন্য মিডিয়ার একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। আর ‘বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিন’—এ কথা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি, এখনো কিন্তু এটা হয়নি। আমাদের হিমোগ্লোবিন থ্রেড, থ্যালাসেমিয়া, এইডস, হেপাটাইটিস-বি আছে কি না এগুলো বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে জানা জরুরি। অন্যথায় সন্তানের মাধ্যমে ছড়াবে। তাই বিয়ের আগে দুজনেরই রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। সম্প্রতি একটি ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে স্টেমসেল ট্রান্সপ্লান্ট। এটা করলে থ্যালাসেমিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বড় কথা আমরা সচেতন হব। রক্তশূন্যতা আছে কি না এবং কী কারণে হলো পরীক্ষা করব। এ ছাড়া থ্যালাসেমিয়া রোগীর যদি রক্ত লাগে তার জন্য রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আমাদের মেডিক্যালের ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।
থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য
প্রফেসর ডা. আবু জাফর মো. সালেহ
 থ্যালাসেমিয়া রোগ জায়গাভেদে ভিন্ন রকম হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এক রকম, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আবার অন্য রকম। আমাদের দেশে ৭ থেকে ১০ শতাংশ মানুষের বিভিন্ন ধরনের হিমোগ্লোবিন অ্যাবনরমালিটিস আছে। এই চিকিৎসার জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন। একটি হলো প্রতিরোধ। আরেকটি হলো চিকিৎসাসেবা দেওয়া। থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে আমরা তেমন কোনো সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে পারিনি। প্রতিরোধের জন্য ধাপে ধাপে চারটি পর্যায় আছে। ব্যক্তিসচেতনতা ও শিক্ষা, রোগের বাহককে চিহ্নিত করা, রোগীকে কাউন্সেলিং করা এবং বাহক যারা আছে তাদের আগত সন্তানদের কিভাবে রোগ থেকে মুক্ত করা যায়। এর চিকিৎসা দুই ধরনের হয়। একটি হলো রোগ থেকে সুস্থতা নিশ্চিত করা (বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট), অন্যটি হলো সাপোর্টিভ। পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য আলাদা হাসপাতাল ও ওষুধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এসব ওষুধের অনুমোদন না থাকায় চোরাই পথে আসে। অনেক সময় আসতে দেওয়া হয় না। এতে রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।
থ্যালাসেমিয়া রোগ জায়গাভেদে ভিন্ন রকম হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এক রকম, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আবার অন্য রকম। আমাদের দেশে ৭ থেকে ১০ শতাংশ মানুষের বিভিন্ন ধরনের হিমোগ্লোবিন অ্যাবনরমালিটিস আছে। এই চিকিৎসার জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন। একটি হলো প্রতিরোধ। আরেকটি হলো চিকিৎসাসেবা দেওয়া। থ্যালাসেমিয়া শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে আমরা তেমন কোনো সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে পারিনি। প্রতিরোধের জন্য ধাপে ধাপে চারটি পর্যায় আছে। ব্যক্তিসচেতনতা ও শিক্ষা, রোগের বাহককে চিহ্নিত করা, রোগীকে কাউন্সেলিং করা এবং বাহক যারা আছে তাদের আগত সন্তানদের কিভাবে রোগ থেকে মুক্ত করা যায়। এর চিকিৎসা দুই ধরনের হয়। একটি হলো রোগ থেকে সুস্থতা নিশ্চিত করা (বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট), অন্যটি হলো সাপোর্টিভ। পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য আলাদা হাসপাতাল ও ওষুধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এসব ওষুধের অনুমোদন না থাকায় চোরাই পথে আসে। অনেক সময় আসতে দেওয়া হয় না। এতে রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।
সচেতনতা-জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব
ড. ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার
 যারা প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করে তাদের এ রোগ সম্পর্কে জানাতে ও বোঝাতে হবে। বংশপরম্পরায় এই রোগ হয় এবং তাদের সচেতনতার জায়গা সৃষ্টি করতে হবে। এই রোগ এমন কোনো বিষয় না যে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে, বরং তাদের আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুব সীমিত। আর ধনী-গরিব বলে নয়, সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি মিডিয়া যার যার ক্ষেত্র থেকে সর্বাত্মক এগিয়ে আসতে হবে। তবেই জনসম্পৃক্ততা তৈরি হবে। কোথায় গেলে টেস্ট করা যাবে, পরে ট্রান্সমিশনের জায়গা থেকে কোথায় গেলে করতে পারবে, ওভারডোজ হয়ে গেলে ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন—এই তথ্যগুলো তাদের পরিষ্কার করতে হবে। কোথায় গেলে সেবা পাবে ও টেস্ট করার বিষয়টি সহজ করে দিতে হবে। জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব।
যারা প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করে তাদের এ রোগ সম্পর্কে জানাতে ও বোঝাতে হবে। বংশপরম্পরায় এই রোগ হয় এবং তাদের সচেতনতার জায়গা সৃষ্টি করতে হবে। এই রোগ এমন কোনো বিষয় না যে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে, বরং তাদের আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুব সীমিত। আর ধনী-গরিব বলে নয়, সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি মিডিয়া যার যার ক্ষেত্র থেকে সর্বাত্মক এগিয়ে আসতে হবে। তবেই জনসম্পৃক্ততা তৈরি হবে। কোথায় গেলে টেস্ট করা যাবে, পরে ট্রান্সমিশনের জায়গা থেকে কোথায় গেলে করতে পারবে, ওভারডোজ হয়ে গেলে ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন—এই তথ্যগুলো তাদের পরিষ্কার করতে হবে। কোথায় গেলে সেবা পাবে ও টেস্ট করার বিষয়টি সহজ করে দিতে হবে। জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্ভব।
থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই করতে হবে
তৌফিক মারুফ
 সম্মিলিতভাবে থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এটি একক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লড়াই নয়। সবাইকে একসঙ্গে, একযোগে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যেতে হবে। তবেই এই রোগ প্রতিরোধ তথা মুক্ত করা সম্ভব। তাই সরকারি, ব্যক্তিগত, সামাজিক গণমাধ্যম—সব দিক থেকে এই সচেতনতা তৈরিতে কাজ করতে হবে। তবেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো সর্বস্তরের সচেতনতা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে পরীক্ষা করা। পরীক্ষিত মা-বাবা পারেন সুরক্ষিত সন্তান নিশ্চিত করতে।
সম্মিলিতভাবে থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এটি একক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লড়াই নয়। সবাইকে একসঙ্গে, একযোগে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যেতে হবে। তবেই এই রোগ প্রতিরোধ তথা মুক্ত করা সম্ভব। তাই সরকারি, ব্যক্তিগত, সামাজিক গণমাধ্যম—সব দিক থেকে এই সচেতনতা তৈরিতে কাজ করতে হবে। তবেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো সর্বস্তরের সচেতনতা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে পরীক্ষা করা। পরীক্ষিত মা-বাবা পারেন সুরক্ষিত সন্তান নিশ্চিত করতে।
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধযোগ্য
আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
 প্রতিবছর কত সংখ্যক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু জন্ম নিচ্ছে সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। কারণ আগে থেকেই যদি চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে প্রতিরোধ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিরোধযোগ্য। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাদের গ্রোথ থেমে যায়। কিছুদিন পর পর রক্ত দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে সপ্তাহে দুই-তিনবার রক্ত দিতে হয়। একসময় অভিভাবকদের এই সক্ষমতাও থাকে না। আক্রান্ত বাচ্চাদের এবং তাদের বাবা-মায়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। থ্যালাসেমিয়ার বাচ্চারা যখন আসে চিকিৎসা নিতে দেখা যায় তার প্লিহা অনেক বড় হয়ে যায়। সেটার জন্য ঠিকমতো হাঁটতেও পারে না। ওজন কমে যায়। আবার অনেকে প্রেগন্যান্সির সময় বলেন, আমার কিছু হলে বাচ্চাটাকে দেখবেন। কারণ মায়ের থেকেও বাচ্চার এই রোগ হতে পারে। পরে দেখা যায় মা মারা গেছেন। সব মিলিয়ে খুবই কষ্টদায়ক এসব দৃশ্য। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন সেটা আমরা করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি।
প্রতিবছর কত সংখ্যক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু জন্ম নিচ্ছে সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। কারণ আগে থেকেই যদি চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে প্রতিরোধ করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিরোধযোগ্য। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাদের গ্রোথ থেমে যায়। কিছুদিন পর পর রক্ত দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে সপ্তাহে দুই-তিনবার রক্ত দিতে হয়। একসময় অভিভাবকদের এই সক্ষমতাও থাকে না। আক্রান্ত বাচ্চাদের এবং তাদের বাবা-মায়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। থ্যালাসেমিয়ার বাচ্চারা যখন আসে চিকিৎসা নিতে দেখা যায় তার প্লিহা অনেক বড় হয়ে যায়। সেটার জন্য ঠিকমতো হাঁটতেও পারে না। ওজন কমে যায়। আবার অনেকে প্রেগন্যান্সির সময় বলেন, আমার কিছু হলে বাচ্চাটাকে দেখবেন। কারণ মায়ের থেকেও বাচ্চার এই রোগ হতে পারে। পরে দেখা যায় মা মারা গেছেন। সব মিলিয়ে খুবই কষ্টদায়ক এসব দৃশ্য। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন সেটা আমরা করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি।
সরকারিভাবে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের পরিচয়পত্র থাকা উচিত
অধ্যাপক ডা. মাসুমা রহমান
 বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন ২০০২ সাল থেকে রোগীদের জন্য কাজ করছে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, একটা সময় ছিল যখন থ্যালাসেমিয়া হতো তখন মা-বাবা দুজনেই হতাশ হয়ে যেতেন। পরে এই রোগীগুলোকে দেখা যেত দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো রক্তের জন্য, আবার কখনো ওষুধের জন্য। বেশির ভাগই দেখা যেত ২০ বছর পার করতে পারত না। এখন আমাদের সরকারি পর্যায়ে কিছুটা সচেতনতা এসেছে এবং কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে এটা নিয়ে কাজ করতে। বলা হচ্ছে, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনা মূল্যে রক্ত দান করা হবে। এ ছাড়া আমাদের সবচেয়ে অভাব হলো আমরা নিরাপদ রক্ত নিশ্চিত করতে পারছি না। এই অপ্রতুলতা রয়েই গেছে এখন পর্যন্ত। এ ছাড়া আমাদের ওষুধের সমস্যা আছে। আর বেশির ভাগ হাসপাতাল রাজধানীকেন্দ্রিক। অথচ বিভিন্ন জেলায় আমাদের রোগী রয়েছে, তারা ঢাকায় এসে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি যায়। যদি সরকারি পর্যায়ে কমপক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে থ্যালাসেমিয়া সেন্টার করা যায় তাহলে রোগীগুলোর কষ্ট কম হবে এবং তারা বেঁচে যাবে। অন্যদিকে আমরা বলছি ৭ শতাংশ বা ১০ শতাংশ থ্যালাসেমিয়া ধারক বা বাহক, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জানি না আমাদের দেশে কত শতাংশ থ্যালাসেমিয়া রোগী বা বাহক আছে। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সরকারিভাবে একটি পরিচয়পত্র থাকা উচিত। এ রোগীগুলো যদি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে যায় তারা যেন একটু সুযোগ-সুবিধা পায়। আর থ্যালাসেমিয়া একটি ইউনিক রোগ। এ রোগের জন্য মা-বাবা দায়ী। তাই আমরা মা-বাবা যারা আছি তাদের অসচেতনতার জন্যই পরে আমাদের বাচ্চারা থ্যালাসেমিয়া রোগী হয়। তাই বিয়ের আগে একটা ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে সচেতন হতে পারি।
বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন ২০০২ সাল থেকে রোগীদের জন্য কাজ করছে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, একটা সময় ছিল যখন থ্যালাসেমিয়া হতো তখন মা-বাবা দুজনেই হতাশ হয়ে যেতেন। পরে এই রোগীগুলোকে দেখা যেত দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো রক্তের জন্য, আবার কখনো ওষুধের জন্য। বেশির ভাগই দেখা যেত ২০ বছর পার করতে পারত না। এখন আমাদের সরকারি পর্যায়ে কিছুটা সচেতনতা এসেছে এবং কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে এটা নিয়ে কাজ করতে। বলা হচ্ছে, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনা মূল্যে রক্ত দান করা হবে। এ ছাড়া আমাদের সবচেয়ে অভাব হলো আমরা নিরাপদ রক্ত নিশ্চিত করতে পারছি না। এই অপ্রতুলতা রয়েই গেছে এখন পর্যন্ত। এ ছাড়া আমাদের ওষুধের সমস্যা আছে। আর বেশির ভাগ হাসপাতাল রাজধানীকেন্দ্রিক। অথচ বিভিন্ন জেলায় আমাদের রোগী রয়েছে, তারা ঢাকায় এসে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি যায়। যদি সরকারি পর্যায়ে কমপক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে থ্যালাসেমিয়া সেন্টার করা যায় তাহলে রোগীগুলোর কষ্ট কম হবে এবং তারা বেঁচে যাবে। অন্যদিকে আমরা বলছি ৭ শতাংশ বা ১০ শতাংশ থ্যালাসেমিয়া ধারক বা বাহক, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জানি না আমাদের দেশে কত শতাংশ থ্যালাসেমিয়া রোগী বা বাহক আছে। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সরকারিভাবে একটি পরিচয়পত্র থাকা উচিত। এ রোগীগুলো যদি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে যায় তারা যেন একটু সুযোগ-সুবিধা পায়। আর থ্যালাসেমিয়া একটি ইউনিক রোগ। এ রোগের জন্য মা-বাবা দায়ী। তাই আমরা মা-বাবা যারা আছি তাদের অসচেতনতার জন্যই পরে আমাদের বাচ্চারা থ্যালাসেমিয়া রোগী হয়। তাই বিয়ের আগে একটা ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে সচেতন হতে পারি।
দেশে ৫০ লাখের বেশি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার জিন বহন করছে
খালেদা আক্তার সিনথিয়া
 বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা, থ্যালাসেমিয়া থেকে সন্তান সুরক্ষা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে সহজ একটি রক্ত পরীক্ষা (হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস) করা। ছোট একটা পরীক্ষাই পারে একটি পরিবার ও শিশুর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। রক্তস্বল্পতাজনিত মারাত্মক এই বংশগত রোগটি প্রধানত দুই প্রকার—আলফা থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া। বিশ্বে বিটা থ্যালাসেমিয়ার চেয়ে আলফা থ্যালাসেমিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলফা থ্যালাসেমিয়া তীব্র হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করে।
বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা, থ্যালাসেমিয়া থেকে সন্তান সুরক্ষা। থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বিয়ের আগে সহজ একটি রক্ত পরীক্ষা (হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস) করা। ছোট একটা পরীক্ষাই পারে একটি পরিবার ও শিশুর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। রক্তস্বল্পতাজনিত মারাত্মক এই বংশগত রোগটি প্রধানত দুই প্রকার—আলফা থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া। বিশ্বে বিটা থ্যালাসেমিয়ার চেয়ে আলফা থ্যালাসেমিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলফা থ্যালাসেমিয়া তীব্র হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করে।
বিটা থ্যালাসেমিয়া দুই রকমের হতে পারে। একটি বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর। এদের থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট বা ক্যারিয়ার বলে (এরা মূলত রোগটির বাহক)। অপরটি থ্যালাসেমিয়া মেজর। থ্যালাসেমিয়া কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। বাবা-মা উভয়ে থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট হলে ভূমিষ্ঠ শিশুর শতকরা ২৫ ভাগ থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আবার বাবা-মার মধ্যে একজন যদি সুস্থ থাকে সে ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুর থ্যালাসেমিয়া হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না, তবে থ্যালাসেমিয়া বাহক হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
থ্যালাসেমিয়া মাইনরে সাধারণত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। থ্যালাসেমিয়া মেজরে নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনই প্রধান চিকিৎসা। রোগীকে ঘন ঘন রক্ত দিতে হয় বলে শরীরে আয়রনের মাত্রা বাড়তে থাকে। আয়রন চিলেটর (ডেফিরক্স) এর মাধ্যমে তা কমাতে হয়। অতিরিক্ত আয়রন জমা হয় হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে, অগ্ন্যাশয়ে, যার কারণে অঙ্গগুলো বিকল হতে শুরু করে। এ রকম পরিস্থিতিতে সঠিক চিকিৎসা না পেলে রোগী মারা যেতে পারে।
সম্পর্কিত খবর
লজ্জা নয়, প্রয়োজন সচেতনতা

নারীর স্বাস্থ্য সমস্যার একটি এন্ডোমেট্রিওসিস। রোগটি যেহেতু পিরিয়ড বা মাসিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই বেশির ভাগ নারী লজ্জা বা ভয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না। এতে রোগটি শনাক্ত হতে একদিকে দেরি হচ্ছে, অন্যদিকে বন্ধ্যাত্ব রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লজ্জা নয়, প্রয়োজন জনসচেতনতা।
লক্ষণ বুঝে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে
অধ্যাপক সামিনা চৌধুরী
 পিরিয়ড বা মাসিকের সময় নারীদের তলপেটে তীব্র ব্যথা হয়। এ সময় অনেক কিশোরী স্কুলে যেতে পারে না, কাজ করতে পারে না, বারবার টয়লেটে যায়।
পিরিয়ড বা মাসিকের সময় নারীদের তলপেটে তীব্র ব্যথা হয়। এ সময় অনেক কিশোরী স্কুলে যেতে পারে না, কাজ করতে পারে না, বারবার টয়লেটে যায়।
পৃথিবীব্যাপী দুই শ মিলিয়ন কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্ক নারী এন্ডোমেট্রিওসিস রোগে ভুগছে।
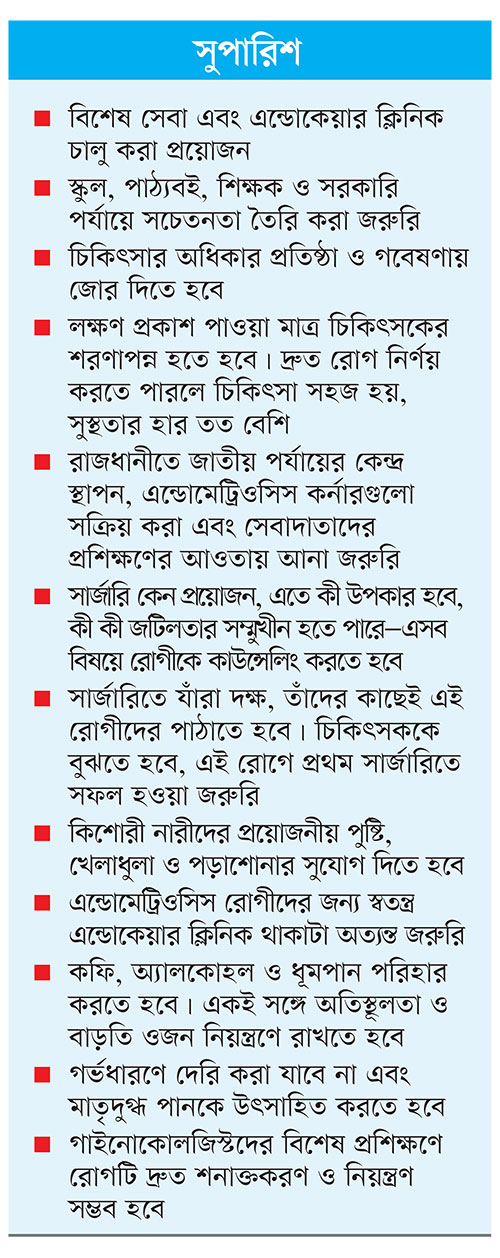 নারীর ক্ষমতায়ন, এন্ডোমেট্রিওসিস যত্নে
নারীর ক্ষমতায়ন, এন্ডোমেট্রিওসিস যত্নে
বাধা দূর করুন
অধ্যাপক সালেহা বেগম চৌধুরী
 এন্ডো-মার্চ সচেতনতার অংশ হিসেবে প্রতিবছর এন্ডোমেট্রিওসিস-অ্যাডেনোমায়োসিস সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ইএএসবি) গোলটেবিল আলোচনাসভার আয়োজন করে থাকে। সারা পৃথিবীতে মার্চ মাস এন্ডো-মার্চ হিসেবে উদযাপিত হয়। এই উদযাপনের উদ্দেশ্য হলো, এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা, তাদের চিকিৎসার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসাব্যবস্থা বিস্তৃত করা।
এন্ডো-মার্চ সচেতনতার অংশ হিসেবে প্রতিবছর এন্ডোমেট্রিওসিস-অ্যাডেনোমায়োসিস সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ইএএসবি) গোলটেবিল আলোচনাসভার আয়োজন করে থাকে। সারা পৃথিবীতে মার্চ মাস এন্ডো-মার্চ হিসেবে উদযাপিত হয়। এই উদযাপনের উদ্দেশ্য হলো, এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা, তাদের চিকিৎসার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসাব্যবস্থা বিস্তৃত করা।
এন্ডোমেট্রিওসিস সচেতনতার মাসকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর আমাদের একটা স্লোগান থাকে, আমরা একটা থিম ঠিক করি। এটি পরে স্লোগান হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে থাকি। একই সঙ্গে আমরা আমাদের কাজগুলো এগিয়ে নিতে থাকি। এবারের স্লোগান, ‘নারীর ক্ষমতায়ন : এন্ডোমেট্রিওসিস যত্নে বাধা দূর করুন’।
আবার আমরা নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গকে এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসার এবং এর অগ্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা, এন্ডোমেট্রিওসিস বিষয়ে তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করা, তাদের চিকিৎসার অধিকারকে উপলব্ধি করা এবং গবেষণার মাধ্যমে এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণগুলো বের করে আরো অগ্রসর হওয়া।
সেবাদাতাকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা জরুরি
অধ্যাপক ফারহানা দেওয়ান
 এন্ডোমেট্রিওসিস রোগটি নিয়ে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। শুধু দিবসকেন্দ্রিক নয়, সারা বছর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। রাজধানীতে জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্র স্থাপন, সেখান থেকে একসঙ্গে সারা দেশে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। প্রেজেন্টেশন, লিফলেট বিতরণ বা ওয়েবিনারের মাধ্যমেও একযোগে এই সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে। এতে আরেকটি সুবিধা হলো, সবাই জানতে পারবে কোথায় গেলে তারা সঠিক সেবা পাবে।
এন্ডোমেট্রিওসিস রোগটি নিয়ে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। শুধু দিবসকেন্দ্রিক নয়, সারা বছর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। রাজধানীতে জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্র স্থাপন, সেখান থেকে একসঙ্গে সারা দেশে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। প্রেজেন্টেশন, লিফলেট বিতরণ বা ওয়েবিনারের মাধ্যমেও একযোগে এই সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে। এতে আরেকটি সুবিধা হলো, সবাই জানতে পারবে কোথায় গেলে তারা সঠিক সেবা পাবে।
আমাদের এন্ডোমেট্রিওসিস কর্নারগুলো সক্রিয় করতে হবে, সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা জরুরি। এ ক্ষেত্রে লালকুটি সেন্টারকে আমরা প্রশিক্ষণের জন্য কাজে লাগাতে পারি। একই সঙ্গে কারিকুলামে রোগটি সম্পর্কে নতুন সংযোজন প্রয়োজন। তাহলেই সচেতনতার কাজটি সহজ হবে।
ওজিএসবির তিন হাজারের বেশি সদস্য আছেন, যাঁরা সারা দেশে ১৯টি শাখায় কাজ করেন। প্রতিটি ব্রাঞ্চে একজন প্রধান রয়েছেন, ফলে কোনো কার্যক্রম পরিচালনায় আমাদের বেগ পেতে হয় না। সারা দেশে আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন। তাঁদের কিভাবে সচেতন করা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
অপারেশনের পর মেডিক্যাল চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যাপক গুলশান আরা
 কিশোরী বা প্রাপ্তবয়স্ত নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হলো মেডিক্যাল চিকিৎসা। এই রোগটিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ব্যথানাশক নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগস বা এনএসআইডি। এটি একটি নিরাপদ ওষুধ, তবে বারবার খেতে হয়। এটি আবার অনেকের কাছে বড় সমস্যা। প্রায় সময়ই ডোজ মিস হয়ে যায়। তারপর যখন গুরুতর এন্ডোমেট্রিওসিস হয়, তখন এনএসআইডি কাজ করে না। তখন অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এর ক্ষতিকর দিক হলো, এসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। ফলে এর জন্য আলাদা ওষুধ খেতে হয়। কিশোরী নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের অপারেশনের পর মেডিক্যাল চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় রোগী চিকিৎসা না পেলে রোগটির পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এতে কিশোরী নারীদের ইনফার্টিলিটি বেড়ে যায়। এই সময়ে ফলোআপ চিকিৎসা নিলে সুস্থতা নিশ্চিত করা যাবে।
কিশোরী বা প্রাপ্তবয়স্ত নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি হলো মেডিক্যাল চিকিৎসা। এই রোগটিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ব্যথানাশক নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগস বা এনএসআইডি। এটি একটি নিরাপদ ওষুধ, তবে বারবার খেতে হয়। এটি আবার অনেকের কাছে বড় সমস্যা। প্রায় সময়ই ডোজ মিস হয়ে যায়। তারপর যখন গুরুতর এন্ডোমেট্রিওসিস হয়, তখন এনএসআইডি কাজ করে না। তখন অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এর ক্ষতিকর দিক হলো, এসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। ফলে এর জন্য আলাদা ওষুধ খেতে হয়। কিশোরী নারীদের এন্ডোমেট্রিওসিসের অপারেশনের পর মেডিক্যাল চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় রোগী চিকিৎসা না পেলে রোগটির পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা বেশি। এতে কিশোরী নারীদের ইনফার্টিলিটি বেড়ে যায়। এই সময়ে ফলোআপ চিকিৎসা নিলে সুস্থতা নিশ্চিত করা যাবে।
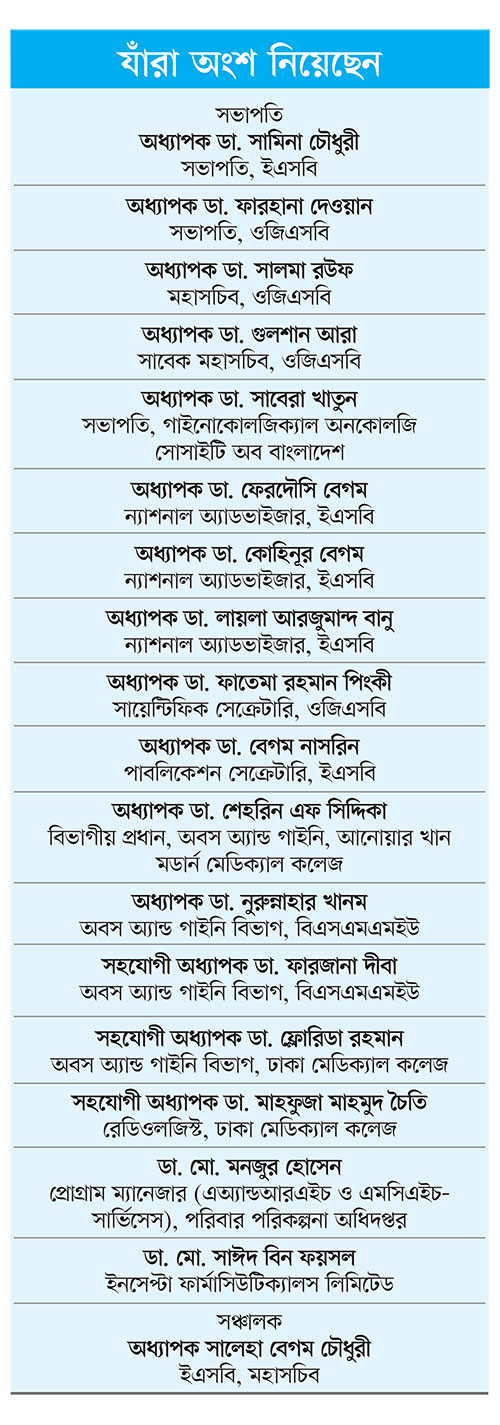 যথাতথা অপারেশন রোগীর ক্ষতির কারণ
যথাতথা অপারেশন রোগীর ক্ষতির কারণ
অধ্যাপক সালমা রউফ
 এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসায় সার্জারি হলো চিকিৎসার শেষ ধাপ। যখন একজন গাইনোকোলজিস্ট সার্জারির দিকে যাবেন, তখন চিন্তা করতে হবে সার্জারি রোগীর জন্য কতটা জরুরি। এক. সার্জারি করার ফলে রোগীর উন্নতি কী হবে বা তার ফার্টিলিটি ইমপ্রুভমেন্ট হবে কি না। দুই. সার্জারির কারণে রোগীর কী কী সমস্যা হতে পারে। কারণ এতে রোগীর ডিম্বাণুর রিজার্ভ কমে গিয়ে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তিন. অস্ত্রোপচারের জটিলতা রোগীর জন্য সহনশীল কি না। এ ক্ষেত্রে সার্জারির আগে সাধারণ পরীক্ষাগুলো করে জানতে হবে কোন ধরনের এন্ডোমেট্রিওসিস; যেমন—খাদ্যনালি, মূত্রথলি বা আশপাশের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। চার. সার্জারি করার জন্য সার্জনের দক্ষতা কতখানি।
এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসায় সার্জারি হলো চিকিৎসার শেষ ধাপ। যখন একজন গাইনোকোলজিস্ট সার্জারির দিকে যাবেন, তখন চিন্তা করতে হবে সার্জারি রোগীর জন্য কতটা জরুরি। এক. সার্জারি করার ফলে রোগীর উন্নতি কী হবে বা তার ফার্টিলিটি ইমপ্রুভমেন্ট হবে কি না। দুই. সার্জারির কারণে রোগীর কী কী সমস্যা হতে পারে। কারণ এতে রোগীর ডিম্বাণুর রিজার্ভ কমে গিয়ে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তিন. অস্ত্রোপচারের জটিলতা রোগীর জন্য সহনশীল কি না। এ ক্ষেত্রে সার্জারির আগে সাধারণ পরীক্ষাগুলো করে জানতে হবে কোন ধরনের এন্ডোমেট্রিওসিস; যেমন—খাদ্যনালি, মূত্রথলি বা আশপাশের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। চার. সার্জারি করার জন্য সার্জনের দক্ষতা কতখানি।
চিকিৎসার বাইরে থাকলে বাড়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি
অধ্যাপক সাবেরা খাতুন
 শারীরিক পরিশ্রম, শরীরচর্চা, চর্বিজাতীয় খাবার কম খাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে হবে। নারীদের ঋতুস্রাবের সময় খুব বেশি ব্যথা হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসা যত দ্রুত শুরু করা যায়, সুস্থতার সম্ভাবনা তত বেশি। গবেষণায় এন্ডোমেট্রিওসিসের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক বেরিয়ে এসেছে। জরায়ুমুখের ক্যান্সারে নির্দিষ্ট কারণ জানা গেলেও এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণ জানা যায়নি। যদিও ক্যান্সারের সঙ্গে এই রোগের কিছু মিল পাওয়া গেছে; যেমন—দুটি রোগই শরীরের যেকোনো জায়গায় হতে পারে। অন্যটি হলো চকোলেট সিস্ট। এ ক্ষেত্রে ক্যান্সার নয়—রোগীকে এমন আশ্বাস দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আলট্রাগ্রাফি বা টিভিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নির্ণয় করতে হয়।
শারীরিক পরিশ্রম, শরীরচর্চা, চর্বিজাতীয় খাবার কম খাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে হবে। নারীদের ঋতুস্রাবের সময় খুব বেশি ব্যথা হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, এন্ডোমেট্রিওসিস চিকিৎসা যত দ্রুত শুরু করা যায়, সুস্থতার সম্ভাবনা তত বেশি। গবেষণায় এন্ডোমেট্রিওসিসের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক বেরিয়ে এসেছে। জরায়ুমুখের ক্যান্সারে নির্দিষ্ট কারণ জানা গেলেও এন্ডোমেট্রিওসিসের কারণ জানা যায়নি। যদিও ক্যান্সারের সঙ্গে এই রোগের কিছু মিল পাওয়া গেছে; যেমন—দুটি রোগই শরীরের যেকোনো জায়গায় হতে পারে। অন্যটি হলো চকোলেট সিস্ট। এ ক্ষেত্রে ক্যান্সার নয়—রোগীকে এমন আশ্বাস দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আলট্রাগ্রাফি বা টিভিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নির্ণয় করতে হয়।
ক্ষমতায়নের গুণাবলি অর্জনেই জীবন-সমাজ সুন্দর হবে
অধ্যাপক ফেরদৌসি বেগম
 রোগীরা প্রায়ই একটি কথা বলে, ‘ডাক্তাররা বলেছেন, আমার পক্ষে শিশু জন্ম দেওয়া প্রায় অসম্ভব।’ তাদের অতীত থেকে জানা যায়, কিশোরীকাল থেকে তারা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগে অনেক ভুগেছে। ওই সময় যদি তারা মুখ খুলতে পারত তাহলে হয়তো এমন দিন আসত না।
রোগীরা প্রায়ই একটি কথা বলে, ‘ডাক্তাররা বলেছেন, আমার পক্ষে শিশু জন্ম দেওয়া প্রায় অসম্ভব।’ তাদের অতীত থেকে জানা যায়, কিশোরীকাল থেকে তারা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগে অনেক ভুগেছে। ওই সময় যদি তারা মুখ খুলতে পারত তাহলে হয়তো এমন দিন আসত না।
আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতার অর্থ ব্যাপক। ক্ষমতা বলতে আমি তিনটি জিনিস বুঝি। এক. সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন, দুই. পুথিগত বিদ্যার বাইরে সুশিক্ষিত, এবং তিন. সম্পদের অধিকার। কারণ অর্থনৈতিক শক্তিই প্রধান ক্ষমতা। চাকরি বা ব্যবসা যেকোনো অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকতে হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক বা অন্যান্য যে ক্ষমতাই থাকুক, তা নিজে প্রয়োগ করতে পারাই আসল ক্ষমতা।
সচেতনতা শুরু করতে হবে পরিবার থেকে
অধ্যাপক কোহিনূর বেগম
 এন্ডোমেট্রিওসিস শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রোগ নয়, এটি কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে রোগটি শুরু হয় কিশোরী বয়সে, অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সে। তবে রোগটি আরো আগেও শুরু হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের মাসিকের সময় তলপেটে তীব্র ব্যথা, কিন্তু সাধারণ ওষুধে কাজ হচ্ছে না—এই গ্রুপের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত এন্ডোমেট্রিওসিস হতে পারে।
এন্ডোমেট্রিওসিস শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রোগ নয়, এটি কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে রোগটি শুরু হয় কিশোরী বয়সে, অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সে। তবে রোগটি আরো আগেও শুরু হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের মাসিকের সময় তলপেটে তীব্র ব্যথা, কিন্তু সাধারণ ওষুধে কাজ হচ্ছে না—এই গ্রুপের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত এন্ডোমেট্রিওসিস হতে পারে।
রোগটি শনাক্ত করতে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ডায়াগনোসিস একটু দ্রুত হলেও কিশোরী মেয়েরা ডায়াগনোসিসের জন্য অনেক পরে আসে। এর অন্যতম কারণ অসচেতনতা। কারণ বেশির ভাগ মানুষ মনে করে, এটা প্রাপ্তবয়স্কদের হয়। আরেকটা গ্রুপ আছে, যারা লজ্জা বা ভয়ে চিকিৎসকের কাছে যায় না বা তাদের মা-বাবা যেতে দেন না। আরেকটি গ্রুপ আছে, যারা মাসিকের মৃদু ব্যথা ও এন্ডোমেট্রিওসিস ব্যথার পার্থক্য বুঝতে পারে না। এখানে মা-বাবার সচেতনতা জরুরি।
প্রয়োজন ছাড়া সার্জারি নয়
অধ্যাপক লায়লা আরজুমান্দ বানু
 কিশোরী বয়স থেকে এন্ডোমেট্রিওসিসের সূত্রপাত হয়। যখন বাচ্চা মায়ের গর্ভে থাকে, তখনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীর ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সিস্ট হতে পারে। আগে আমরা রোগীদের উপসর্গ দেখে বোঝার চেষ্টা করতাম এন্ডোমেট্রিওসিসের সিস্ট হতে পারে। সিস্ট অনেক রকম হয়। পানি ভরার থলির মতো হলে এটাকে চকোলেট সিস্ট বলি। এখন সিস্টের অনেক ধরনের চিকিৎসা এসেছে। ৫ সেন্টিমিটারের কম সিস্ট হলে ওষুধ খেলেই অনেক সময় তা ভালো হয়ে যাচ্ছে।
কিশোরী বয়স থেকে এন্ডোমেট্রিওসিসের সূত্রপাত হয়। যখন বাচ্চা মায়ের গর্ভে থাকে, তখনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীর ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সিস্ট হতে পারে। আগে আমরা রোগীদের উপসর্গ দেখে বোঝার চেষ্টা করতাম এন্ডোমেট্রিওসিসের সিস্ট হতে পারে। সিস্ট অনেক রকম হয়। পানি ভরার থলির মতো হলে এটাকে চকোলেট সিস্ট বলি। এখন সিস্টের অনেক ধরনের চিকিৎসা এসেছে। ৫ সেন্টিমিটারের কম সিস্ট হলে ওষুধ খেলেই অনেক সময় তা ভালো হয়ে যাচ্ছে।
অনেক রোগী সিস্ট সার্জারিতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে রোগী চাইলেই হবে না, চিকিৎসককে বুঝতে হবে সার্জারি করলে রোগীর ভালো হবে না ক্ষতি হবে।
এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি
অধ্যাপক ফাতেমা রহমান পিংকী
 আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় চিকিৎসকের স্বল্পতা আছে। বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা আরো বেশি। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সারাক্ষণ রোগীর ভিড় লেগে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পক্ষে রোগীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, রোগ নির্ণয়, রোগীর ইতিহাস জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা পেতে যেন রোগীদের ভোগান্তির সম্মুখীন হতে না হয়।
আমাদের দেশে রোগীর তুলনায় চিকিৎসকের স্বল্পতা আছে। বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা আরো বেশি। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সারাক্ষণ রোগীর ভিড় লেগে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পক্ষে রোগীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, রোগ নির্ণয়, রোগীর ইতিহাস জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসা পেতে যেন রোগীদের ভোগান্তির সম্মুখীন হতে না হয়।
সরকারি হাসপাতালে যেসব রোগী মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্ত যাওয়া, বেশি ব্যথা অনুভব হওয়া, স্বামীর সঙ্গে মেলামেশার সময় ব্যথা বা বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ নিয়ে আসে, তাদের যেন এন্ডোকেয়ার ক্লিনিকে পাঠিয়ে দিতে পারি। যাতে তাদের বিভিন্ন কাউন্টারে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা নিতে না হয়।
গর্ভধারণ ও স্তন্যপান রোগ নিরাময়ে সহায়ক
অধ্যাপক বেগম নাসরিন
 এন্ডোমেট্রিওসিস একটি প্রগতিশীল রোগ। এর চারটি ধাপ আছে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের মধ্যে লক্ষণও বাড়তে থাকে। এটা এমন কোনো রোগ নয়, যেটা প্রতিকার করা যায়। এর কোনো টিকাও নেই। যত দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যাবে, তত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে রোগের বিস্তার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
এন্ডোমেট্রিওসিস একটি প্রগতিশীল রোগ। এর চারটি ধাপ আছে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের মধ্যে লক্ষণও বাড়তে থাকে। এটা এমন কোনো রোগ নয়, যেটা প্রতিকার করা যায়। এর কোনো টিকাও নেই। যত দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যাবে, তত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে রোগের বিস্তার থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
অতিস্থূলতা ও বাড়তি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কফি, অ্যালকোহল ও ধূমপান যারা বেশি করে তাদের এই সমস্যা বেশি। এসব অভ্যাস বাদ দিতে হবে। গরুর মাংস ও চর্বিজাতীয় খাবার পরিত্যাগসহ কিছু খাবার বেছে চলতে হবে।
স্কুল থেকে সচেতনতা বাড়াতে হবে
অধ্যাপক শেহরিন এফ সিদ্দিকা
 এন্ডোমেট্রিওসিস মারণব্যাধি না হলেও তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এন্ডোমেট্রিওসিস মানেই হলো ব্যথা, ব্যথা এবং ব্যথা। চলাফেরায় ব্যথা, মাসিকের ব্যথা, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ব্যথা, স্বামীর সহবাসের সময় ব্যথা। একটা সময় এ রকম হয় যে ব্যথা নিয়েই তার জীবন চলছে। আমরা যদি এর ব্যাপকতা দেখি, বেশির ভাগ রোগীর ডায়াগনোসিস হয় অন্তত সাত বছর পর। তখন দেখা যায়, রোগীর অনেক বড় একটা সিস্ট হয়ে গেছে এবং এর ব্যাপকতা হিসেবে কিশোরী মেয়েটির সন্তানসম্ভাবনা হওয়ার সক্ষমতা কমে এসেছে। তার ইনফার্টিলিটি এরই মধ্যে বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মনে হয়, স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও আক্রান্তদের আলাদা করা যেতে পারে।
এন্ডোমেট্রিওসিস মারণব্যাধি না হলেও তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এন্ডোমেট্রিওসিস মানেই হলো ব্যথা, ব্যথা এবং ব্যথা। চলাফেরায় ব্যথা, মাসিকের ব্যথা, প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় ব্যথা, স্বামীর সহবাসের সময় ব্যথা। একটা সময় এ রকম হয় যে ব্যথা নিয়েই তার জীবন চলছে। আমরা যদি এর ব্যাপকতা দেখি, বেশির ভাগ রোগীর ডায়াগনোসিস হয় অন্তত সাত বছর পর। তখন দেখা যায়, রোগীর অনেক বড় একটা সিস্ট হয়ে গেছে এবং এর ব্যাপকতা হিসেবে কিশোরী মেয়েটির সন্তানসম্ভাবনা হওয়ার সক্ষমতা কমে এসেছে। তার ইনফার্টিলিটি এরই মধ্যে বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মনে হয়, স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও আক্রান্তদের আলাদা করা যেতে পারে।
গবেষণায় দেখা যায়, এই রোগে আক্রান্ত ৫০ শতাংশ নারী যথাযথভাবে যৌনজীবনে যেতে পারে না। ৪০ শতাংশ মেয়ে অফিস বা স্কুলে যাওয়ার মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। ৩০ শতাংশ মেয়ের স্কুল ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য স্কুল থেকে সচেতনতা বাড়াতে হবে।
এন্ডোমেট্রিওসিস উইং চিকিৎসাব্যবস্থা সহজ করবে
অধ্যাপক নুরুন্নাহার খানম
 মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস অ্যান্ড গাইনি বিভাগে এন্ডোমেট্রিওসিস উইং চালু করা আমাদের স্বপ্ন। এটি যদি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এন্ডোমেট্রিওসিস অনেক সহজ হয়ে যাবে। এ ছাড়া যদি আমরা এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক করতে চাই তাহলে বহির্বিভাগে সপ্তাহে ছয় দিন চিকিৎসা দিতে হবে। এর জন্য বহির্বিভাগে আলাদা কক্ষ থাকতে হবে, আলাদা সেন্টার হতে হবে। কোনো রোগীর যদি বন্ধ্যাত্বের কারণে ল্যাপারোস্কোপির অথবা মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার হয়, তারপর তারা ইনফার্টিলিটিতে যাবে। যেগুলো বন্ধ্যাত্ব নয়, বিশেষ করে কিশোরী মেয়ে যারা সার্জারি করতে চায় না, তাদের জন্য কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য আলাদা ওয়ার্ড রাখতে হবে। আলাদা চিকিৎসক দরকার। গাইনোকোলজিস্টদের বেশি বেশি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস অ্যান্ড গাইনি বিভাগে এন্ডোমেট্রিওসিস উইং চালু করা আমাদের স্বপ্ন। এটি যদি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে এন্ডোমেট্রিওসিস অনেক সহজ হয়ে যাবে। এ ছাড়া যদি আমরা এন্ডোকেয়ার ক্লিনিক করতে চাই তাহলে বহির্বিভাগে সপ্তাহে ছয় দিন চিকিৎসা দিতে হবে। এর জন্য বহির্বিভাগে আলাদা কক্ষ থাকতে হবে, আলাদা সেন্টার হতে হবে। কোনো রোগীর যদি বন্ধ্যাত্বের কারণে ল্যাপারোস্কোপির অথবা মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার হয়, তারপর তারা ইনফার্টিলিটিতে যাবে। যেগুলো বন্ধ্যাত্ব নয়, বিশেষ করে কিশোরী মেয়ে যারা সার্জারি করতে চায় না, তাদের জন্য কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য আলাদা ওয়ার্ড রাখতে হবে। আলাদা চিকিৎসক দরকার। গাইনোকোলজিস্টদের বেশি বেশি প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
বহির্বিভাগের ৫০% রোগীর এন্ডোমেট্রিওসিস সমস্যা
ডা. ফারজানা দীবা
 সচেতনতা তৈরি এন্ডোমেট্রিওসিস রোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আমরা বিএসএমএমইউতে বন্ধ্যাত্বের পাশাপাশি এন্ডোমেট্রিওসিসের চিকিৎসা করি। কিছু রোগী আসে শুধু মাসিকজনিত রোগ নিয়ে। আবার কিছু রোগী আসে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে। এ সময় আমরা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগী পেয়ে যাই। ৩০ শতাংশ রোগী আমরা আউটডোরে পাই। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ রোগীই এন্ডোমেট্রিওসিস সমস্যা নিয়ে আসে। দেখা যায়, প্রতি দুইজনের একজন এই রোগে ভুগছে। এখানে কিছু কিশোরীও আসে।
সচেতনতা তৈরি এন্ডোমেট্রিওসিস রোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। আমরা বিএসএমএমইউতে বন্ধ্যাত্বের পাশাপাশি এন্ডোমেট্রিওসিসের চিকিৎসা করি। কিছু রোগী আসে শুধু মাসিকজনিত রোগ নিয়ে। আবার কিছু রোগী আসে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে। এ সময় আমরা এন্ডোমেট্রিওসিস রোগী পেয়ে যাই। ৩০ শতাংশ রোগী আমরা আউটডোরে পাই। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ রোগীই এন্ডোমেট্রিওসিস সমস্যা নিয়ে আসে। দেখা যায়, প্রতি দুইজনের একজন এই রোগে ভুগছে। এখানে কিছু কিশোরীও আসে।
আইভিএফ সফলতা ৪০ শতাংশ
ডা. ফ্লোরিডা রহমান
 প্রথমে আমরা রোগীকে কাউন্সেলিং করি। এরপর প্রত্যেক রোগীর ট্রান্সভ্যাজাইনাল সনোগ্রাফি করি। জানার চেষ্টা করি সিস্টের পরিমাপ চার সেন্টিমিটারের বেশি না কম। একই সঙ্গে আলট্রাসনোগ্রাফ করে বোঝার চেষ্টা করি রোগী কোন পর্যায়ে রয়েছে। এরপর ডিম্বাশয়ের সক্ষমতা যাচাই, বড় ধরনের কোনো সমস্যা বা কোমরবিডিটিস আছে কি না দেখে নিই।
প্রথমে আমরা রোগীকে কাউন্সেলিং করি। এরপর প্রত্যেক রোগীর ট্রান্সভ্যাজাইনাল সনোগ্রাফি করি। জানার চেষ্টা করি সিস্টের পরিমাপ চার সেন্টিমিটারের বেশি না কম। একই সঙ্গে আলট্রাসনোগ্রাফ করে বোঝার চেষ্টা করি রোগী কোন পর্যায়ে রয়েছে। এরপর ডিম্বাশয়ের সক্ষমতা যাচাই, বড় ধরনের কোনো সমস্যা বা কোমরবিডিটিস আছে কি না দেখে নিই।
যদি রোগী স্টেজ-ওয়ান বা স্টেইজ-টুতে থাকে, যেটাকে বলে মাইল্ড এন্ডোমেট্রিওসিস।
স্টেজ-থ্রি বা স্টেজ-ফোর রোগীর ক্ষেত্রে সরাসরি আইভিএফ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা ছাড়া আইভিএফ করলে যেখানে স্টেজ-ওয়ান বা স্টেজ-টু সফলতার হার ৪০ শতাংশ, সেখানে স্টেজ-থ্রি বা স্টেজ-ফোর সফলতা ১২ থেকে ১৩ শতাংশ। এ জন্য আমেরিকান সোসাইটির গাইডলাইন অনুযায়ী যদি কারো ব্যথা থাকে, ডিম্বাশয়ের রিজার্ভ ভালো, এর সঙ্গে ডিম্বাশয়ের এন্ডোমেট্রিওমা আছে চার সেন্টিমিটারের বেশি—এ ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপি করার কথা বলা আছে।
যাদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি, ডিম্বাশয়ের রিজার্ভ অনেক কম—এই রোগীদের আমরা বলি, আপনার বিকল্প চিকিৎসা হচ্ছে আইভিএফ।
‘টিভিএস’ এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে সহজ পদ্ধতি
ডা. মাহফুজা মাহমুদ চৈতি
 এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে ট্রান্স-অ্যাবডোমিনাল আলট্রাসাউন্ড, ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড ও এমআরআই করে থাকি। কিন্তু এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে যেসব পরীক্ষা পদ্ধতি আছে তার মধ্যে ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড বা টিভিএস একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সংবেদনশীলতা ও সঠিক রোগ শনাক্তের হার ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ। একই সঙ্গে রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে পারি।
এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে ট্রান্স-অ্যাবডোমিনাল আলট্রাসাউন্ড, ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড ও এমআরআই করে থাকি। কিন্তু এন্ডোমেট্রিওসিস শনাক্তে যেসব পরীক্ষা পদ্ধতি আছে তার মধ্যে ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড বা টিভিএস একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সংবেদনশীলতা ও সঠিক রোগ শনাক্তের হার ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ। একই সঙ্গে রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে পারি।
ট্রান্সভ্যাজাইনাল আলট্রাসাউন্ড খুবই সহজলভ্য। এটা যোনিতে একটি ছোট কাঠির মতো ডিভাইস (ট্রান্সডুসার) স্থাপন করে সঞ্চালিত হয়। ইউটেরাস, জরায়ু, ফেলোপেন টিউব—সব ছবি নিয়ে আমরা পরীক্ষা করতে পারি। এ বিষয়ে দক্ষ না হলে শনাক্তকরণ ভুল হতে পারে।
টিভিএস পরীক্ষা এখন আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞই করছেন। আমাদের উচিত যেসব জায়গায় ভালোভাবে পরীক্ষাটা হয় সেখানে এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীকে পাঠানো। গাইনোকোলজিস্টরা বিশেষ প্রশিক্ষণ পেলে এন্ডোমেট্রিওসিস বা চকোলেট সিস্ট—এগুলো পরীক্ষা করতে পারে। এতে রোগটি দ্রুত শনাক্ত করতে পারব।
ঘর থেকে ক্ষমতায়নের যাত্রা শুরু করতে হবে
ডা. মো. মনজুর হোসেন
 বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসার যত প্রটোকল, গাইডলাইন, চেকলিস্ট—সব কিছু পেশাদার সংগঠনের থেকে নিয়ে বাস্তবায়ন করে থাকি। এন্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাডেনোমায়োসিস, পিসিওএস প্রোগ্রাম কিন্তু আগে ছিল না। তবে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে এর কৌশলগত উন্নয়ন যেটুকু করেছিলাম, সেখানেও প্রশিক্ষণ ছিল না। আপনারা জেনে খুশি হবেন, ওজিএসবির সহায়তায় সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় এই তিন বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসার যত প্রটোকল, গাইডলাইন, চেকলিস্ট—সব কিছু পেশাদার সংগঠনের থেকে নিয়ে বাস্তবায়ন করে থাকি। এন্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাডেনোমায়োসিস, পিসিওএস প্রোগ্রাম কিন্তু আগে ছিল না। তবে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে এর কৌশলগত উন্নয়ন যেটুকু করেছিলাম, সেখানেও প্রশিক্ষণ ছিল না। আপনারা জেনে খুশি হবেন, ওজিএসবির সহায়তায় সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় এই তিন বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।
নারীর ক্ষমতায়ন কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বলব, ঘর থেকে যাত্রা শুরু করো। আমি যদি আমার সমাজকে, আমার মেয়েকে ক্ষমতায়ন করতে চাই, আমার বাড়ি থেকে শুরু করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সুশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়ন। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই তথ্য বেশির ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এ জন্য স্কুল হেলথ এডুকেশন প্রোগ্রামে পাঠ্যক্রম রয়েছে। সেখানে কিছু পাঠ আমরা যোগ করেছি। তবে বিদ্যমান কাঠামোতে আমরা এখনো এন্ডোমেট্রিওসিস ও অ্যাডেনোমায়োসিস যোগ করতে পারিনি। আজকে যেহেতু আমরা একত্র হয়েছি এবং এখানে এন্ডোমেট্রিওসিসকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমার বিদ্যমান কাঠামোতে এ বিষয়গুলো যুক্ত করতে।
নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে এন্ডোমেট্রিওসিস
ডা. মো. সাঈদ বিন ফয়সল
 শুধু চিকিৎসা দিয়ে এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময় সম্ভব নয়। আমরা যদি সচেতনতা তৈরি করতে না পারি, আমাদের কোনো পরিশ্রমই অর্থবহ হবে না। স্কুল, পাঠ্যবই, শিক্ষক বা সরকারি কোনো সাহায্যের মাধ্যমে যদি সচেতনতা তৈরি করা যায় তাহলে দ্রুততম সময়ে শনাক্ত ও নিরাময় করতে পারব। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা অর্থবহ হবে। অনেক রোগীকে সার্জারি পর্যন্ত যেতে না-ও হতে পারে।
শুধু চিকিৎসা দিয়ে এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময় সম্ভব নয়। আমরা যদি সচেতনতা তৈরি করতে না পারি, আমাদের কোনো পরিশ্রমই অর্থবহ হবে না। স্কুল, পাঠ্যবই, শিক্ষক বা সরকারি কোনো সাহায্যের মাধ্যমে যদি সচেতনতা তৈরি করা যায় তাহলে দ্রুততম সময়ে শনাক্ত ও নিরাময় করতে পারব। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা অর্থবহ হবে। অনেক রোগীকে সার্জারি পর্যন্ত যেতে না-ও হতে পারে।
নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে এন্ডোমেট্রিওসিস। নতুন বাংলাদেশে এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময়ে আমাদের সবার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি। আমি ইনসেপ্টার পক্ষ থেকে বলব, এন্ডোমেট্রিওসিস নিরাময়ে সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যে বাজারে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। যেকোনো ধরনের সচেতনতা বা চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজে ইনসেপ্টা অত্যন্ত উৎসাহী। আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং সব সময় থাকব।
বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

কালের কণ্ঠের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ রবিবার দিনব্যাপী রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটির কনফারেন্স রুমে ‘বিজয় দিবস : নতুন প্রত্যাশা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, গবেষক,
পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। আলোচনার সারসংক্ষেপ নিয়ে আজকের দুই পাতার এই বিশেষ আয়োজন। গ্রন্থনা ও সমন্বয় করেছেন কালের কণ্ঠের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।
সংবিধান সংস্কার নয়, এটা নতুন করে লিখতে হবে
অধ্যাপক ড. মাহবুবউল্লাহ
ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী ও আওয়ামী লীগ ১০০ বছর ধরে যেসব বয়ান তৈরি করে রেখেছিল, তা আমাদের ঘায়েল করেছে। বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বয়ান তৈরি করতে হবে।
 এই দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। একক কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে নতুন বয়ান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মতামতের সারসংক্ষেপ সংকলন করে এটি তৈরি করতে হবে।
এই দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। একক কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে নতুন বয়ান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মতামতের সারসংক্ষেপ সংকলন করে এটি তৈরি করতে হবে।
ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে নতুন অভিজাত শ্রেণি জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন করে।
এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বাহাত্তরের সংবিধান তৈরি হয়েছিল। এই সংবিধানে একটি দেশ চলতে পারে না। সংবিধান নতুন করে লিখতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নতুন সামাজিক চুক্তি করতে হবে, যেটার মাধ্যমে জনগণের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারব। সেই সংবিধানে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে। শুধু আইনের শাসন নয়, সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বভিত্তিক সমাজ গঠন করতে হবে।
ভারতের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আগে যেভাবে গোপন চুক্তি হয়েছিল, সেটি নতুন করে ভাবতে হবে। শেখ হাসিনা ও অন্য সরকারগুলোর সময় দেশে যত অসম ও রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তি হয়েছে, সেগুলো বাতিলের দুঃসাহস থাকতে হবে। জুলাই আন্দোলন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই আন্দোলনে আমাদের মূল শিক্ষা—ক্ষমতা চিরকাল ধরে রাখা যায় না। অভ্যুত্থানের পর নানা সংকটের সৃষ্টি হয়। এগুলো উত্তরণে উদ্যমী নেতৃত্বের প্রয়োজন।
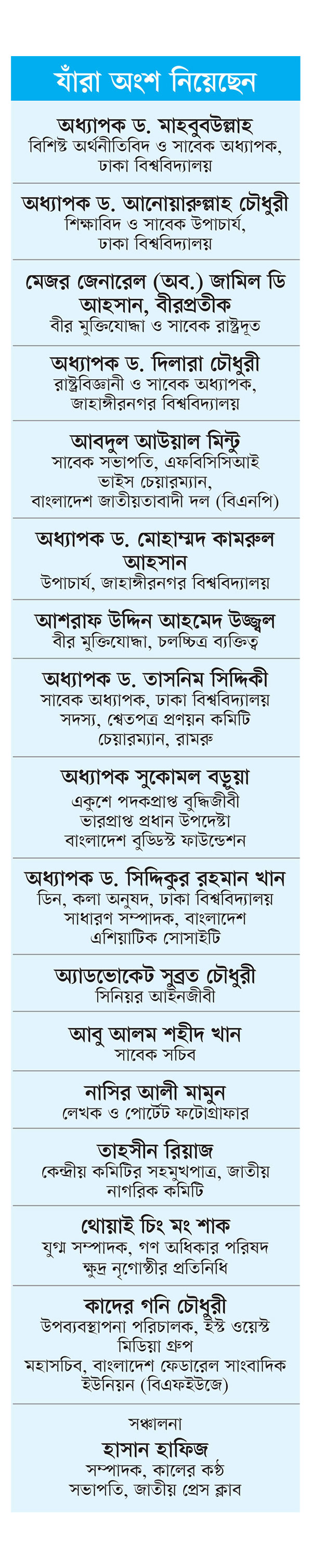 মুক্তির জন্য আরো বন্ধুর পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে
মুক্তির জন্য আরো বন্ধুর পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে
অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী
বিজয় দিবসে আমার অনুভূতি দুই ধরনের। একটি আনন্দের, অন্যটি বিষাদের। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমার মতো অন্য শিক্ষক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বাহাত্তর সালে যখন দেশে ফিরে  এলাম, দেখি অনেক সহকর্মী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। এই স্বাধীনতা তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন ও গর্বের। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, কারণ পাকিস্তান আমলে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না, কথা বলার অধিকার ছিল না। জনগণের ধারণা ছিল, দেশ স্বাধীন হলে গণতন্ত্র ফিরে পাবে। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পাইনি।
এলাম, দেখি অনেক সহকর্মী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। এই স্বাধীনতা তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন ও গর্বের। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, কারণ পাকিস্তান আমলে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না, কথা বলার অধিকার ছিল না। জনগণের ধারণা ছিল, দেশ স্বাধীন হলে গণতন্ত্র ফিরে পাবে। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পাইনি।
বাহাত্তর সালে দেশে ফিরে দেখলাম, আমরা যে গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, তা বিলীন হয়ে গেছে। মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। একদলীয় শাসন কায়েম হলো। রক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হলো। সময়ের ধারাবাহিকতায় নব্বইয়ে একই আকাঙ্ক্ষায় আরেকটি অভ্যুত্থান হলো। এরপর আবার ফ্যাসিবাদের উত্থান হলো। গত ১৫ বছরে অসংখ্য মানুষ গুম ও খুনের শিকার হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার ছিল সারা বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নিষ্ঠুর ফ্যাসিবাদী সরকার। দেশের তরুণসমাজকে আরো অনুপ্রাণিত করতে হবে। আমাদের দেশের তরুণরা শেষ পর্যন্ত এই ফ্যাসিবাদকে তাড়িয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আরেকটি সুযোগ এসেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাম্য-ন্যায়ের প্রত্যাশার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা জারি রাখতে হবে। অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, সেটি পূরণে আমাদের আরো বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, তরুণসমাজের নেতৃত্বে আমাদের পথ চলতে হবে।
অভ্যুত্থানে বিজয় আমাদের প্রথম পর্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, তরুণসমাজের নেতৃত্বে আমাদের পথ চলতে হবে। গণতন্ত্র দিয়ে জনগণের সরকার হয় না, হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার। তাই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তরুণসমাজকে আরো অনুপ্রাণিত করতে হবে।
ভারতের সঙ্গে করা সব চুক্তি উন্মুক্ত করে দিতে হবে
মেজর জেনারেল (অব.) জামিল ডি আহসান বীরপ্রতীক
মহান মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্র বিনির্মাণের সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। আমাদের একটি প্রত্যাশা ছিল যে এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে একটি সম্প্রীতির দেশ গঠিত হবে। আমরা চেয়েছিলাম একটি শক্ত নেতৃত্বের অধীনে আত্মপ্রত্যয়ী একটি জাতি গঠিত হবে। স্বাধীনতার পরই  শাসকদের অবক্ষয়ে সেগুলো হারিয়ে গেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আর পেলাম না। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর আবার নতুন একটি প্রত্যাশা পাওয়া গেল। মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান—দুটিই আমাদের জন্য বড় অর্জন। এই অর্জন রক্ষা করতে হবে।
শাসকদের অবক্ষয়ে সেগুলো হারিয়ে গেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা আর পেলাম না। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর আবার নতুন একটি প্রত্যাশা পাওয়া গেল। মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান—দুটিই আমাদের জন্য বড় অর্জন। এই অর্জন রক্ষা করতে হবে।
এই অর্জন রক্ষায় সুষ্ঠু নেতৃত্ব এবং একতাবদ্ধ থাকতে হবে। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর জাতি নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ। ধর্ম ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে হবে। ভারত আমাদের সম্প্রীতি নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। গত ১৫ বছরে তাদের তৈরি করা ক্ষমতা কাঠামোর পতনের পর কারা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। আমাদের জাতিগত ঐক্য তাদের ভালো লাগছে না। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের জাতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সম্প্রীতির বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। গত ১৫ বছরে ভারতের সঙ্গে হওয়া বাংলাদেশের সব চুক্তি জনগণের সামনে উন্মুক্ত করতে হবে।
বর্তমানে রাজনীতির চরিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। রাজনীতিতে এখন বেশির ভাগই ব্যবসায়ী। ফলে ব্যবসাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থেই রাজনীতির গতিমুখ নির্ধারিত হচ্ছে। এটি বৈষম্য সৃষ্টি করছে, যার বিরুদ্ধে ছাত্ররা অভ্যুত্থান করেছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। রাজনীতিতে সব শ্রেণি ও পেশার অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। তবে সরকারের পাশাপাশি ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকার যেটা বলতে পারে না, সেটা সমন্বয়ক কিংবা ছাত্র নেতাদের দিয়ে বলানো যায়। এটি দেশের জন্য বেশ ভালো কাজ করছে।
আমাদের একটা বিষয় খুব খেয়াল করতে হবে, আবেগ-বিপ্লব আর সরকার পরিচালনা এক জিনিস নয়। পাহাড় ও সমতলের মধ্যে আরো সাম্য প্রয়োজন। সেনাবাহিনী গেছে বিধায় পাহাড় এখনো বাংলাদেশের সঙ্গে আছে। ফলে তাদের সমতলের সঙ্গে আরো কিভাবে সমন্বিতভাবে আনা যায়, সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে।
সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ প্রয়োজন
অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী
১৯৭২ সালে দেশে বুর্জোয়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছিল এক ব্যক্তির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য। অথচ যুদ্ধ করেছিল সাধারণ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের গণমুখী বয়ান তৈরি হয়নি। তাই আমরা বারবার হোঁচট খেয়েছি। সাম্য  ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য, তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ লক্ষ্য পূরণে ছাত্ররা জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থান করেছে। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্ররা সরে আসেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের খুব ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এ জন্যই প্রয়োজন, যেন তাদের থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার আদায় করা যেতে পারে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব দিচ্ছে, কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, সে বিষয়টা স্পষ্ট করছে না। রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে সংস্কার প্রত্যাশা করছে, সেটি রাজনৈতিক দলগুলোকেই বলতে হবে। রাজনৈতিক দলেরও সংস্কার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোতে তৃণমূল পর্যন্ত গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। দলগুলো নিজেদের মধ্যে কী সংস্কার করবে সেটি জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি কিভাবে চলবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সংস্কার প্রয়োজন। জবাবদিহির বিষয়টি সংবিধানের মধ্যেই আনতে হবে। এ জন্য বর্তমান সরকার সংস্কার কার্যক্রম করছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ দেওয়া প্রয়োজন। অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো সংস্কার চলতে পারে না। বাংলাদেশের এখন কোনো বন্ধু নেই, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রগুলোর ছায়া পড়েছে। আমাদের এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রয়োজন, যে জনগণকে নিয়ে এই চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করবে। যে সরকার জনগণের অধিকার নিশ্চিত করবে, জনগণের অর্থ লুট করে বিদেশে পাচার করবে না। ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের শিক্ষার্থীরা লড়াই করেছে। এই আধিপত্যবাদ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আগে সই করা গোপন চুক্তি থেকেই শুরু। এটি বাড়তে বাড়তে এই পর্যায়ে চলে এসেছে।
ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য, তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ লক্ষ্য পূরণে ছাত্ররা জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থান করেছে। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্ররা সরে আসেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের খুব ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এ জন্যই প্রয়োজন, যেন তাদের থেকে জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকার আদায় করা যেতে পারে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব দিচ্ছে, কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, সে বিষয়টা স্পষ্ট করছে না। রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে সংস্কার প্রত্যাশা করছে, সেটি রাজনৈতিক দলগুলোকেই বলতে হবে। রাজনৈতিক দলেরও সংস্কার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোতে তৃণমূল পর্যন্ত গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। দলগুলো নিজেদের মধ্যে কী সংস্কার করবে সেটি জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। ছাত্ররাজনীতি কিভাবে চলবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সংস্কার প্রয়োজন। জবাবদিহির বিষয়টি সংবিধানের মধ্যেই আনতে হবে। এ জন্য বর্তমান সরকার সংস্কার কার্যক্রম করছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের একটি রোডম্যাপ দেওয়া প্রয়োজন। অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো সংস্কার চলতে পারে না। বাংলাদেশের এখন কোনো বন্ধু নেই, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রগুলোর ছায়া পড়েছে। আমাদের এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রয়োজন, যে জনগণকে নিয়ে এই চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করবে। যে সরকার জনগণের অধিকার নিশ্চিত করবে, জনগণের অর্থ লুট করে বিদেশে পাচার করবে না। ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের শিক্ষার্থীরা লড়াই করেছে। এই আধিপত্যবাদ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আগে সই করা গোপন চুক্তি থেকেই শুরু। এটি বাড়তে বাড়তে এই পর্যায়ে চলে এসেছে।
গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনে
আবদুল আউয়াল মিন্টু
৫৩ বছর আগে আমাদের যা প্রত্যাশা ছিল, তা এখনো তেমনই আছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তথা একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু এই প্রত্যাশাটা কে পূরণ করবে? আমি যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা চাই, তা  আজও দেখিনি। রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ইতিবাচক না হলে এসব প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব না। আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, মানবিক মর্যাদা ও সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকুক। রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদেরই দিতে হবে, যারা বৈষম্য কমাতে পারবে, জনগণের অধিকার যারা নিশ্চিত করবে।
আজও দেখিনি। রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ইতিবাচক না হলে এসব প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব না। আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, মানবিক মর্যাদা ও সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকুক। রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদেরই দিতে হবে, যারা বৈষম্য কমাতে পারবে, জনগণের অধিকার যারা নিশ্চিত করবে।
সমাজে দুই শ্রেণির মানুষের বসবাস। এক শ্রেণির মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করছে, যারা সেই সম্পদের পুরো সুবিধাভোগী নয়। অন্য একটি শ্রেণি এই সম্পদ অর্জন করছে এবং বিদেশে সেই সম্পদ পাচারও করছে। দেশের সম্পদের বিলি-বণ্টনে গণতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন। আমরা বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজ চাই। এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হবে, বিনিয়োগ বাড়বে। কারণ আমাদের সমাজে প্রতিবছর ২০ থেকে ২২ লাখ বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। বিনিয়োগ বাড়াতে না পারলে এই বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ বৈষম্যের মুখে পড়বে। একজন ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করার পর তা ফেরত আসার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কায়েমি স্বার্থবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। জনগণের টাকায় পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান গত ১৫ বছরে ধ্বংস করা হয়েছে। এগুলো সংস্কার করতে হবে, যেন তারা জনকল্যাণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এ জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রী করে এর ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। কারণ সব রাজনৈতিক দলই সুযোগ পেয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। রাজনৈতিক দল যেন জনগণের সেবার মানসিকতা থেকে বিচ্যুত না হয়, সে জন্য সংস্কার প্রয়োজন। আইনের শাসনের পরিবর্তে এখন আইনের দ্বারা শাসন চলছে। বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা প্রশাসনের পরিবর্তে সুশাসন চাই।
রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান
স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও আমরা প্রকৃত বিজয় অর্জন করতে পারিনি। এই দেশ যিনি স্বাধীন করেছেন—শেখ মুজিব, তাঁর হাতেই দেশের সংবিধানকে ক্ষমতার হাতিয়ার বানানো হয়েছে, বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৩০ লাখ শহীদ এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ  বুদ্ধিজীবীদের আত্মদানের পরও আমাদের অর্জন বলতে কিছুই নেই। এটি অনুধাবন করা খুবই জরুরি। ৫৩ বছর পর এসে আমরা দেখছি, সংস্কার করার জন্য সব কিছু রয়ে গেল। তাহলে এত দিন আমরা কী করেছি? বারবার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণকে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে হচ্ছে। এবারের জুলাই অভ্যুত্থানে যে ঐক্য অর্জিত হয়েছে, যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে—সেগুলো হাতছাড়া করা যাবে না। যখন সন্তু লারমাদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার আহবান জানানো হয়েছিল, তখন থেকেই বিভাজনের রাজনীতি শুরু। অথচ প্রয়োজনে বাংলাদেশের সব মানুষ একত্র হয়ে অভ্যুত্থান করে। এ জন্যই সব ব্যর্থতার মধ্যেও আমাদের অর্জন আমরা বাংলাদেশি বলে নিজেদের পরিচয় লিখি। দেশের নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহবান থাকবে, রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের বিষয়টিতে নজর দিন। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আবার প্রশাসনিক চাকরির মাধ্যমে ক্ষমতার কাছে থাকার প্রবণতার বিরুদ্ধে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। এই প্রবণতার মধ্যেই সব সংকটের মূল লুকিয়ে আছে। এই প্রবণতাই শেখ হাসিনার মতো স্বৈরশাসক এবং আজিজ-বেনজীরের মতো প্রশাসক তৈরি করেছে। আমাদের সন্তানরা নিজেদের জীবন দিয়ে এই স্বৈরাচারদের বিদায় করেছে। তবে এর অবসান করতে হবে, কতবার শিক্ষার্থীদের প্রাণ দিতে হবে?
বুদ্ধিজীবীদের আত্মদানের পরও আমাদের অর্জন বলতে কিছুই নেই। এটি অনুধাবন করা খুবই জরুরি। ৫৩ বছর পর এসে আমরা দেখছি, সংস্কার করার জন্য সব কিছু রয়ে গেল। তাহলে এত দিন আমরা কী করেছি? বারবার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণকে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে হচ্ছে। এবারের জুলাই অভ্যুত্থানে যে ঐক্য অর্জিত হয়েছে, যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে—সেগুলো হাতছাড়া করা যাবে না। যখন সন্তু লারমাদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার আহবান জানানো হয়েছিল, তখন থেকেই বিভাজনের রাজনীতি শুরু। অথচ প্রয়োজনে বাংলাদেশের সব মানুষ একত্র হয়ে অভ্যুত্থান করে। এ জন্যই সব ব্যর্থতার মধ্যেও আমাদের অর্জন আমরা বাংলাদেশি বলে নিজেদের পরিচয় লিখি। দেশের নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহবান থাকবে, রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের বিষয়টিতে নজর দিন। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আবার প্রশাসনিক চাকরির মাধ্যমে ক্ষমতার কাছে থাকার প্রবণতার বিরুদ্ধে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। এই প্রবণতার মধ্যেই সব সংকটের মূল লুকিয়ে আছে। এই প্রবণতাই শেখ হাসিনার মতো স্বৈরশাসক এবং আজিজ-বেনজীরের মতো প্রশাসক তৈরি করেছে। আমাদের সন্তানরা নিজেদের জীবন দিয়ে এই স্বৈরাচারদের বিদায় করেছে। তবে এর অবসান করতে হবে, কতবার শিক্ষার্থীদের প্রাণ দিতে হবে?
বৈচিত্র্যের নামে বিভাজন এবং পরিবর্তনের নামে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এই বিভাজনের বিরুদ্ধে ৭ নভেম্বর যেভাবে ঐক্য তৈরি হয়েছিল, ‘বাঙালি হয়ে যাওয়ার’ বিরুদ্ধে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ঐক্য হয়েছিল। এসব থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হ্বে। স্বৈরাচার যেন ফিরে আসতে না পারে তার জন্য জনগণের ক্ষমতা সুসংহত করতে হবে। প্রত্যাশিত পরিবর্তন যতটুকু দরকার, এ জন্য সবাইকে নিয়ে ডায়ালগ করতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্বকে সামনে রেখে সব মতকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মতৈক্যের জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা।
একক উন্নতি নয় সামষ্টিক উন্নতি হতে হবে মূলমন্ত্র
আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জ্বল
মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পর আমাদের দেশটি পরিণত সময়ে থাকার কথা থাকলেও এখন দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। যাদের এটি রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল, তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের ব্যর্থতা হচ্ছে, আমরা ব্যক্তিগত লাভের আশায় দেশের  সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি ভুলে গেছি। তাই দেশ বারবার স্বৈরাচারের কবলে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গত ১৫ বছরের স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংস হয়েছে। চলচ্চিত্রশিল্পটি এতটাই রুগ্ণ হয়েছে যে, এখানে আশু সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কৃতির উন্নয়নে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, একাডেমিক ফ্যাসিলিটির অবস্থা খুবই দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাটক, চলচ্চিত্রের জন্য খোলা বিভাগগুলোয় নাকি বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। জ্ঞান ও মেধাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা না হওয়ায় এমন দুর্দশা, কারণ নাটক ও চলচ্চিত্র কোনো চাকরি নয়।
সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি ভুলে গেছি। তাই দেশ বারবার স্বৈরাচারের কবলে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গত ১৫ বছরের স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংস হয়েছে। চলচ্চিত্রশিল্পটি এতটাই রুগ্ণ হয়েছে যে, এখানে আশু সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কৃতির উন্নয়নে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, একাডেমিক ফ্যাসিলিটির অবস্থা খুবই দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাটক, চলচ্চিত্রের জন্য খোলা বিভাগগুলোয় নাকি বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। জ্ঞান ও মেধাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা না হওয়ায় এমন দুর্দশা, কারণ নাটক ও চলচ্চিত্র কোনো চাকরি নয়।
বিগত স্বৈরাচারের আমলে বড় বড় দালান হয়েছে, স্টুডিও হয়েছে, কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের মানুষ তৈরি হয়নি। চলচ্চিত্রে কলাকুশলীদের মেধা লালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্বউদ্যোগে যাঁরা ভালো কাজ করেছেন, তাঁদের মূল্যায়ন করা হয়নি। চলচ্চিত্রের সোনালি যুগ ফেরাতে মেধাভিত্তিক বরাদ্দ লাগবে।
প্রবীণ প্রজন্মের অভিজ্ঞতা এবং নতুন প্রজন্মের উদ্যমের মধ্য দিয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একক উন্নতি নয়, সামষ্টিক উন্নতি—এই চিন্তাটি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বপন করতে হবে। উন্নয়নের লক্ষ্য হবে পরিবার ও গোষ্ঠীর জন্য তথা সামষ্টিক উন্নয়ন। বিগত ১৫ বছরে আমরা দেখলাম, বিদ্যমান ব্যবস্থা এমন ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অনধিকার চর্চা করে। যেমন—পুলিশের ক্ষমতা ব্যবহার করেছে বেনজীর-বিপ্লবের মতো মানুষেরা, যারা ক্ষমতা পেয়ে জনগণকে নিপীড়ন করেছে। এমন একটি পদ্ধতি তৈরি করতে হবে, যেন ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ আর কেউ না পায়।
জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রে জনগণের অংশীদারি নিশ্চিতে সংসদে প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সংসদের উচ্চকক্ষ থাকতে হবে, যেখানে শিক্ষক, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞরা দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবেন।
জাতীয় সংসদে ৩৩ শতাংশ নারী হতে হবে নির্বাচিত
অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী
নতুন বাংলাদেশে সবার প্রথমে আমি রাজনীতিতে এমন একটা ব্যবস্থা চাই, যেখানে হাজার চেষ্টা করেও কেউ একচ্ছত্র স্বৈরাচারী ক্ষমতা আর ব্যবহার করতে পারবে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যদি সংস্কার না আনতে পারি, তাহলে স্বৈরাচার ফিরে আসবে। একটি  বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ক্ষমতা কখনোই এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা দেখেছি, একই ব্যক্তি একাধারে দলের প্রধান, পার্লামেন্টের প্রধান ও নির্বাহী প্রধান। এই জায়গাটাতে সংস্কারের মাধ্যমে তিন ব্যক্তিকে আলাদা করতে হবে। সংবিধানের যে পরিবর্তন আসছে, সেখানে নিশ্চিত করতে হবে যেখানে তিন ব্যক্তি আলাদা হবে। যেখানে ক্ষমতা ভাগ হবে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বিভাজনের জন্য আমাদের দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের জন্য সুন্দর আগামী নিশ্চিত করতে হলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন এখন সময়ের দাবি।
বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ক্ষমতা কখনোই এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা দেখেছি, একই ব্যক্তি একাধারে দলের প্রধান, পার্লামেন্টের প্রধান ও নির্বাহী প্রধান। এই জায়গাটাতে সংস্কারের মাধ্যমে তিন ব্যক্তিকে আলাদা করতে হবে। সংবিধানের যে পরিবর্তন আসছে, সেখানে নিশ্চিত করতে হবে যেখানে তিন ব্যক্তি আলাদা হবে। যেখানে ক্ষমতা ভাগ হবে। আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বিভাজনের জন্য আমাদের দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের জন্য সুন্দর আগামী নিশ্চিত করতে হলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন এখন সময়ের দাবি।
এবারের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নারীরাও অসম সাহস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা অংশ নিয়েছেন। যদি তাঁরা না আসতেন, তাহলে আজকের বিপ্লব কতটুকু সার্থক হতো তা নিয়ে আমি সন্দিহান। সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন বাতিল করতে হবে। মোট আসনের ৩৩ শতাংশ আসনে নারী আসতে হবে। এটি করতে না পারলে নারীরা পিছিয়ে পড়বেন। তরুণ নেতৃৃত্ব ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা এগোবে না। গ্রাম থেকে নেতৃত্ব বাছাই করে আনতে হবে। দলগুলোর গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে গ্রামের নেতৃত্ব আনতে হবে। আমরা দেখছি যে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন দফা ও দাবি দিচ্ছে। কিন্তু দলের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন কিভাবে আনবে, সেটি বলছে না। গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন না এলে নতুন নেতৃত্ব কিভাবে আসবে? আমি সন্ত্রাসমুক্ত ছাত্ররাজনীতি চাই। নারী হিসেবে প্রতিটা জায়গায় সমান অধিকার চাই। এই অধিকার যেমন ঘোমটা দেওয়ার, তেমনি ঘোমটা ছাড়া চলার অধিকার। সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাই না। আমি চাই না আমার ওপর কারো কর্তৃত্ব আসুক। যেই কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের আবরণের মধ্য দিয়ে একজন নারী কিভাবে চলবে তা শিখিয়ে দেবে, সেই শিক্ষা চাই না।
গণ-অভ্যুত্থানের অর্জন রক্ষায় জাতিগত ঐক্য তৈরি করতে হবে
অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া
১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর দীর্ঘ ৫৪ বছর আমরা পার করেছি। এর মধ্যে বিগত সাড়ে ১৫টি বছর আমরা বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মধ্যেই কারারুদ্ধ ছিলাম। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের মুক্তি ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার  খুলে গেছে। মানুষ তার চির আকাঙ্ক্ষিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। বিগত স্বৈরাচার যা কিছু গোপন করেছিল, তা আজ আমরা সবাই মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পারছি। মুক্তিযুদ্ধের পর আবারও এ দেশের মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পেয়েছে। এই অর্জনগুলো রক্ষায় আমাদের জাতিগত ঐক্য তৈরি করতে হবে। ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানের রক্তভেজা অর্জনগুলোকে কাজে লাগাতে আমাদের হতে হবে সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী।
খুলে গেছে। মানুষ তার চির আকাঙ্ক্ষিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। বিগত স্বৈরাচার যা কিছু গোপন করেছিল, তা আজ আমরা সবাই মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পারছি। মুক্তিযুদ্ধের পর আবারও এ দেশের মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পেয়েছে। এই অর্জনগুলো রক্ষায় আমাদের জাতিগত ঐক্য তৈরি করতে হবে। ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানের রক্তভেজা অর্জনগুলোকে কাজে লাগাতে আমাদের হতে হবে সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী।
সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন প্রজন্ম খুবই সচেষ্ট, তাদের এ চেতনা সত্যিই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই প্রজন্ম যেকোনো অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের এই প্রাণবন্ত চেতনার সঙ্গে দেশের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছে, মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্ভব ঘটেছে। দেশ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সবার একত্রিত চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু, এভাবে বিভাজন করাটা বাংলাদেশের একজন নাগরিকের জন্য বিব্রতকর। পাহাড়ি ও বাঙালি, এভাবে বিভাজন করার জন্য বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়নি। আমি মনে করি, সার্বভৌম-স্বাধীন দেশের মধ্যে এসব বিভাজনের রাজনীতিকে আর ফিরতে দেওয়া যাবে না। প্রিয় মাতৃভূমিকে মনের মতো করে গড়ার উপযুক্ত সময় এখন এসে গেছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা একজন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞজন। মানুষকে একটি সম্ভাবনার দেশ দিতে চান তিনি। বিগত ১৬ বছরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশটাকে সংস্কার করতে তাঁকে সময় দিতে হবে। এই সংস্কারগুলোর মধ্য দিয়ে দেশে সম্প্রীতির আবরণ তৈরি হবে। আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলনে সব দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের দেশের ৫১টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ কথা বলবে। এই দেশের সম্প্রীতির অভিজাত্য সম্পর্কে তারা জানবে।
প্রতিবেশীর দাদাগিরি আচরণ আমরা মোটেও প্রত্যাশা করি না
অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান খান
১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে মহৎ অর্জন। ২৪ বছরের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজ ও  রাষ্ট্র বিনির্মাণ, একটি শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ তৈরি। আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা নিপাট জনযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। এটার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান পেয়েছিল। ৫৪ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সব সময়ই উন্নয়নের কথা বলেছে। কিন্তু সেই উন্নয়ন সাধারণ মানুষ কখনোই পায়নি। স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এরশাদ সরকার এসে তা ভূলুণ্ঠিত করে। রক্ত দিয়ে মানুষ গণ-অভ্যুত্থান করেছিল। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পথচলা শুরু করেছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এর মধ্য দিয়ে টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাত্রাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। চব্বিশের অভ্যুত্থানে সেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পতন হয়েছে। শ্বেতপত্র কমিটি ও গুম কমিশনের প্রতিবেদনে গত সরকারের নানা তথ্য উঠে এসেছে। এখানকার তথ্যগুলো শিহরিত করে তুলছে সাধারণ মানুষকে। আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে যাতে সবাই টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে পারে। আমরা এমন রাষ্ট্রকাঠামো চাই যেখানে আমার কষ্টার্জিত অর্থ শাসকগোষ্ঠী পাচার করে বিদেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারে। আমরা মানবিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই। ন্যায়ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাজ চাই।
রাষ্ট্র বিনির্মাণ, একটি শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ তৈরি। আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা নিপাট জনযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। এটার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান পেয়েছিল। ৫৪ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সব সময়ই উন্নয়নের কথা বলেছে। কিন্তু সেই উন্নয়ন সাধারণ মানুষ কখনোই পায়নি। স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের কবর রচনা করেছিল। সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এরশাদ সরকার এসে তা ভূলুণ্ঠিত করে। রক্ত দিয়ে মানুষ গণ-অভ্যুত্থান করেছিল। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পথচলা শুরু করেছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এর মধ্য দিয়ে টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাত্রাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। চব্বিশের অভ্যুত্থানে সেই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পতন হয়েছে। শ্বেতপত্র কমিটি ও গুম কমিশনের প্রতিবেদনে গত সরকারের নানা তথ্য উঠে এসেছে। এখানকার তথ্যগুলো শিহরিত করে তুলছে সাধারণ মানুষকে। আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে যাতে সবাই টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে পারে। আমরা এমন রাষ্ট্রকাঠামো চাই যেখানে আমার কষ্টার্জিত অর্থ শাসকগোষ্ঠী পাচার করে বিদেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারে। আমরা মানবিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই। ন্যায়ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাজ চাই।
নির্বাচন নিয়ে বেশি অপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না
অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী
জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে সফলতার পরও আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যটিতে দৃষ্টি রাখতে পারছি না। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর আমরা যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবারও তাই ঘটছে। অভ্যুত্থানের পর সব দাবিদাওয়া নিয়ে আলাপ করে তা  সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। সংস্কার বিলম্বিত হলে মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে।
সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। সংস্কার বিলম্বিত হলে মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে।
রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে নতুন প্রত্যাশার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় আনতে হবে। বিগত ১৫ বছর মানুষ ভোট দিতে পারেনি, জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের সব নির্বাচন হয়েছে ভোটারহীন। দ্রুত একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচন নিয়ে বেশি অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহবান থাকবে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার। শেখ হাসিনা এক ব্যক্তি এক দলের ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সংবিধানে ইচ্ছামতো কাটাছেঁড়া করেছিলেন, কোনো লাভ হয়নি। সংবিধানকে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটি বেশি কাটাছেঁড়া করা ঠিক হবে না। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সংস্কার করতে হবে। বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে, এ ছাড়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আগের সরকারগুলো যা করেছে, তার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে স্বৈরশাসনের বিচার করতে হবে। একদলীয় বিচারক ও আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া ঠিক হবে না। নইলে নতুন এই বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। বিচার বিভাগের সংস্কার খুবই জরুরি। বিচারক নিয়োগের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে শেখ হাসিনা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাতিল করেছিলেন। বিচারপতিদের অনিয়মের বিষয়ে এই কাউন্সিল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। এটি বাতিল করে শেখ হাসিনা বিচার বিভাগকে পরাধীন করেছেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত করতে উদ্যোগ নিতে হবে। জনগণের মতামত দেওয়ার এবং রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে জবাবাদিহির আওতায় আনতে হবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।
সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে
আবু আলম শহীদ খান
বৈষম্যহীন মানুষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি হবে—সেই প্রত্যাশা নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। সংবিধানে প্রস্তাব ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন একটি সুষম সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং  রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু গত ৫৪ বছরে কী পেলাম? একাত্তর থেকে চব্বিশের এই পর্যন্ত বলতে গেলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো করে বলতে হয়, ‘কেউ কথা রাখেনি’। এমন রাজনৈতিক কাঠামো চাই, যেখানে ফ্যাসিবাদ যেন ফিরে আসতে না পারে। সব খারাপ কাজ তারা করেছে। সে জন্য সংস্কার ও নির্বাচনের কথা হচ্ছে।
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু গত ৫৪ বছরে কী পেলাম? একাত্তর থেকে চব্বিশের এই পর্যন্ত বলতে গেলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো করে বলতে হয়, ‘কেউ কথা রাখেনি’। এমন রাজনৈতিক কাঠামো চাই, যেখানে ফ্যাসিবাদ যেন ফিরে আসতে না পারে। সব খারাপ কাজ তারা করেছে। সে জন্য সংস্কার ও নির্বাচনের কথা হচ্ছে।
সংস্কার চলমান প্রক্রিয়া। আমরা মনে করি, প্রত্যাশিত সংস্কার হবে। সঙ্গে নির্বাচনের আলোচনাও চলবে। নির্বাচনে সব প্রার্থীর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকতে হবে। উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন চাই। ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন। ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট যেন গণনা করা হয়। ভোট কেন ভালো হয় না, তার পরিষ্কার উত্তর—যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা এসব হতে দেয় না। তারা পুলিশ প্রশাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। সিভিল আইন বা গণকর্মচারী আইন এমন হতে হবে, যেখানে মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ও বদলি হবে, পদায়ন হবে। কোনো রাজনৈতিক বিবেচনায় যেন এগুলো করা না হয়। প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারীদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। গণকর্মচারী, বিশেষ করে বিচারক, পুলিশ, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে ঠিকমতো গড়ে তুলতে হবে। তাদের ব্যবহার করা হয়েছে বলেই একটি কমিশন একটি বাহিনীকে তুলে নেওয়ার বা বন্ধ করার সুপারিশ বা প্রস্তাব করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো নতুন নতুন বাহিনী বানিয়েছে প্রতিপক্ষকে খুনের জন্য। আমরা তেমন কোনো বাহিনী চাই না।
আয়নাঘর আর যেন দেশে ফিরে আসতে না পারে
নাসির আলী মামুন
বিজয় দিবসকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেওয়া যাবে না। সমুদ্রসীমা নিয়ে আমরা কথা বলছি না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমুদ্রসীমার বিষয়ে কয়েক শ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল। সেটির অগ্রগতি কত দূর, সে বিষয়টা জানতে হবে। কোনোভাবেই সমুদ্রসীমার  বিষয়টি ভুললে চলবে না। এই পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ নিয়ে সুখ-সমৃদ্ধির বাংলাদেশ দেখতে চাই। এ জন্য সবাইকে আওয়াজ তুলতে হবে। ১৬ বছরে স্বৈরাচার তৈরি হয়নি। এর বহু আগে তৈরি হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৪ সালে রক্ষীবাহিনী যাত্রা শুরু করে। ওই বছরের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ছিল। ওই দিন মিন্টো রোডে মিছিল হয়। সেই মিছিলে গুলি করে ২৫ জনকে হত্যা করা হয়। আমি ক্যামেরা নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আ স ম আবদুর রব, মেজর জলিলসহ ওই সময়ের বেশির ভাগ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করে।
বিষয়টি ভুললে চলবে না। এই পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ নিয়ে সুখ-সমৃদ্ধির বাংলাদেশ দেখতে চাই। এ জন্য সবাইকে আওয়াজ তুলতে হবে। ১৬ বছরে স্বৈরাচার তৈরি হয়নি। এর বহু আগে তৈরি হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৪ সালে রক্ষীবাহিনী যাত্রা শুরু করে। ওই বছরের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ছিল। ওই দিন মিন্টো রোডে মিছিল হয়। সেই মিছিলে গুলি করে ২৫ জনকে হত্যা করা হয়। আমি ক্যামেরা নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আ স ম আবদুর রব, মেজর জলিলসহ ওই সময়ের বেশির ভাগ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করে।
আমাদের দেশে উধাও হওয়ার রাজনীতি রয়েছে। আমাদের দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান ছিল, পরিকল্পিতভাবে তাঁদের ইতিহাস থেকে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মওলানা ভাসানী, কমরেড মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মেজর জিয়াউর রহমান, কাদের সিদ্দিকীসহ অসংখ্য মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু বই থেকে তাঁদের ইতিহাস উধাও করে দেওয়া হয়েছে। শুধু ইতিহাস থেকে নয়, অনেক মানুষকে গুম করা হয়েছে। আয়নাঘর বহু আগে থেকেই তৈরি হয়েছে। আমাদের ভেতরে নৈরাজ্যবাদ, স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদ রয়েছে।
নিজেদের এই ফ্যাসিবাদ দূর করতে
হবে। প্রত্যাশা থাকবে, ভবিষ্যতে যেন কোনো আয়নাঘর না হয়। পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে গেলে মালয়েশিয়া
থেকেও সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশ।
ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি হতে হবে
তাহসীন রিয়াজ
একাত্তর আসলে আমাদের মৌলিক চিন্তার জায়গা। একাত্তর সালে আমাদের পথচলা শুরু। সেই একাত্তর থেকেই আমাদের ভাবনাগুলো শুরু। সেই ভাবনা পূর্ণতা পেয়েছে ২০২৪ সালে এসে। একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রামে মানুষ জীবন দিয়েছে দেশকে ঐক্যবদ্ধ  করতে; কিন্তু তারা জীবন দিলেও বাংলাদেশে বিভাজনের রাজনীতি আছে। বাংলাদেশে আমরা স্বৈরাচারিতা দেখেছি। আমরা আয়নাঘর দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের বোনদের ওপর হামলা দেখেছি, অসংখ্য মা-বাবার কান্না দেখেছি, বাবাদের আহাজারি দেখেছি, গুম-খুন দেখেছি। সত্যিকার অর্থে একাত্তর পূর্ণতা পায়নি। আমাদের গুরুজন যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই একমত ছিলেন বিধায় আমরা চব্বিশে স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে পেরেছি। একটা রাষ্ট্রে ১৬ বছর ধরে এমন শাসনব্যবস্থা ছিল, যেখানে যারাই সঠিক কথা বলেছে, তাদের বিভাজনের মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। কাউকে কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। আমরা জাতিগতভাবে সংঘবদ্ধ, জাতিগতভাবে আমরা স্বাধীনতাকামী, সেটির জন্যই এই চব্বিশের বিজয় অর্জিত হয়েছে।
করতে; কিন্তু তারা জীবন দিলেও বাংলাদেশে বিভাজনের রাজনীতি আছে। বাংলাদেশে আমরা স্বৈরাচারিতা দেখেছি। আমরা আয়নাঘর দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের বোনদের ওপর হামলা দেখেছি, অসংখ্য মা-বাবার কান্না দেখেছি, বাবাদের আহাজারি দেখেছি, গুম-খুন দেখেছি। সত্যিকার অর্থে একাত্তর পূর্ণতা পায়নি। আমাদের গুরুজন যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই একমত ছিলেন বিধায় আমরা চব্বিশে স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে পেরেছি। একটা রাষ্ট্রে ১৬ বছর ধরে এমন শাসনব্যবস্থা ছিল, যেখানে যারাই সঠিক কথা বলেছে, তাদের বিভাজনের মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। কাউকে কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। আমরা জাতিগতভাবে সংঘবদ্ধ, জাতিগতভাবে আমরা স্বাধীনতাকামী, সেটির জন্যই এই চব্বিশের বিজয় অর্জিত হয়েছে।
আমরা বিভাজনের রাজনীতি, প্রতিহিংসার রাজনীতি চাই না। তবে বিভাজনের রাজনৈতিক প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। নির্বাচনে যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন, আগামীর বাংলাদেশে যেন আর কোনো স্বৈরাচার না আসে। কালের কণ্ঠ এই দেশ থেকে ফ্যাসিস্ট তাড়ানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বলতে চাই, সাবেক পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে যেভাবে কলম ধরেছে এই পত্রিকা, সেটি প্রশংসার দাবি রাখে। আমি মনে করি, সামনে থেকেই গণমাধ্যম হিসেবে কালের কণ্ঠ ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সত্যিকার অর্থে প্রতাপশালী ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে গণমাধ্যম যে দাঁড়াতে পারে, সেটি কালের কণ্ঠ দেখিয়েছে। নিজের সুবিধার জন্য কোনো স্বৈরাচারকে যেন প্রশ্রয় না দিই। বাংলাদেশের পরিচয়ে আমরা বড় হতে চাই।
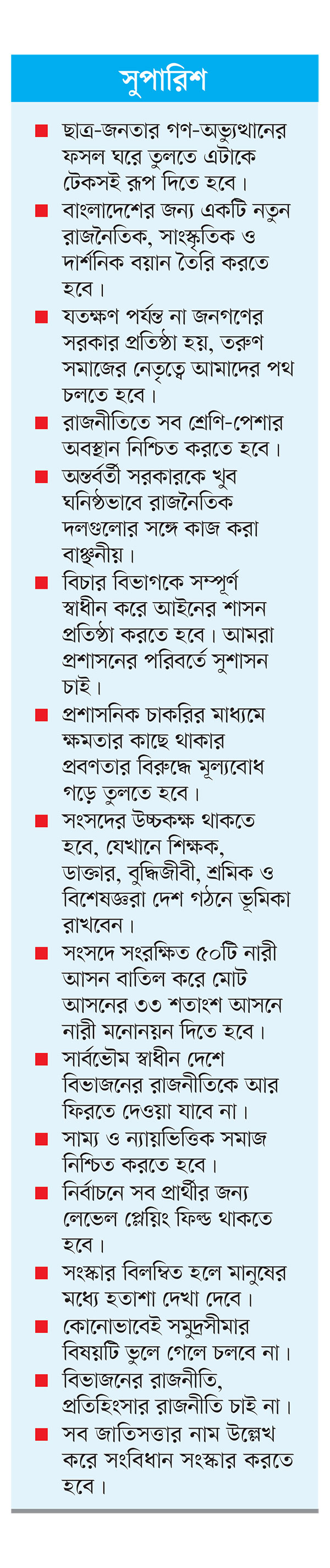 পাহাড়ে অশান্তির জন্য একমাত্র ভারতই দায়ী
পাহাড়ে অশান্তির জন্য একমাত্র ভারতই দায়ী
থোয়াই চিং মং শাক
পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত আমাদের দেশ নিয়ে প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে যে অশান্তি চলছে তার জন্য একমাত্র দায়ী হলো পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। তারা আমাদের আস্থা নষ্ট করছে। বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে না। ভারত বাংলাদেশে অস্থিতিশীল  পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। তাদের এই প্রপাগান্ডা রুখতে হলে ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে প্রচার করতে হবে। এমন বাংলাদেশ চাই, সেখানে ধর্মকে নিয়ে টানাটানি করা হবে না।
পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। তাদের এই প্রপাগান্ডা রুখতে হলে ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে প্রচার করতে হবে। এমন বাংলাদেশ চাই, সেখানে ধর্মকে নিয়ে টানাটানি করা হবে না।
সব জাতিসত্তার নাম উল্লেখ করে সংবিধান সংস্কার করতে হবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম থাকবে না। আমরা বাংলাদেশের প্রশ্নে সবাই এক, যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, ভেদাভেদ থাকবে না। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত আমাদের দেশ নিয়ে সংখ্যালঘু ইস্যু তৈরি করছে। অথচ আমরা সংখ্যালঘু বলতে চাই না। ভারত যেভাবে আমাদের নিয়ে প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছে, এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একজন মাওলানা হাজারবার যখন বলে বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে না, কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ ভাইকে আক্রমণ করা হচ্ছে না। তার হাজারবার আওয়াজের চেয়ে আমার এক আওয়াজ যথেষ্ট। বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে না।
ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিতে পারলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ইমেজ ভালো থাকবে। এমন বাংলাদেশ চাই, সেখানে ধর্মকে নিয়ে টানাটানি হবে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চাকর হতে শেখায়। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। যে সংস্কার চাকর হতে নয়, মালিক হতে শেখাবে। আমি শিখতে পারি না উদ্যোক্তা হতে, ভালো ডাক্তার হতে কিংবা অন্য পেশায় ভালো ও দক্ষ হতে। ২০২৩ সালে ঔষধ আইনের কারণে ছোট্ট উদ্যোক্তা চিকিৎসাক্ষেত্রে আসতে পারছেন না। এই আইনটির সংস্কার করা উচিত।
আমরা স্বপ্ন দেখছি একটি বৈষম্যহীন মানবিক বাংলাদেশের
কাদের গনি চৌধুরী
আমাদের জাতীয় জীবনে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে ‘বিজয় দিবস’ অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় দিন। সুদীর্ঘ ৯ মাসের মরণপণ লড়াইয়ে ৩০ লাখ শহীদের তাজা রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর আমরা প্রিয় মাতৃভূূমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম  হয়েছিলাম। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে যুগ যুগ ধরে এই দিনটি আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে আসছে। বাংলাদেশ আজ যেকোনো সময়ের তুলনায় ভিন্ন রকমের সময়ের সাক্ষী। ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা ফ্যাসিবাদের উত্খাত শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দেশের তরুণসমাজের আপসহীন বিচক্ষণতা ও ঈর্ষণীয় নেতৃত্বে লাখো জনতা রাজপথে নেমে নির্ভয়ে লড়াই করেছে, রক্ত দিয়েছে। মাত্র এক মাসে দীর্ঘ ১৫ বছর জাতির ঘাড়ে চেপে বসা স্বৈরাচারকে তারা তাড়িয়েছে। তাই ২০২৪ সালের বিজয় দিবস নতুন সংকল্প ও নতুন প্রত্যয় নিয়ে উদযাপিত হবে—এটাই সবার প্রত্যাশা।
হয়েছিলাম। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে যুগ যুগ ধরে এই দিনটি আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে আসছে। বাংলাদেশ আজ যেকোনো সময়ের তুলনায় ভিন্ন রকমের সময়ের সাক্ষী। ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা ফ্যাসিবাদের উত্খাত শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দেশের তরুণসমাজের আপসহীন বিচক্ষণতা ও ঈর্ষণীয় নেতৃত্বে লাখো জনতা রাজপথে নেমে নির্ভয়ে লড়াই করেছে, রক্ত দিয়েছে। মাত্র এক মাসে দীর্ঘ ১৫ বছর জাতির ঘাড়ে চেপে বসা স্বৈরাচারকে তারা তাড়িয়েছে। তাই ২০২৪ সালের বিজয় দিবস নতুন সংকল্প ও নতুন প্রত্যয় নিয়ে উদযাপিত হবে—এটাই সবার প্রত্যাশা।
’৭১, তারপর ’২৪। গত ৫ আগস্ট ২০২৪-এ দ্বিতীয় বিজয় অর্জনের পর আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব্বপূর্ণ সময় পার করছি। আমরা কি আবারও সেই গুমরাজ্যে ফিরে যাব, আবারও ভোটাধিকারহীন থাকব? নাকি একটা বৈষম্যহীন মানবিক ও আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশ গড়তে পারব? সেই বিষয়টি সুরাহার প্রসঙ্গ এসে গেছে। ১৯৭১ সালে আমরা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিজয়ের স্বাদ কি জনগণ পেয়েছে? আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন থাকল। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর ২০২৪ সালে এসে আমাদের গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার জন্য রক্ত দিতে হলো। আজ আমি বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সব শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের আত্মত্যাগে আমাদের এই বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জুলাই আন্দোলনে আহতদের, যাঁরা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা ফ্যাসিস্টদের তাড়াতে গিয়ে অঙ্গ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন।
গণ-অভ্যুত্থানের কাঙ্ক্ষিত বিজয়টাকে টেকসই রূপ দিতে হবে
হাসান হাফিজ
আপনারা জানেন, একটা নতুন তাৎপর্য এবং নতুন প্রেক্ষাপটে এবারের বিজয় দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি। বৈদেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে জাতির ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো চেপে বসা এবং গুম-খুনের ঘৃণ্য সংস্কৃতি চালু করা ফ্যাসিস্ট  শাসকের লাগাতার শোষণে প্রিয় মাতৃভূমির গণতন্ত্রই ধ্বংস হয়নি, গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধও একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। সীমাহীন লুটপাট আর ব্যাপক অর্থপাচার দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে একেবারে নড়বড়ে বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ছাত্র-জনতার অতুলনীয় ত্যাগের বিনিময়ে স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে জনগণের প্রত্যাশাও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। সংগত কারণেই এখন দেশব্যাপী নানামুখী সংস্কারের একটা ঢেউ চলছে। নানামুখী দাবিদাওয়াও প্রতিদিন উচ্চারিত হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়; একদিকে নির্বাচন, অন্যদিকে সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী ফ্যাসিবাদী দোসরদের ষড়যন্ত্র—সবই মোকাবেলা করতে হচ্ছে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে। এ ছাড়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে একটি কঠিন সময় পার করছে বাংলাদেশ।
শাসকের লাগাতার শোষণে প্রিয় মাতৃভূমির গণতন্ত্রই ধ্বংস হয়নি, গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধও একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। সীমাহীন লুটপাট আর ব্যাপক অর্থপাচার দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে একেবারে নড়বড়ে বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ছাত্র-জনতার অতুলনীয় ত্যাগের বিনিময়ে স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে জনগণের প্রত্যাশাও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। সংগত কারণেই এখন দেশব্যাপী নানামুখী সংস্কারের একটা ঢেউ চলছে। নানামুখী দাবিদাওয়াও প্রতিদিন উচ্চারিত হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়; একদিকে নির্বাচন, অন্যদিকে সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী ফ্যাসিবাদী দোসরদের ষড়যন্ত্র—সবই মোকাবেলা করতে হচ্ছে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে। এ ছাড়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে একটি কঠিন সময় পার করছে বাংলাদেশ।
কাঙ্ক্ষিত গণ-অভ্যুত্থানে নির্মম ফ্যাসিবাদের নিগড়ে বন্দি থাকা দেশবাসীর প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হয়েছে। এটাই এখন প্রিয় স্বদেশভূমির বাস্তবতা। বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে—অকুতোভয় ছাত্র-জনতার দুনিয়া কাঁপানো সফল গণ-অভ্যুত্থানের সেই ফসল যেকোনো মূল্যে আমাদের ঘরে তুলতে হবে। সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী হিসেবে এই গণ-অভ্যুত্থানের ফসলকে টেকসই রূপ দিতে হবে। গণদাবিকে এক পাশে ঠেলে দেওয়ার সুযোগও নেই। তাই গণ-অভ্যুত্থানের কাঙ্ক্ষিত বিজয়টাকে সংহত রূপ দেওয়ার কৌশল নির্ধারণ এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আগামীর বাংলাদেশে কী কী নতুন প্রত্যাশা হতে পারে, সেই লক্ষ্যে কালের কণ্ঠ ‘বিজয় দিবস : নতুন প্রত্যাশা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করেছে। আমাদের এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।
বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী আইন ও আমাদের প্রত্যাশা
দ্রুত আইন পাস ও সচেতনতা তৈরি করতে হবে

হিজড়া, দলিতসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সমাজে প্রতিনিয়ত বৈষম্য ও অবমাননার শিকার হচ্ছে। ২০২২ সালে বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। খসড়া আইনটির কিছু বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনাও রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ আইনটি পাস করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আশা করছি, এই সংসদেই প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইনটি পাস হবে
অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম
 বৈষম্যের বিরুদ্ধে চেতনা থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
বৈষম্যের বিরুদ্ধে চেতনা থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
তবে আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করতে চাই (আইনটির ব্যাপারে)। প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র, দলিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করছেন। বর্তমান সরকার ২০১৩ সালে কিন্তু হিজড়াদের নিয়ে নীতিমালা করেছে।
আমি কথা দিচ্ছি, সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদে দাঁড়িয়েও আমি এই আইনের কথা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য দেব। আজকের আলোচনায় প্রস্তাবিত আইনটির কিছু ঘাটতি ও সুপারিশ উঠে এসেছে। এগুলো নিয়েও কথা বলব। আপনারা বলেছেন, প্রস্তাবিত আইনটির নাম ‘বৈষম্যবিরোধী’ না হয়ে ‘বৈষম্য বাতিল (বিলোপ)’ হতে পারে। এ ছাড়া অপরাধের বিষয়টিও যুক্ত হওয়া উচিত। এসব ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে একেবারেই একমত। আশা করছি, এই সংসদেই প্রস্তাবিত আইনটি পাস হবে।
বৈষম্য পরিবার থেকে শুরু হয়ে রাষ্ট্রে পৌঁছে
ড. তানিয়া হক
 বৈষম্য পরিবার থেকে শুরু হয়ে রাষ্ট্রে গিয়ে পৌঁছে। শুধু আইন দিয়ে আমাদের জীবন চলে না। যেমন—কোনো প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের ওপর নারী শ্রমিক কাজ করলে সেই প্রতিষ্ঠানে দিবাযত্ন কেন্দ্র (ডে কেয়ার সেন্টার) তৈরি করতে মালিকপক্ষ বাধ্য। এটা আইনে রয়েছে। এখন কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি ২৫ জনের কম নারী থাকে তাহলে কী হবে? আরেকটি বিষয়, এক থেকে তিন বছরের শিশুর সঙ্গে নারীর সম্পৃক্ততা বেশি থাকে। কিন্তু শিশুর তিন থেকে পাঁচ বছর বা এর পরের সময়টাতে তো একজন পুরুষ লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে পারে। এই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা এখনো মানবিক সমাজ তৈরি করতে পারিনি। আইনের পাশাপাশি আমাদের কিছু বাজেট অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন, যা দিয়ে আইনের বিষয়ে নাগরিকদের জানাতে হবে। আইন জানাও নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব।
বৈষম্য পরিবার থেকে শুরু হয়ে রাষ্ট্রে গিয়ে পৌঁছে। শুধু আইন দিয়ে আমাদের জীবন চলে না। যেমন—কোনো প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের ওপর নারী শ্রমিক কাজ করলে সেই প্রতিষ্ঠানে দিবাযত্ন কেন্দ্র (ডে কেয়ার সেন্টার) তৈরি করতে মালিকপক্ষ বাধ্য। এটা আইনে রয়েছে। এখন কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি ২৫ জনের কম নারী থাকে তাহলে কী হবে? আরেকটি বিষয়, এক থেকে তিন বছরের শিশুর সঙ্গে নারীর সম্পৃক্ততা বেশি থাকে। কিন্তু শিশুর তিন থেকে পাঁচ বছর বা এর পরের সময়টাতে তো একজন পুরুষ লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে পারে। এই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা এখনো মানবিক সমাজ তৈরি করতে পারিনি। আইনের পাশাপাশি আমাদের কিছু বাজেট অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন, যা দিয়ে আইনের বিষয়ে নাগরিকদের জানাতে হবে। আইন জানাও নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব।
আইনে অপরাধ ও শাস্তির বিষয় না থাকলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে না
শামীম হায়দার পাটোয়ারী
 আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় নাগরিকদের সম-অধিকার ও সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইনটি যখন চূড়ান্ত খসড়া পর্যায়ের দিকে গেছে তখন আমি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলাম। ফলে এটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের করা খসড়াটি একদম যথার্থ ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, মানবাধিকার কমিশন হঠাৎ করে দৃশ্যের বাইরে চলে গেছে। তাদের আইনটিও চলে গেছে। আইনটির মনিটরিং কমিটিতে অবশ্যই মানবাধিকার কমিশনের থাকা উচিত। যেহেতু বিষয়টি মানবাধিকারসংক্রান্ত এবং মানবাধিকার কমিটি এ বিষয়ে সব সময় কাজ করে, তাদের প্রতিনিধি ছাড়া আমি মনে করি, মনিটরিং কমিটি পরিপূর্ণ হবে না। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে ‘মানবাধিকার কমিশন’ শব্দটিও নেই।
আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় নাগরিকদের সম-অধিকার ও সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইনটি যখন চূড়ান্ত খসড়া পর্যায়ের দিকে গেছে তখন আমি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলাম। ফলে এটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের করা খসড়াটি একদম যথার্থ ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, মানবাধিকার কমিশন হঠাৎ করে দৃশ্যের বাইরে চলে গেছে। তাদের আইনটিও চলে গেছে। আইনটির মনিটরিং কমিটিতে অবশ্যই মানবাধিকার কমিশনের থাকা উচিত। যেহেতু বিষয়টি মানবাধিকারসংক্রান্ত এবং মানবাধিকার কমিটি এ বিষয়ে সব সময় কাজ করে, তাদের প্রতিনিধি ছাড়া আমি মনে করি, মনিটরিং কমিটি পরিপূর্ণ হবে না। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে ‘মানবাধিকার কমিশন’ শব্দটিও নেই।
প্রস্তাবিত আইনটির নাম ‘বৈষম্যবিরোধী’ না হয়ে ‘বৈষম্য বিলোপ’ আইন হওয়া উচিত। এ ছাড়া আইনে ‘দলিত’দের সংজ্ঞা নেই, যেটি থাকা উচিত। যৌনকর্মীদের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আসা উচিত। খসড়া আইনে ‘অপরাধ’ নামক কোনো শব্দই নেই। এখানে মৃদু ভর্ত্সনা, ক্ষেত্রবিশেষে জরিমানা অথবা সাত দিনের জেল-জরিমানা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।
বৈষম্যের আসল সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়নি
অধ্যাপক ড. এস এম মাসুম বিল্লাহ
 আইনটি যখন উত্থাপন করা হয় তখন যদি আইনটি তৈরি করে ফেলা যেত তবে আজ এই ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হতো না। যেহেতু আগের সংসদের মেয়াদকালে আইনটি উত্থাপন করা হয়েছে এবং তখন পাস হয়নি, এখন আবার নতুন সংসদ হওয়ায় আইনটি নতুন করে উত্থাপন করতে হবে। অনেক সময় গেছে, তবে আমাদের মূল কথা হলো, এই আইন আমাদের লাগবেই। দুটি কারণে এই আইন লাগবে। একটি হলো আমরা জেনেভায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে অতিদ্রুত এই আইন করা হবে। আরেকটি হলো সরকারের যে ভাবমূর্তি রয়েছে তা টিকিয়ে রাখতে এই আইন করতে হবে। তবে প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইনে কিছু ঘাটতি আছে। আইনে আমরা বৈষম্যের আসল সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারিনি। আইনের শক্তি আসে আইন মানার ক্ষমতা থেকে। আমরা যত ভালো আইনই করি না কেন, আইন মানার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এই আইন কার্যকর হবে না। সুতরাং আমাদের সমাজ যদি প্রস্তুত না থাকে তাহলে যত বড় আইনই হোক, তা প্রভাব ফেলতে পারবে না।
আইনটি যখন উত্থাপন করা হয় তখন যদি আইনটি তৈরি করে ফেলা যেত তবে আজ এই ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হতো না। যেহেতু আগের সংসদের মেয়াদকালে আইনটি উত্থাপন করা হয়েছে এবং তখন পাস হয়নি, এখন আবার নতুন সংসদ হওয়ায় আইনটি নতুন করে উত্থাপন করতে হবে। অনেক সময় গেছে, তবে আমাদের মূল কথা হলো, এই আইন আমাদের লাগবেই। দুটি কারণে এই আইন লাগবে। একটি হলো আমরা জেনেভায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে অতিদ্রুত এই আইন করা হবে। আরেকটি হলো সরকারের যে ভাবমূর্তি রয়েছে তা টিকিয়ে রাখতে এই আইন করতে হবে। তবে প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইনে কিছু ঘাটতি আছে। আইনে আমরা বৈষম্যের আসল সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারিনি। আইনের শক্তি আসে আইন মানার ক্ষমতা থেকে। আমরা যত ভালো আইনই করি না কেন, আইন মানার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এই আইন কার্যকর হবে না। সুতরাং আমাদের সমাজ যদি প্রস্তুত না থাকে তাহলে যত বড় আইনই হোক, তা প্রভাব ফেলতে পারবে না।
কাটছাঁট করতে গিয়ে মূল জায়গা নষ্ট হয়েছে
রবিউল ইসলাম
 প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইনের খসড়া আমরা (মানবাধিকার কমিশন) যেভাবে দিয়েছিলাম, উত্থাপনের সময় তার কিছুই রাখা হয়নি। এই খসড়া কাটছাঁট করতে গিয়ে আইনের মূল জায়গাটাই নষ্ট হয়েছে। যে সংসদে যে আইন উত্থাপন করা হয় সে সংসদে যদি সেটি পাস না হয় তাহলে পরবর্তী সংসদে তা পুনরায় শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। অর্থাৎ বৈষম্যবিরোধী আইনটি আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে আমাদের। আরো হতাশার বিষয় হচ্ছে, মানবাধিকার কমিশন আইনটির শুরু থেকে খুবই নিবিড়ভাবে সুধীসমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। আমরা এই আইনের বিষয়ে সুধীসমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালা করেছি। এরপর আমরা এই আইনটি আবার আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করি, যাতে এটি আলোর মুখ দেখে। আমাদের আইনমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে অতিদ্রুত আইনটি পাস করা হবে। কিন্তু আইনটি এখনো সংসদে আলোর মুখ দেখেনি। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, কোনো জনগোষ্ঠীকে অবদমন করে বা পিছিয়ে রেখে এর কোনো সমাধান হবে না। এ বিষয়ে জনসচেতনতাও বাড়ানো প্রয়োজন।
প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইনের খসড়া আমরা (মানবাধিকার কমিশন) যেভাবে দিয়েছিলাম, উত্থাপনের সময় তার কিছুই রাখা হয়নি। এই খসড়া কাটছাঁট করতে গিয়ে আইনের মূল জায়গাটাই নষ্ট হয়েছে। যে সংসদে যে আইন উত্থাপন করা হয় সে সংসদে যদি সেটি পাস না হয় তাহলে পরবর্তী সংসদে তা পুনরায় শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। অর্থাৎ বৈষম্যবিরোধী আইনটি আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে আমাদের। আরো হতাশার বিষয় হচ্ছে, মানবাধিকার কমিশন আইনটির শুরু থেকে খুবই নিবিড়ভাবে সুধীসমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। আমরা এই আইনের বিষয়ে সুধীসমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালা করেছি। এরপর আমরা এই আইনটি আবার আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করি, যাতে এটি আলোর মুখ দেখে। আমাদের আইনমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে অতিদ্রুত আইনটি পাস করা হবে। কিন্তু আইনটি এখনো সংসদে আলোর মুখ দেখেনি। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, কোনো জনগোষ্ঠীকে অবদমন করে বা পিছিয়ে রেখে এর কোনো সমাধান হবে না। এ বিষয়ে জনসচেতনতাও বাড়ানো প্রয়োজন।
আইনে ক্ষতিপূরণ ও লঘু সাজা রাখতে হবে
মো. তাজুল ইসলাম
 আইনটির খসড়া তৈরির সময় আমরা সাজার বিষয় পর্যালোচনা করে দেখেছিলাম যে এই আইনে দুই ধরনের সাজা রাখতে হবে। একটি হচ্ছে ক্ষতিপূরণ, আরেকটি লঘু সাজা। কিন্তু ২০২২ সালের সংসদে বিল উত্থাপনের সময় আমরা এই দুটি সাজার কোনোটিই দেখতে পাইনি। আমি মনে করি, আইনে ক্ষতিপূরণ ও লঘু সাজা রাখতে হবে এবং আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে কতটুকু বৈষম্য হওয়ার পর ক্ষতিপূরণ ও লঘু সাজা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ছাড়া আইনে প্রতিকারের যে ব্যবস্থা দেওয়া আছে তাতে মনে হচ্ছে, একজন ভুক্তভোগীর পক্ষে ভালোভাবে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ প্রতিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে যে ভুক্তভোগী তিনটি কমিটি পার হওয়ার পর আদালতে মামলা করতে পারবে। অর্থাৎ ভুক্তভোগীর জন্য বিষয়টিকে অনেক কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন স্তরে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে তার কোনোটিতেই ভুক্তভোগীদের প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত আইনটি পাস করার জন্য একটি উদ্যোগ নেওয়া দরকার।
আইনটির খসড়া তৈরির সময় আমরা সাজার বিষয় পর্যালোচনা করে দেখেছিলাম যে এই আইনে দুই ধরনের সাজা রাখতে হবে। একটি হচ্ছে ক্ষতিপূরণ, আরেকটি লঘু সাজা। কিন্তু ২০২২ সালের সংসদে বিল উত্থাপনের সময় আমরা এই দুটি সাজার কোনোটিই দেখতে পাইনি। আমি মনে করি, আইনে ক্ষতিপূরণ ও লঘু সাজা রাখতে হবে এবং আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে কতটুকু বৈষম্য হওয়ার পর ক্ষতিপূরণ ও লঘু সাজা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ছাড়া আইনে প্রতিকারের যে ব্যবস্থা দেওয়া আছে তাতে মনে হচ্ছে, একজন ভুক্তভোগীর পক্ষে ভালোভাবে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ প্রতিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে যে ভুক্তভোগী তিনটি কমিটি পার হওয়ার পর আদালতে মামলা করতে পারবে। অর্থাৎ ভুক্তভোগীর জন্য বিষয়টিকে অনেক কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন স্তরে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে তার কোনোটিতেই ভুক্তভোগীদের প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত আইনটি পাস করার জন্য একটি উদ্যোগ নেওয়া দরকার।
৪ স্তর পেরিয়ে অধিকার আদায় কার্যত অসম্ভব
উত্তম কুমার ভক্ত
 প্রস্তাবিত আইনে দলিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ যদি বৈষম্যের শিকার হয়ে মামলা করতে চায় তাহলে চারটি স্তর পার হতে হবে তাদের। ৩০ দিন ধরে জেলা কমিটি, ৩০ দিন বিভাগীয় কমিটি ও ৪৫ দিন জাতীয় কমিটি ঘুরে তারপর মামলা করার সুযোগ পাবে তারা। এটি এই শ্রেণির মানুষের জন্য বড় ধরনের দীর্ঘসূত্রতা। ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী যেখানে এই আইন সম্পর্কেই জানে না সেখানে তাদের পক্ষে এভাবে চার স্তর পেরিয়ে অধিকার আদায় করা কার্যত অসম্ভব। আমরা এই আইনের বিষয়ে কিছু মানুষকে যুক্ত করতে পেরেছি। তবে আমরা বেশিসংখ্যক মানুষ এই আইনের সপক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়েছি। এই আইনের প্রথম খসড়া হয় ২০১৪ সালে। সেই খসড়ায় আমরা আইনটির নাম চেয়েছিলাম বৈষম্য বিলোপ আইন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ‘বৈষম্যবিরোধী’ নামটি প্রস্তাব করা হয়। খসড়া আইনটির আরেকটি দুর্বল দিক হলো ভুক্তভোগী সরাসরি আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না। এখন আমরা চাচ্ছি, অনতিবিলম্বে আইনটি তৈরি করা হোক। পরে এটি সংস্কার করা যাবে।
প্রস্তাবিত আইনে দলিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ যদি বৈষম্যের শিকার হয়ে মামলা করতে চায় তাহলে চারটি স্তর পার হতে হবে তাদের। ৩০ দিন ধরে জেলা কমিটি, ৩০ দিন বিভাগীয় কমিটি ও ৪৫ দিন জাতীয় কমিটি ঘুরে তারপর মামলা করার সুযোগ পাবে তারা। এটি এই শ্রেণির মানুষের জন্য বড় ধরনের দীর্ঘসূত্রতা। ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী যেখানে এই আইন সম্পর্কেই জানে না সেখানে তাদের পক্ষে এভাবে চার স্তর পেরিয়ে অধিকার আদায় করা কার্যত অসম্ভব। আমরা এই আইনের বিষয়ে কিছু মানুষকে যুক্ত করতে পেরেছি। তবে আমরা বেশিসংখ্যক মানুষ এই আইনের সপক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়েছি। এই আইনের প্রথম খসড়া হয় ২০১৪ সালে। সেই খসড়ায় আমরা আইনটির নাম চেয়েছিলাম বৈষম্য বিলোপ আইন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ‘বৈষম্যবিরোধী’ নামটি প্রস্তাব করা হয়। খসড়া আইনটির আরেকটি দুর্বল দিক হলো ভুক্তভোগী সরাসরি আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না। এখন আমরা চাচ্ছি, অনতিবিলম্বে আইনটি তৈরি করা হোক। পরে এটি সংস্কার করা যাবে।
সামাজিক সচেতনতার আন্দোলন চালাতে হবে
রুমা সুলতানা
 বৈষম্য দূর করতে আইনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আইন দিয়ে সব কিছুর সমাধান হবে না। আইনে বলা আছে, একজন ভুক্তভোগী যদি সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রতিকার না পায় তাহলে সে আদালতে যেতে পারবে। একজন ব্যক্তি যখন বৈষম্যের শিকার হয় তখন সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই মানসিক বিপর্যস্ততা নিয়ে সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রতিকার না পেলে তখন আদালতের ওপর ভুক্তভোগীর আস্থা থাকবে না। খসড়া আইনে একটি ভালো জিনিস রয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকে বৈষম্যমূলক কাজের ধারণা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা ঠিক যে আইন হলে রাতারাতি পরিবর্তন হবে না। তবে আইনটি দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের অংশ হিসেবে কাজ করবে। খসড়া আইনের আরেকটি প্রশংসনীয় বিষয় হলো এখানে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টি একটি ধারায় রয়েছে।
বৈষম্য দূর করতে আইনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আইন দিয়ে সব কিছুর সমাধান হবে না। আইনে বলা আছে, একজন ভুক্তভোগী যদি সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রতিকার না পায় তাহলে সে আদালতে যেতে পারবে। একজন ব্যক্তি যখন বৈষম্যের শিকার হয় তখন সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই মানসিক বিপর্যস্ততা নিয়ে সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রতিকার না পেলে তখন আদালতের ওপর ভুক্তভোগীর আস্থা থাকবে না। খসড়া আইনে একটি ভালো জিনিস রয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকে বৈষম্যমূলক কাজের ধারণা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা ঠিক যে আইন হলে রাতারাতি পরিবর্তন হবে না। তবে আইনটি দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের অংশ হিসেবে কাজ করবে। খসড়া আইনের আরেকটি প্রশংসনীয় বিষয় হলো এখানে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টি একটি ধারায় রয়েছে।
আইন হলে দলিতরা বৈষম্য থেকে মুক্তি পাবে
মনি রানী দাস
 বৈষম্য বিলোপ আইন নিয়ে ২০১২-১৩ সাল থেকে আমরা কাজ শুরু করি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত এটি নিয়ে আমরা কাজ করেছি। ধীরে ধীরে এটি ২০২২ সালে সংসদ পর্যন্ত যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি আইন হিসেবে পাস হয়নি। আজকে এই আইন আমাদের বিশেষ দরকার। আইনটি হলে দলিত জনগোষ্ঠী যেখানে যেখানে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সেখানে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে। ওরা স্কুলে গেলেও ওদের দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করানো হয়। ওদের খাবার হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। জয়পুরহাটে আমাদের একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন বাবু রবি দাস নামে। তিনি একজন অ্যাডভোকেট হয়েও অন্য অ্যাডভোকেটদের পাশে বসে খেতে পারতেন না কখনো।
বৈষম্য বিলোপ আইন নিয়ে ২০১২-১৩ সাল থেকে আমরা কাজ শুরু করি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত এটি নিয়ে আমরা কাজ করেছি। ধীরে ধীরে এটি ২০২২ সালে সংসদ পর্যন্ত যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি আইন হিসেবে পাস হয়নি। আজকে এই আইন আমাদের বিশেষ দরকার। আইনটি হলে দলিত জনগোষ্ঠী যেখানে যেখানে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সেখানে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে। ওরা স্কুলে গেলেও ওদের দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করানো হয়। ওদের খাবার হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। জয়পুরহাটে আমাদের একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন বাবু রবি দাস নামে। তিনি একজন অ্যাডভোকেট হয়েও অন্য অ্যাডভোকেটদের পাশে বসে খেতে পারতেন না কখনো।
১৯৭১ সালে দেশটা যে জায়গায় স্বাধীন হয়েছে বৈষম্য আইন না থাকার কারণে দলিত জনগোষ্ঠী আজও সেই জায়গায়ই রয়ে গেছে। স্বাধীনতা দিবসে তাদের বলা হয়, আজ তোমার বাবা আসেনি, তুমি কিন্তু বাথরুম পরিষ্কার করবে। আমরা মনে করি না, আমাদের কোনো নিরাপত্তা আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী দলিতবান্ধব। তিনি দলিতদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। আজকে আমাদের জনগোষ্ঠী ভাতা পাচ্ছে। আমাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। এখন আমাদের চাওয়া, অতি শিগগিরই যাতে এই আইন পাস হয়।
হিজড়াদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেড়ে চলছে
রানী চৌধুরী
 আমি একজন হিজড়া। আমার পরিচয় দিতে সব সময় স্বাচ্ছন্দ্য ও গর্ববোধ করি। সংবিধানে কোথাও আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে কিছু বলা নেই। নারীদের জন্য নারী সুরক্ষা আইন, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন রয়েছে। কিন্তু আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কোনো আইন নেই। এমনকি আমাদের জনগোষ্ঠী যে সম্পত্তি পাবে তারও কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা বা আইন নেই। আমরা কোথায় যাব?
আমি একজন হিজড়া। আমার পরিচয় দিতে সব সময় স্বাচ্ছন্দ্য ও গর্ববোধ করি। সংবিধানে কোথাও আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে কিছু বলা নেই। নারীদের জন্য নারী সুরক্ষা আইন, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন রয়েছে। কিন্তু আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কোনো আইন নেই। এমনকি আমাদের জনগোষ্ঠী যে সম্পত্তি পাবে তারও কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা বা আইন নেই। আমরা কোথায় যাব?
হিজড়াদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেড়ে চলছে। কিছুদিন আগে একজন হিজড়া আত্মহত্যা করেছে। কারণ সে যে বাসায় ভাড়া থাকত সেখান থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। হিজড়ারা কোথাও বাসা ভাড়া পায় না। স্কুল থেকে হিজড়া শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু স্বীকৃতির পর আইন হিসেবে আর কিছু আসেনি। সুতরাং আমি চাইব, এই আইন (বৈষম্যবিরোধী আইন) যাতে খুব তাড়াতাড়ি সংসদে পাস হয়। আরেকটি বিষয়, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের জন্যও যেন একটা সোজা রাস্তা তৈরি হয় সে ব্যাপারেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
স্থানীয় সরকারকে ভূমিকা পালন করতে হবে
নুজহাত জাবিন
 আমাদের কমিউনিটিগুলোর মধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিষয়ে যে সাধারণ চিন্তা রয়েছে তা পুরোপুরি নেতিবাচক। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, দলিতসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও সমাজের সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে এবং এই জনগোষ্ঠীকে সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে দিতে হবে যেন তারা সহজেই তা নিতে পারে। এখানে স্থানীয় সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা এই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে তাদের সেবাটা পৌঁছে দেবেন। শুধু সেবা পৌঁছালেই হবে না, সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি এই জনগোষ্ঠীর মানুষকে জানাতে হবে যে তারা এই সেবা পাওয়ার অধিকার রাখে। আমরা ক্রিশ্চিয়ান এইডের পক্ষ থেকে সব সময় চেষ্টা করি যে এই দলিত শ্রেণির জনগোষ্ঠীর মানুষকে কিভাবে সামনের সারিতে আনা যায়, তাদের অধিকার সম্পর্কে কিভাবে সচেতনতা তৈরি করা যায়।
আমাদের কমিউনিটিগুলোর মধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিষয়ে যে সাধারণ চিন্তা রয়েছে তা পুরোপুরি নেতিবাচক। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, দলিতসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও সমাজের সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে এবং এই জনগোষ্ঠীকে সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে দিতে হবে যেন তারা সহজেই তা নিতে পারে। এখানে স্থানীয় সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা এই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে তাদের সেবাটা পৌঁছে দেবেন। শুধু সেবা পৌঁছালেই হবে না, সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি এই জনগোষ্ঠীর মানুষকে জানাতে হবে যে তারা এই সেবা পাওয়ার অধিকার রাখে। আমরা ক্রিশ্চিয়ান এইডের পক্ষ থেকে সব সময় চেষ্টা করি যে এই দলিত শ্রেণির জনগোষ্ঠীর মানুষকে কিভাবে সামনের সারিতে আনা যায়, তাদের অধিকার সম্পর্কে কিভাবে সচেতনতা তৈরি করা যায়।
আইনটি দলিত জনগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে
নাদিরা পারভীন
 প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইন মানুষের চিন্তার পরিবর্তন করতে পারবে না। এর জন্য সামাজিক আন্দোলন কর্মসূচি করতে হবে। তবে আইনটি হলে তা দলিত জনগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। এই শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যারা বৈষম্য করবে তাদের অন্তত বলা যাবে যে তুমি কারো অধিকার হরণ করলে তোমাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হবে। আইন যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে আইনের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। আমাদের সংবিধানে বলা আছে, কোনো রকম পুনর্বাসন ছাড়া দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষকে উচ্ছেদ করা যাবে না। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় এই শ্রেণির মানুষকে উচ্ছেদ করতে দেখি। এ থেকে বোঝা যায়, আইন থাকলেই সব হয় না। তবে আইন থাকলে এটাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে কাজ করা যায়।
প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইন মানুষের চিন্তার পরিবর্তন করতে পারবে না। এর জন্য সামাজিক আন্দোলন কর্মসূচি করতে হবে। তবে আইনটি হলে তা দলিত জনগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। এই শ্রেণির মানুষের সঙ্গে যারা বৈষম্য করবে তাদের অন্তত বলা যাবে যে তুমি কারো অধিকার হরণ করলে তোমাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হবে। আইন যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে আইনের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। আমাদের সংবিধানে বলা আছে, কোনো রকম পুনর্বাসন ছাড়া দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষকে উচ্ছেদ করা যাবে না। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় এই শ্রেণির মানুষকে উচ্ছেদ করতে দেখি। এ থেকে বোঝা যায়, আইন থাকলেই সব হয় না। তবে আইন থাকলে এটাকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে কাজ করা যায়।
খসড়া আইনের দুর্বলতাগুলো ঠিক করতে হবে
মাহেনুর আলম চৌধুরী
 নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন বেসরকারি-স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবির ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে আইন কমিশন বৈষম্য বিলোপ আইনের প্রথম খসড়া তৈরি করে। ২০১৮ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খসড়া আইনটি পরিমার্জন করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রেরণ করে। ২০২২ সালে বৈষম্যবিরোধী আইন-২০২২ বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়, যা পরে সংসদীয় কমিটিতে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পাঠানো হয়। পরে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।
নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন বেসরকারি-স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবির ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে আইন কমিশন বৈষম্য বিলোপ আইনের প্রথম খসড়া তৈরি করে। ২০১৮ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খসড়া আইনটি পরিমার্জন করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রেরণ করে। ২০২২ সালে বৈষম্যবিরোধী আইন-২০২২ বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়, যা পরে সংসদীয় কমিটিতে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য পাঠানো হয়। পরে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।
খসড়া আইনে বেশ কিছু ঘাটতি ও দুর্বলতা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু সুপারিশ রয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটির নাম ‘ বৈষম্য বিলোপ আইন’ করা, বৈষম্যগুলোকে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করতে হবে। বৈষম্যমূলক কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করা এবং শাস্তির বিধান রাখতে হবে। খসড়ায় অভিযোগের কথা বলা থাকলেও প্রতিকার কী হবে তা বলা নেই। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।
মানুষ সচেতন না হলে দেশ বদলায় না
ইমদাদুল হক মিলন
 আসলে বৈষম্য শুরু হয় কোথা থেকে? বৈষম্য তো শুরু হয় আমাদের ঘর থেকে, প্রতিদিনকার জীবন থেকে। আমরা যখন ঘরে বসে খাই, আমাদের বাড়িতে যে ছেলে বা মেয়েটি কাজ করে তাকে কখনোই আমরা আমাদের খাওয়ার টেবিলে বসতে অনুমতি দিই না। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা বৈষম্য তৈরি করেছি। মানুষ সচেতন না হলে দেশ বদলায় না, পৃথিবী বদলায় না। তাই মানুষের সচেতনতার দরকার। এই সচেতনতা আমরা তৈরি করতে চাই বলেই আজকের এই আয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের জায়গা থেকে বৈষম্য দূরীকরণের কাজ শুরু করা উচিত; মানুষকে সচেতন করা উচিত। দৈনিক কালের কণ্ঠ’র মধ্য দিয়ে আজকের আলোচনার বিষয়গুলো আমরা জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেব।
আসলে বৈষম্য শুরু হয় কোথা থেকে? বৈষম্য তো শুরু হয় আমাদের ঘর থেকে, প্রতিদিনকার জীবন থেকে। আমরা যখন ঘরে বসে খাই, আমাদের বাড়িতে যে ছেলে বা মেয়েটি কাজ করে তাকে কখনোই আমরা আমাদের খাওয়ার টেবিলে বসতে অনুমতি দিই না। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা বৈষম্য তৈরি করেছি। মানুষ সচেতন না হলে দেশ বদলায় না, পৃথিবী বদলায় না। তাই মানুষের সচেতনতার দরকার। এই সচেতনতা আমরা তৈরি করতে চাই বলেই আজকের এই আয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের জায়গা থেকে বৈষম্য দূরীকরণের কাজ শুরু করা উচিত; মানুষকে সচেতন করা উচিত। দৈনিক কালের কণ্ঠ’র মধ্য দিয়ে আজকের আলোচনার বিষয়গুলো আমরা জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেব।
সবারই ন্যায়বিচার, সাম্য ও শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে
আলী হাবিব
 বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে সমতা, সমান সুযোগ ও বৈষম্যহীনতার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতা ঠিক সে রকম কি না, তা নিয়ে আমাদের একটু সন্দেহ থেকেই যায়। ২০২১ সালে ক্রিশ্চিয়ান এইডের করা এক জরিপে দেখা গেছে, মানুষ মনে করে, হিজড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাকরি বা কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। এই জনগোষ্ঠীগুলোর মানুষের সঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারেও অনেকের আপত্তি আছে।
বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে সমতা, সমান সুযোগ ও বৈষম্যহীনতার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতা ঠিক সে রকম কি না, তা নিয়ে আমাদের একটু সন্দেহ থেকেই যায়। ২০২১ সালে ক্রিশ্চিয়ান এইডের করা এক জরিপে দেখা গেছে, মানুষ মনে করে, হিজড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাকরি বা কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। এই জনগোষ্ঠীগুলোর মানুষের সঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারেও অনেকের আপত্তি আছে।
আমাদের আলোচকদের বক্তব্যেও উঠে এসেছে, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার বাইরেও জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নানা পরিচয়ের ভিত্তিতে অনেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সমাজের অনেকে খায় না, বসে না। তাদের চাকরি দেওয়া হয় না, বাচ্চাদের স্কুলে পর্যন্ত ভর্তি করানো হয় না। এই মানুষগুলোরও সমাজে ন্যায়বিচার, সাম্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, সরকার অবিলম্বে একটি বিল আনবে এবং বৈষম্যবিরোধী আইন পাস করবে।
![]()
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
পিএইচডি প্রদানে চ্যালেঞ্জ যোগ্য শিক্ষক

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৫টি। এর মধ্যে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় মানদণ্ড বজায় রেখে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়েও তারা এগিয়ে যাচ্ছে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও পিএইচডি ডিগ্রির ব্যবস্থাটা থাকুক
ইমদাদুল হক মিলন
 যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটি হলো, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি : সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। এই পত্রিকাটির বয়স হলো ১৫ বছর। পত্রিকাটির শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা গোলটেবিলের ব্যবস্থা করে থাকি। সেখানে সুধীজনরা ও সমাজের নীতিনির্ধারকরা উপস্থিত থাকেন এবং আলোচনা করেন।
যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটি হলো, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি : সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। এই পত্রিকাটির বয়স হলো ১৫ বছর। পত্রিকাটির শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা গোলটেবিলের ব্যবস্থা করে থাকি। সেখানে সুধীজনরা ও সমাজের নীতিনির্ধারকরা উপস্থিত থাকেন এবং আলোচনা করেন।
বিশিষ্টজনদের আলোচনার মধ্য দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে আলোচকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। সেগুলো আমরা আমাদের পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরব। যাতে দেশের মানুষ, শিক্ষক, ছাত্রসমাজ ও চিন্তাশীল মানুষ যেন বুঝতে পারে যে আমরা কেন চাই আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও পিএইচডি ডিগ্রির ব্যবস্থাটা থাকুক।
ডিগ্রির সঙ্গে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার রাখতে হবে
অধ্যাপক ড. আব্দুর রব
 বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে টেকনোলজিতে আমরা পিছিয়ে আছি, বিশেষ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা অনেক পিছিয়ে। এআই প্রযুক্তির ব্যবহার কিভাবে পিএইচডির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে টেকনোলজিতে আমরা পিছিয়ে আছি, বিশেষ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা অনেক পিছিয়ে। এআই প্রযুক্তির ব্যবহার কিভাবে পিএইচডির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের  শিক্ষার্থীরা যেন তাদের কাজের সুবিধার্থে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আলাদা একটি কোর্স রাখা যেতে পারে। ইউজিসি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির অনুমোদন দেওয়া হবে। ফলে এখন এই ডিগ্রির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে, যে গবেষণালব্ধ ফল সমাজ বা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার উপযোগী। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ল্যাবসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যেন তা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমিত না থেকে দেশের ইন্ডাস্ট্রি পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্ডাস্ট্রি থেকে যাঁরা পিএইচডি করতে অসবেন, আশা করছি তাঁদের এই ডিগ্রি বেশি কার্যকর হবে। কোন পর্যায়ের শিক্ষার্থী পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তি হবেন, তার ওপর নির্ভর করে কোর্সসংখ্যা রাখা যেতে পারে। মাস্টার্স করে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য তুলনামূলক কম কোর্সের প্রয়োজন হবে। তবে স্নাতকোত্তর শেষ করে পিএইচডি করতে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য এই কোর্সসংখ্যা বাড়তে পারে। এই ডিগ্রি অর্জনে প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগের যেসব শিক্ষক সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের এখন থেকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেতে পারে। ইউজিসি যে নীতিমালা তৈরি করছে, তা যথাযথ পালন না করলে ডিগ্রি দেওয়ার অনুমতি বন্ধ করা যেতে পারে। ইউজিসির পাশাপাশি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এই শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে।
শিক্ষার্থীরা যেন তাদের কাজের সুবিধার্থে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আলাদা একটি কোর্স রাখা যেতে পারে। ইউজিসি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির অনুমোদন দেওয়া হবে। ফলে এখন এই ডিগ্রির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে, যে গবেষণালব্ধ ফল সমাজ বা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার উপযোগী। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ল্যাবসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যেন তা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমিত না থেকে দেশের ইন্ডাস্ট্রি পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্ডাস্ট্রি থেকে যাঁরা পিএইচডি করতে অসবেন, আশা করছি তাঁদের এই ডিগ্রি বেশি কার্যকর হবে। কোন পর্যায়ের শিক্ষার্থী পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তি হবেন, তার ওপর নির্ভর করে কোর্সসংখ্যা রাখা যেতে পারে। মাস্টার্স করে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য তুলনামূলক কম কোর্সের প্রয়োজন হবে। তবে স্নাতকোত্তর শেষ করে পিএইচডি করতে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য এই কোর্সসংখ্যা বাড়তে পারে। এই ডিগ্রি অর্জনে প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগের যেসব শিক্ষক সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের এখন থেকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যেতে পারে। ইউজিসি যে নীতিমালা তৈরি করছে, তা যথাযথ পালন না করলে ডিগ্রি দেওয়ার অনুমতি বন্ধ করা যেতে পারে। ইউজিসির পাশাপাশি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এই শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে।
নীতিমালায় আলংকারিক ডিগ্রি গ্রহণকে নিরুৎসাহ করব
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ
 আমরা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান এবং এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে চাই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে একটি শক্ত নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে। যেন প্রতিটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) হস্তক্ষেপ করতে না হয়। নীতিমালার মধ্য দিয়েই আমরা আলংকারিক ডিগ্রি গ্রহণকে নিরুৎসাহ করব। পিএইচডি ডিগ্রি কেন নেবেন এবং তা রাষ্ট্র, সমাজ ও ইন্ডাস্ট্রিতে ভূমিকা রাখবে কি না তা বিবেচনা করা হবে। পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে প্রপোজাল তৈরি করতে বলা হবে। আগের পাবলিকেশন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ক আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। এই ডিগ্রি পরবর্তী সময়ে কিভাবে কাজে লাগাবেন তাও দেখা হবে। ডিগ্রি নিয়ে নামের আগে শুধু ‘ড.’ বসাবেন, তা হবে না। নীতিমালা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে, যেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি বিক্রির দোকানে পরিণত না হয়। গবেষণা, ল্যাব সুবিধা ও প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষকসহ সব বিষয় নিশ্চিত করেই প্রতিষ্ঠান বা বিভাগভিত্তিক ডিগ্রি প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে। যদি দেখা যায়, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগ থেকে দুই-তিনজন ডিগ্রি নিয়েছেন, তবে পরবর্তী সময়ে এই ডিগ্রি দেশ ও সমাজের কোনো কাজে আসেনি, তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের ডিগ্রি দেওয়ার অনুমোদন বাতিলেরও সুপারিশ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা এমন সব সুপারিশ করেছেন। ইউজিসির কমিটি তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আরো বৈঠক করবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আইন অমান্য করবে, বরাবরের মতো ইউজিসি তাদের বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। ডিগ্রির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে প্রথম বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি সেমিস্টার শেষে শিক্ষার্থীদের যাচাই করার বিষয়েও পরামর্শ এসেছে। কোনো শিক্ষার্থী একটি সেমিস্টারে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেখাতে না পারলে পরবর্তী ধাপে যেতে পারবে না। এই যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারভাইজারের পাশাপাশি একটি কমিটি বা উপদেষ্টা প্যানেল থাকা আবশ্যক। এ ছাড়া ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশ থেকে পরীক্ষক রাখা যেতে পারে। সুপারভাইজারদের যোগ্যতা ও দক্ষতার বিষয়ে নির্দেশনা থাকবে, অনলাইনে পিএইচডি করা শিক্ষকরা সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োজিত হতে পারবেন না।
আমরা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান এবং এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে চাই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে একটি শক্ত নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে। যেন প্রতিটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) হস্তক্ষেপ করতে না হয়। নীতিমালার মধ্য দিয়েই আমরা আলংকারিক ডিগ্রি গ্রহণকে নিরুৎসাহ করব। পিএইচডি ডিগ্রি কেন নেবেন এবং তা রাষ্ট্র, সমাজ ও ইন্ডাস্ট্রিতে ভূমিকা রাখবে কি না তা বিবেচনা করা হবে। পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে প্রপোজাল তৈরি করতে বলা হবে। আগের পাবলিকেশন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ক আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। এই ডিগ্রি পরবর্তী সময়ে কিভাবে কাজে লাগাবেন তাও দেখা হবে। ডিগ্রি নিয়ে নামের আগে শুধু ‘ড.’ বসাবেন, তা হবে না। নীতিমালা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে, যেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডি বিক্রির দোকানে পরিণত না হয়। গবেষণা, ল্যাব সুবিধা ও প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষকসহ সব বিষয় নিশ্চিত করেই প্রতিষ্ঠান বা বিভাগভিত্তিক ডিগ্রি প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে। যদি দেখা যায়, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগ থেকে দুই-তিনজন ডিগ্রি নিয়েছেন, তবে পরবর্তী সময়ে এই ডিগ্রি দেশ ও সমাজের কোনো কাজে আসেনি, তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের ডিগ্রি দেওয়ার অনুমোদন বাতিলেরও সুপারিশ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা এমন সব সুপারিশ করেছেন। ইউজিসির কমিটি তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আরো বৈঠক করবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আইন অমান্য করবে, বরাবরের মতো ইউজিসি তাদের বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। ডিগ্রির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে প্রথম বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি সেমিস্টার শেষে শিক্ষার্থীদের যাচাই করার বিষয়েও পরামর্শ এসেছে। কোনো শিক্ষার্থী একটি সেমিস্টারে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেখাতে না পারলে পরবর্তী ধাপে যেতে পারবে না। এই যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারভাইজারের পাশাপাশি একটি কমিটি বা উপদেষ্টা প্যানেল থাকা আবশ্যক। এ ছাড়া ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশ থেকে পরীক্ষক রাখা যেতে পারে। সুপারভাইজারদের যোগ্যতা ও দক্ষতার বিষয়ে নির্দেশনা থাকবে, অনলাইনে পিএইচডি করা শিক্ষকরা সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োজিত হতে পারবেন না।
মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে পিএইচডি অপরিহার্য
অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম মিয়া
 আমরা সব সময় বলে থাকি, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানসম্মত না। মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিএইচডি শিক্ষার্থী না থাকলে সেই মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব না। পিএইচডি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র্যাংকিং করা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ডিগ্রি দেওয়ার সুবিধা না থাকায় সেখানে আমরা পিছিয়ে পড়ি। পিএইচডিধারী শিক্ষকদের সংখ্যাও খুব কম। আমাদের শিক্ষকরা পিএইচডি করতে বিদেশ যান, যার বেশির ভাগই আর ফিরে আসেন না, এটাই বাস্তবতা। ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদেরও এই ডিগ্রি প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ের র্যাংকিংগুলোতে দেখা যায়, দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র্যাংকিংয়ে খুব কাছাকাছি রয়েছে। এ ছাড়া দেশে সমস্যার তো অভাব নেই। সেই সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে। বাইরের বিশেষজ্ঞরা আমাদের সংস্কৃতি ও সমস্যার সঙ্গে অভ্যস্ত নন। ফলে তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া প্যাকেট (গবেষণা) আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না। আমরা যদি পিএইচডিগুলো, বিশেষ করে গবেষণা আমাদের এখানে করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমাদের দারুণ সম্ভাবনা আসবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় প্রতিকূলতা মানসম্মত শিক্ষক। একজন পিএইচডিধারী দেশে ফিরলে সবাই তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অন্যদিকে রয়েছে তহবিল সংকট। আমরা যদি বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কাছে যেতে পারি, তাদের বড় সমস্যাগুলো গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দিতে পারি, তাহলে এই তহবিল সংকট নিরসন সম্ভব। আমরা যদি মানসম্মত পিএইচডি দিতে পারি, তাহলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কাছে আসবে, আমাদের অর্থায়ন করবে। এর জন্য মানসম্মত শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। কিভাবে ছাঁকনি দিয়ে মানসম্মত শিক্ষার্থী বের করা যায়, সেটা নীতিমালায় থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো গবেষণা করছে কি না, সেটিও মনিটর করতে হবে। তাহলে আমরা মানসম্মত পিএইচডি পাব।
আমরা সব সময় বলে থাকি, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানসম্মত না। মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিএইচডি শিক্ষার্থী না থাকলে সেই মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব না। পিএইচডি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র্যাংকিং করা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ডিগ্রি দেওয়ার সুবিধা না থাকায় সেখানে আমরা পিছিয়ে পড়ি। পিএইচডিধারী শিক্ষকদের সংখ্যাও খুব কম। আমাদের শিক্ষকরা পিএইচডি করতে বিদেশ যান, যার বেশির ভাগই আর ফিরে আসেন না, এটাই বাস্তবতা। ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদেরও এই ডিগ্রি প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ের র্যাংকিংগুলোতে দেখা যায়, দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র্যাংকিংয়ে খুব কাছাকাছি রয়েছে। এ ছাড়া দেশে সমস্যার তো অভাব নেই। সেই সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে। বাইরের বিশেষজ্ঞরা আমাদের সংস্কৃতি ও সমস্যার সঙ্গে অভ্যস্ত নন। ফলে তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া প্যাকেট (গবেষণা) আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না। আমরা যদি পিএইচডিগুলো, বিশেষ করে গবেষণা আমাদের এখানে করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমাদের দারুণ সম্ভাবনা আসবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় প্রতিকূলতা মানসম্মত শিক্ষক। একজন পিএইচডিধারী দেশে ফিরলে সবাই তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অন্যদিকে রয়েছে তহবিল সংকট। আমরা যদি বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কাছে যেতে পারি, তাদের বড় সমস্যাগুলো গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দিতে পারি, তাহলে এই তহবিল সংকট নিরসন সম্ভব। আমরা যদি মানসম্মত পিএইচডি দিতে পারি, তাহলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কাছে আসবে, আমাদের অর্থায়ন করবে। এর জন্য মানসম্মত শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। কিভাবে ছাঁকনি দিয়ে মানসম্মত শিক্ষার্থী বের করা যায়, সেটা নীতিমালায় থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো গবেষণা করছে কি না, সেটিও মনিটর করতে হবে। তাহলে আমরা মানসম্মত পিএইচডি পাব।
পেশাজীবনে ডিগ্রির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহফুজুল আজিজ
 পিএইচডি ডিগ্রি কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষার বিষয় নয়, এটি আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে। এটি কারা করবেন এবং কেন করবেন? প্রতিটি জিনিসের তো একটি উদ্দেশ্য থাকে। আমি একটি জিনিস করলাম, সেটির সুফল, ফসলটা ঘরে তুলতে পারলাম না, দেশ, জাতি বা প্রতিষ্ঠান লাভবান হলো না।
পিএইচডি ডিগ্রি কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষার বিষয় নয়, এটি আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে। এটি কারা করবেন এবং কেন করবেন? প্রতিটি জিনিসের তো একটি উদ্দেশ্য থাকে। আমি একটি জিনিস করলাম, সেটির সুফল, ফসলটা ঘরে তুলতে পারলাম না, দেশ, জাতি বা প্রতিষ্ঠান লাভবান হলো না।  শুধু নামের আগে ‘ড.’ বসল। এ ধরনের পিএইচডি যেন আমরা উৎসাহিত না করি। কোনো ব্যক্তির পিএইচডি করার কারণটা আগে উদঘাটন করা দরকার। পাশাপাশি ওই ব্যক্তির উৎসাহ, মেধা, দক্ষতা ও সক্ষমতা আছে কি না সেটাও দেখা দরকার। সেই সঙ্গে পেশাজীবনে এর ব্যবহার হবে কি না সেটাও দেখা দরকার। এই বিষয়গুলো যাচাই করতে একজন শিক্ষার্থী ভর্তির আগে তাকে অবশ্যই ‘প্রপোজাল’ লিখতে দিতে হবে। এর মাধ্যমে তার দক্ষতার বিষয়টির পাশাপাশি উদ্দেশ্যও জানা যাবে। আগে শিক্ষাজীবনে দু-একটি পাবলিকেশন থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। পিএইচডিতে ভর্তির পরও নিয়মিত তদারকির প্রয়োজন রয়েছে। মানসম্মত পিএইচডির জন্য ছয় মাস অন্তর অন্তর রিভিউ করতে হবে। তাদের দিয়ে অন্তত দুটি পাবলিকেশন করাতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির সম্ভাবনা অনেক। কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাবলিকেশনের সংখ্যা ও মান দিন দিন বাড়ছে। এখন আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে, যাঁরা গবেষণা করে জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবেন। কারণ আজকের যুগে উদ্ভাবন ছাড়া কোনো জাতি উন্নত হতে পারবে না। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। পিএইচডি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাপোর্ট দিতে হবে, যাতে তিনি হতাশ না হন। এ ছাড়া যাঁরা পিএইচডি করাবেন, তাঁদের পেশাগত ট্রেনিং দিতে হবে। যিনি পিএইচডি করছেন, তাঁকে বিষয়ভিত্তিক একটি-দুটি কোর্স করানো যেতে পারে, যা তাঁকে পিএইচডি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। যেমন : ইংরেজির কোর্স করানো যেতে পারে।
শুধু নামের আগে ‘ড.’ বসল। এ ধরনের পিএইচডি যেন আমরা উৎসাহিত না করি। কোনো ব্যক্তির পিএইচডি করার কারণটা আগে উদঘাটন করা দরকার। পাশাপাশি ওই ব্যক্তির উৎসাহ, মেধা, দক্ষতা ও সক্ষমতা আছে কি না সেটাও দেখা দরকার। সেই সঙ্গে পেশাজীবনে এর ব্যবহার হবে কি না সেটাও দেখা দরকার। এই বিষয়গুলো যাচাই করতে একজন শিক্ষার্থী ভর্তির আগে তাকে অবশ্যই ‘প্রপোজাল’ লিখতে দিতে হবে। এর মাধ্যমে তার দক্ষতার বিষয়টির পাশাপাশি উদ্দেশ্যও জানা যাবে। আগে শিক্ষাজীবনে দু-একটি পাবলিকেশন থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। পিএইচডিতে ভর্তির পরও নিয়মিত তদারকির প্রয়োজন রয়েছে। মানসম্মত পিএইচডির জন্য ছয় মাস অন্তর অন্তর রিভিউ করতে হবে। তাদের দিয়ে অন্তত দুটি পাবলিকেশন করাতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির সম্ভাবনা অনেক। কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাবলিকেশনের সংখ্যা ও মান দিন দিন বাড়ছে। এখন আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে, যাঁরা গবেষণা করে জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবেন। কারণ আজকের যুগে উদ্ভাবন ছাড়া কোনো জাতি উন্নত হতে পারবে না। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। পিএইচডি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাপোর্ট দিতে হবে, যাতে তিনি হতাশ না হন। এ ছাড়া যাঁরা পিএইচডি করাবেন, তাঁদের পেশাগত ট্রেনিং দিতে হবে। যিনি পিএইচডি করছেন, তাঁকে বিষয়ভিত্তিক একটি-দুটি কোর্স করানো যেতে পারে, যা তাঁকে পিএইচডি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। যেমন : ইংরেজির কোর্স করানো যেতে পারে।
সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধের উদ্যোগ প্রয়োজন
অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি
 প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় কিছু প্রভাব বা হস্তক্ষেপের ভয় থেকেই যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড থেকেও হস্তক্ষেপ করা হয়। পিএইচডি ডিগ্রিতে এমন হস্তক্ষেপ বন্ধের বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে নীতিমালায় আনতে হবে। ডিগ্রি দেওয়ার অনুমোদন বা ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে। যেন চাইলেই হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে। পিএইচডি বিষয়টাকে আমরা চাহিদা ও সরবরাহ—দুই দিক থেকেই দেখতে পারি। এটি অন্তত বিশেষায়িত ধরনের ডিগ্রি, যা ঢালাওভাবে দেওয়ার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। অনুমোদন পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ থাকতে হবে। ডিগ্রিটির তত্ত্বাবধানে যিনি থাকবেন, তাঁকে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স থাকা বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরির পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকলে এই ভারী ডিগ্রি দেওয়ার বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে ইউজিসিতে আবেদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য কোর্স ও গবেষণা মিলিয়ে একটি পদ্ধতিগত কাঠামো তৈরি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা উন্নত দেশগুলোর কাঠামোগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রতি বর্ষ শেষে একটি পরীক্ষাব্যবস্থা রাখতে হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়—এমন পিএইচডি বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধি রাখতে হবে।
প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় কিছু প্রভাব বা হস্তক্ষেপের ভয় থেকেই যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড থেকেও হস্তক্ষেপ করা হয়। পিএইচডি ডিগ্রিতে এমন হস্তক্ষেপ বন্ধের বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে নীতিমালায় আনতে হবে। ডিগ্রি দেওয়ার অনুমোদন বা ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে। যেন চাইলেই হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে। পিএইচডি বিষয়টাকে আমরা চাহিদা ও সরবরাহ—দুই দিক থেকেই দেখতে পারি। এটি অন্তত বিশেষায়িত ধরনের ডিগ্রি, যা ঢালাওভাবে দেওয়ার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। অনুমোদন পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ থাকতে হবে। ডিগ্রিটির তত্ত্বাবধানে যিনি থাকবেন, তাঁকে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স থাকা বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরির পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকলে এই ভারী ডিগ্রি দেওয়ার বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে ইউজিসিতে আবেদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য কোর্স ও গবেষণা মিলিয়ে একটি পদ্ধতিগত কাঠামো তৈরি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা উন্নত দেশগুলোর কাঠামোগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রতি বর্ষ শেষে একটি পরীক্ষাব্যবস্থা রাখতে হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়—এমন পিএইচডি বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধি রাখতে হবে।
যখন সমাজে কিংবা কর্মক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি দিয়ে পাঠাচ্ছি, তখন সমাজ তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করছে সে বিষয়ে আমাদের দুই থেকে তিনটি পরিসরে কাজ করতে হবে। ইউজিসি তাদের পর্যায় থেকে একটি সার্বিক নজরদারি করতে হবে। কিছুদিন পরপর বিশ্লেষণ করতে হবে, সমাজে আমরা কী ধরনের পিএইচডি ডিগ্রিধারী পাঠাচ্ছি ও কতসংখ্যক পাঠাচ্ছি। আমরা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এই সুযোগটি কাজে লাগাতে চাই।
বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে
অধ্যাপক এস কে তৌফিক এম হক, পিএইচডি
 বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের কিছু ভিন্নতা আছে, যা আলাদা শক্তি জোগায়। এর মধ্যে একটা হচ্ছে নিজস্বকরণ। এর ফলে নতুন কোনো বিষয়ে ডিগ্রি দেওয়া আমাদের জন্য সহজতর হয়। আরেকটি বিষয় হলো, বিদেশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পিএইচডি ডিগ্রি চালুর মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরো ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারবে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর মাধ্যমে বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে, সম্ভাবনার দ্বার আরো উঁচু করবে। বর্তমানে এসব বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করছে। তবে চ্যালেঞ্জের বিষয় হলো, সরকার বা অন্যভাবে সাহায্য-সহযোগিতা না থাকায় এখানে রিসার্চসংখ্যা খুবই নগণ্য। পুরো পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগতে বলা হয়, গবেষণা ছাড়া পিএইচডি কখনোই সম্ভব নয়। পিএইচডি প্রগ্রাম না থাকলে গবেষণার বিকাশ হয় না। গবেষণা করার জন্যই আসলে পিএইচডি প্রগ্রাম অত্যন্ত জরুরি। পিএইচডি না থাকলে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ নিজ উদ্যোগে কিছু প্রকাশনা করে থাকে। আর এই ডিগ্রির শিক্ষার্থীরা সুপারভাইজারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একত্রিতভাবে গবেষণা করেন। সেখান থেকে প্রকাশনা করা হয়, যা সারা পৃথিবীতে প্রচলিত বিষয়। আবার পিএইচডি শিক্ষার্থী ও গবেষণা থাকলে আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে থাকে। দেশে দুই-তিন দশক পর্যন্ত টিচিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চলেছে। ২০১৫ সালের পর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা শুরু হয়। আমাদের গবেষণার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবরেশন ছাড়া পিএইচডির বাস্তবতা তৈরি করা সম্ভব নয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা ও অর্থায়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোলাবরেশনের মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রির ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটি দেশে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি প্রয়োজন। আমরা যদি সত্যিই পিএইচডির জ্ঞানটাকে সমাজে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও সরকারে কাজে লাগাতে চাই, তাহলে সরকারি লোকজন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর লোকজনকে এই কমিটিতে রাখতে হবে। ডিজিটাল গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করতে হবে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের কিছু ভিন্নতা আছে, যা আলাদা শক্তি জোগায়। এর মধ্যে একটা হচ্ছে নিজস্বকরণ। এর ফলে নতুন কোনো বিষয়ে ডিগ্রি দেওয়া আমাদের জন্য সহজতর হয়। আরেকটি বিষয় হলো, বিদেশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পিএইচডি ডিগ্রি চালুর মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরো ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারবে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর মাধ্যমে বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে, সম্ভাবনার দ্বার আরো উঁচু করবে। বর্তমানে এসব বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ইনস্টিটিউট হিসেবে কাজ করছে। তবে চ্যালেঞ্জের বিষয় হলো, সরকার বা অন্যভাবে সাহায্য-সহযোগিতা না থাকায় এখানে রিসার্চসংখ্যা খুবই নগণ্য। পুরো পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগতে বলা হয়, গবেষণা ছাড়া পিএইচডি কখনোই সম্ভব নয়। পিএইচডি প্রগ্রাম না থাকলে গবেষণার বিকাশ হয় না। গবেষণা করার জন্যই আসলে পিএইচডি প্রগ্রাম অত্যন্ত জরুরি। পিএইচডি না থাকলে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ নিজ উদ্যোগে কিছু প্রকাশনা করে থাকে। আর এই ডিগ্রির শিক্ষার্থীরা সুপারভাইজারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একত্রিতভাবে গবেষণা করেন। সেখান থেকে প্রকাশনা করা হয়, যা সারা পৃথিবীতে প্রচলিত বিষয়। আবার পিএইচডি শিক্ষার্থী ও গবেষণা থাকলে আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে থাকে। দেশে দুই-তিন দশক পর্যন্ত টিচিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চলেছে। ২০১৫ সালের পর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা শুরু হয়। আমাদের গবেষণার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবরেশন ছাড়া পিএইচডির বাস্তবতা তৈরি করা সম্ভব নয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা ও অর্থায়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোলাবরেশনের মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রির ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটি দেশে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি প্রয়োজন। আমরা যদি সত্যিই পিএইচডির জ্ঞানটাকে সমাজে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ও সরকারে কাজে লাগাতে চাই, তাহলে সরকারি লোকজন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর লোকজনকে এই কমিটিতে রাখতে হবে। ডিজিটাল গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করতে হবে।
গুণগত মান রক্ষায় প্রতি সেমিস্টার শেষে মূল্যায়ন করতে হবে
অধ্যাপক ড. কবিরুল ইসলাম
 আমাদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পিএইচডি প্রগ্রামটি সাধারণত তিন বছরের জন্য করে থাকি। এর মধ্যে প্রতিবছর দুটি করে সেমিস্টার থাকে। এই তিন বছরে গুণগত পিএইচডি ডিগ্রি নিশ্চিত করতে হলে আলোচনার মাধ্যমে একটি গুণগত নীতিমালা তৈরি করতে হবে।
আমাদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পিএইচডি প্রগ্রামটি সাধারণত তিন বছরের জন্য করে থাকি। এর মধ্যে প্রতিবছর দুটি করে সেমিস্টার থাকে। এই তিন বছরে গুণগত পিএইচডি ডিগ্রি নিশ্চিত করতে হলে আলোচনার মাধ্যমে একটি গুণগত নীতিমালা তৈরি করতে হবে।
আমি মনে করি, প্রতি সেমিস্টার শেষে যদি একটি অ্যাসেসমেন্টের (মূল্যায়ন) কাঠামো থাকে তাহলে গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব। কারণ গুণগত মান নিশ্চিত করতে হলে মূল্যায়নের কোনো বিকল্প নেই। আমরা যদি এভাবে শুরু করি যে প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারে একটি সেমিনার থাকবে। সেই সেমিনার শেষে নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশকের (ইন্ডিকেটর) মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে দেখা যাবে, ওই শিক্ষার্থী সেমিস্টার শেষে কী অর্জন (আউটকাম) নিয়ে এলো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আন্তর্জাতিক কাঠামোতে পিএইচডির কাঠামো তৈরি করতে পারি, তবে গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এভাবে প্রতি বর্ষের সেমিস্টারে যদি একটা সেমিনার থাকে এবং সেই সেমিনারে পিএইচডি প্রার্থীর মূল্যায়ন করা হয়, তবে সেটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ পিএইচডি হয়ে থাকবে। প্রতিটি সেমিনার শেষে মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে একজন বিশেষজ্ঞ রাখতে হবে। প্রয়োজনে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষের শুরুতে এই কমিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। কমিটিতে যদি তিনজন সদস্য থাকেন, এর মধ্যে অন্তত একজন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসতে হবে। প্রতি বর্ষ শেষে পরবর্তী বর্ষে উন্নীত করা হবে কি না তা নির্ধারণ করতে একটি কাঠামো (মডিউল) তৈরি করতে হবে। যেন এই কাঠামোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিকশিত হতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে নামমাত্র ডিগ্রি অর্জন বন্ধ হবে, পিএইচডির নামে যেসব গুঞ্জন শুনতে পাই, তা অনেকটা বন্ধ হবে। বর্তমানে অনলাইন পিএইচডি কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। এই পিএইচডি হোল্ডারদের কোনোভাবেই সুপারভাইজারের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। নীতিমালায় এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।
অনুমতির পর ইউজিসিকে মনিটরিংয়েও জোর দিতে হবে
আলী হাবিব
 দেশে বর্তমানে ১১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি করার সুযোগ থাকলেও ১৯৯২ সাল থেকে চালু হওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা নেই। দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর অনুমতি ছিল না। এখন আগের সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্স চালুর বিষয়ে খসড়া নীতিমালা করতে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। নীতিমালা প্রণয়ন করতে কমিটি কাজ করছে। নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন চলমান। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানের দিক দিয়ে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই শুধু এই সুযোগ দেওয়া যায়। তাঁরা এটিও বলছেন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর অনুমতি দেওয়া হলে মনিটরিংয়েও জোর দিতে হবে। এ ছাড়া ভালো মানের গবেষণার প্রয়োজনে ইউজিসিকে সঠিক তদারকির বিষয়েও কঠোর হতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিএইচডি প্রগ্রাম চালুর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে দিতে হবে। যারা ক্রাইটেরিয়া পূর্ণ করবে, তারাই পিএইচডি প্রগ্রাম চালু করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হলো গবেষণালব্ধ নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা। এ জন্য দরকার স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষক শিক্ষার্থী। তাই সীমিত পর্যায়ে হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
দেশে বর্তমানে ১১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি করার সুযোগ থাকলেও ১৯৯২ সাল থেকে চালু হওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা নেই। দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর অনুমতি ছিল না। এখন আগের সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্স চালুর বিষয়ে খসড়া নীতিমালা করতে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। নীতিমালা প্রণয়ন করতে কমিটি কাজ করছে। নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন চলমান। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানের দিক দিয়ে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই শুধু এই সুযোগ দেওয়া যায়। তাঁরা এটিও বলছেন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিএইচডি ডিগ্রি চালুর অনুমতি দেওয়া হলে মনিটরিংয়েও জোর দিতে হবে। এ ছাড়া ভালো মানের গবেষণার প্রয়োজনে ইউজিসিকে সঠিক তদারকির বিষয়েও কঠোর হতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিএইচডি প্রগ্রাম চালুর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে দিতে হবে। যারা ক্রাইটেরিয়া পূর্ণ করবে, তারাই পিএইচডি প্রগ্রাম চালু করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হলো গবেষণালব্ধ নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা। এ জন্য দরকার স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষক শিক্ষার্থী। তাই সীমিত পর্যায়ে হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।


