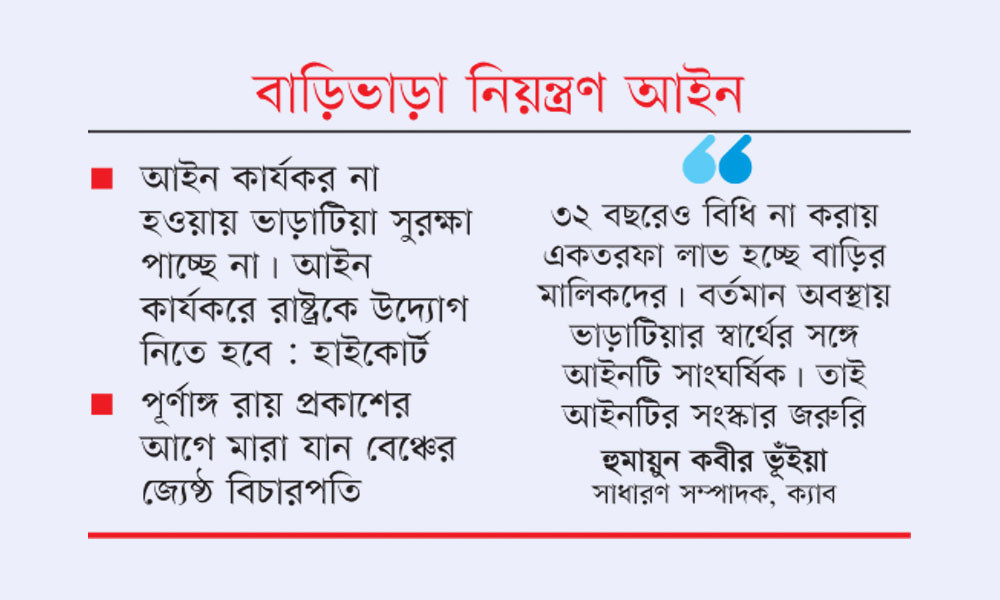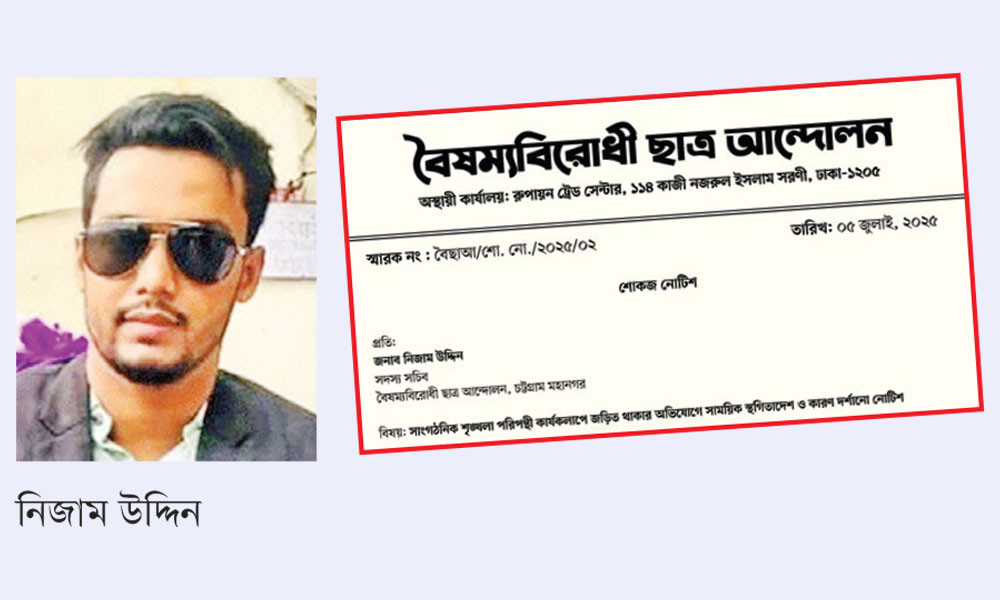বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণে ৩২ বছর আগে সরকার আইন করলেও তা প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। কারণ আইনটি প্রয়োগের জন্য যে বিধি প্রণয়ন করা দরকার তা এখনো হয়নি।
বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৯১ সালে। ভাড়া বাড়ানোর বিধি-নিষেধ, বাড়ির উন্নয়ন, ভাড়া আদায়ের রসিদ দেওয়া, বাস্তবসম্মত ভাড়া নির্ধারণে নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, ভাড়া বাড়ানোর হার সংক্রান্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিধান রাখা হয়েছে আইনটিতে।
কিন্তু দীর্ঘ সময়েও বিধি প্রণয়ন না করায় আইনটি কাগুজে আইনে পরিণত হয়েছে।
বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ৭ ধারায় বলা আছে, কোনো বাড়ির ভাড়া বাস্তবতার নিরিখে অধিক বাড়ানো হলে ওই বাড়তি ভাড়া আদায়যোগ্য হবে না। এমনকি ভাড়ার চুক্তিতে থাকলেও তা আদায় করা যাবে না।
আইনে বলা হয়েছে, ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে জামানত বা অন্য কোনো টাকা রাখতে পারবেন না বাড়ির মালিক।
এক মাসের বেশি অগ্রিম ভাড়া নেওয়া যাবে না।
আইনের ১৫ ধারায় মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণে বলা আছে, বাড়ির মালিক বা ভাড়াটিয়ার আবেদনের ভিত্তিতে মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণ করা হবে। এমনভাবে ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে, যাতে বাড়ির বাজারমূল্যের ১৫ শতাংশের সমান হয়।
১৩(১) ধারায় ভাড়া পরিশোধের রসিদ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
১৬(১) ধারায় বলা আছে, মানসম্মত ভাড়া, বাড়ির মালিক বা ভাড়াটিয়ার আবেদনের ভিত্তিতে প্রতি দুই বছর পর (নিয়ন্ত্রক কর্তৃক) পুনর্নির্ধারণ করা যাবে।
অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হলে বাড়ির মালিকের শাস্তি কী হবে, তা-ও বলা আছে আইনে। এসংক্রান্ত ২৩ ধারায় বলা হয়েছে, ‘আইনের এসব বিধান না মানলে আইনের অন্য কিছু বিধি-নিষেধ ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিক ভাড়া গ্রহণ করলে বাড়ির মালিক প্রথমবারের অপরাধের জন্য মানসম্মত ভাড়ার অতিরিক্ত আদায় করা টাকার দ্বিগুণ এবং পরবর্তী প্রতিবারের অপরাধের জন্য ওই অতিরিক্ত টাকার তিন গুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।’
আইনের পূর্বাপর : ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল বাড়িভাড়া আইনের গেজেট জারি করা হয়। ১৭ বছর পর ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা মহানগরীকে ১০টি রাজস্ব অঞ্চলে ভাগ করে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাড়া নির্ধারণ করে দেয় সিটি করপোরেশন (ডিসিসি)।
এর তিন বছর পর ২০১০ সালের ২৫ এপ্রিল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিট করা হয়। তাতে বলা হয়, বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে ভাড়ার রসিদ প্রদান, বাড়ি ছাড়ার জন্য নোটিশ দেওয়াসহ বিভিন্ন বিধান থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির মালিক সেটা পালন করেন না। ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা অনুযায়ী ভাড়াও আদায় করা হচ্ছে না। প্রাথমিক শুনানির পর ওই বছরের ১৭ মে আদালত রুল জারি করেন। বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান কার্যকর করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয় রুলে।
দীর্ঘ শুনানি করে ২০১৫ সালের ১ জুলাই বিচারপতি বজলুর রহমান ও বিচারপতি রুহুল কুদ্দুসের হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় দেন। রায়ে সারা দেশে এলাকাভেদে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাড়িভাড়া নির্ধারণের জন্য সরকারকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। রায়ে বলা হয়, বিদ্যমান আইনটি কার্যকর না হওয়ায় ভাড়াটিয়াকে সুরক্ষা দেওয়া যাচ্ছে না। আইনটি কার্যকরে রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিতে হবে।
কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই মারা যান বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বজলুর রহমান। এরপর মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে গেলে তিনি মামলাটির নিষ্পত্তির জন্য বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেন; কিন্তু পরে আর রিটের শুনানি করা হয়নি।
এর মধ্যে বাড়িভাড়া আইনের ১৫ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ এবং বাড়িভাড়া নির্ধারণে কমিশন গঠনে ২০১৯ সালে সম্পূরক আবেদন করে এইচআরপিবি। সেই আবেদনের শুনানি করে আদালত রুল জারি করেন। আইনের ১৫ ধারা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না এবং ‘ভাড়া নিয়ন্ত্রক’ নিয়োগসহ বাড়িভাড়ার বিদ্যমান অসংগতি দূর করে ‘মানসম্মত বাড়িভাড়া’ নির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়নে ১৯৫৬ সালের অনুসন্ধান আইনের ৩(১) ধারা অনুযায়ী অনুসন্ধান কমিশন গঠনের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না—তা জানতে চাওয়া হয় রুলে। মন্ত্রিপরিষদসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, সংসদ সচিবালয়ের সচিব, আইনসচিব ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এরপর আর এই রুলের শুনানি হয়নি।
রিটকারীর পক্ষের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, এখতিয়ারসম্পন্ন বেঞ্চে কয়েকবার রুল শুনানির জন্য গেলেও রুলটির আর শুনানি করা হয়নি। আবারও রুলটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে।
মনজিল মোরসেদ বলেন, আইনটি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আইনটি প্রণয়ন করেছে আইন মন্ত্রণালয়। তাই ধরে নেওয়া যায় আইনের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষও আইন মন্ত্রণালয়; কিন্তু আজ পর্যন্ত আইনটির বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীতে ১৯৯০ সালে পাকা ভবনে দুই কক্ষের একটি বাসাভাড়া ছিল দুই হাজার ৯৪২ টাকা। ২০১৫ সালে সেই ভাড়া দাঁড়ায় ১৮ হাজার টাকার বেশি। বর্তমানে তা ২৫ হাজার টাকার ওপরে।
ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবীর ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, আইনটির কার্যকারিতা না থাকায় মানুষ এই আইনে কোনো প্রতিকারও পাচ্ছে না। ৩২ বছরেও বিধি না করায় একতরফা লাভ হচ্ছে বাড়ির মালিকদের। বর্তমান অবস্থায় ভাড়াটিয়ার স্বার্থের সঙ্গে আইনটি সাংঘর্ষিক। তাই আইনটির সংস্কার জরুরি।