সারা দেশে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে, যেন গাছ কাটার মহোৎসব চলছে। সম্প্রতি যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা জেনে কোনো বিবেকবান মানুষের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়।
বেসরকারি সংস্থা রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি)-এর গাছ কাটাবিষয়ক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের মার্চ থেকে গত এপ্রিল পর্যন্ত দেশে সরকারি প্রকল্পে প্রায় ১৩ লাখ গাছ কাটা পড়েছে। এই হিসাবটি স্রেফ সংবাদপত্রের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।
আরডিআরসির লগিং অব প্লান্টস ইন বাংলাদেশ (২০২৪-২৫) শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে গত এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি প্রকল্পে প্রায় এক লাখ ৮২ হাজার গাছ কাটা হয়েছে। আগের বছরে একই গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত কাটা হয়েছে সাড়ে ১১ লাখ গাছ। গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি গাছ কাটা হয়েছে খুলনা জেলায়, ৮৫ হাজারের ওপরে। এর বাইরে অভাবে পড়ে, চুরি করে, বাড়ি করতে গিয়ে, রাস্তা বানাতে, কারখানা বা অফিস স্থাপন করতে, এমনকি শত্রুতা করেও অনেক গাছ কাটা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক কারণে, যেমন ঝড়ের কবলে পড়ে এবং খরায়ও প্রচুর গাছ ধ্বংস হয় বা মারা যায়।
এই গণহত্যার প্রধান রাজা হলো খোদ সরকারি সংস্থা। আরডিআরসির সর্বশেষ গবেষণা প্রতিবেদনে গাছ কাটায় এক্সপার্ট হিসেবে যে সংস্থাগুলোর নাম উঠে এসেছে সেগুলো হলো সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনার দিঘলিয়া উপজেলা মৎস্য কার্যালয়, রাজশাহী জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যশোর জেলা পরিষদ, মেহেরপুর জেলা পরিষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বন গবেষণা ইনস্টিটিউট।
গবেষণার প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫০ বছর বেঁচে থাকা একটা গাছ জীবন রক্ষাকারী যে অক্সিজেন দেয় তার মূল্য ২৫ লাখ টাকা, বায়ুদূষণ থেকে রক্ষায় ১০ লাখ টাকা, বৃষ্টি ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে বাঁচায় পাঁচ লাখ টাকা, মাটির ক্ষয়রোধ ও উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে বাঁচায় পাঁচ লাখ টাকা, বৃক্ষে বসবাসকারী প্রাণীদের খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে বাঁচায় পাঁচ লাখ টাকা, আসবাব, জ্বালানি কাঠ ও ফল সরবরাহ করে পাঁচ লাখ টাকা, বিভিন্ন জীবজন্তুর খাদ্য জোগান দিয়ে বাঁচায় আরো ৪০ হাজার টাকা।
তাহলে একটি বৃক্ষের আর্থিক সুবিধার মূল্য দাঁড়ায় ৫০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এ রকম কোনো উপকার প্রদানকারীকে পরিণত বয়সের আগেই কি খুন বলা যায় না?
কেউ কেউ বলবেন, বৃহত্তর স্বার্থে এমন কিছু কাজ সম্পন্ন করতে হয়, যেখানে গাছ না কেটে উপায় থাকে না। মানলাম সে যুক্তি। কিন্তু এখানে কয়েকটি বিষয় কি বিবেচনা আনা যায় না? যেমন গাছ না কেটে যতদূর সম্ভব প্রকল্প ডিজাইন করা যায় না? যদি কাটতেই হয়, তাহলে ন্যূনতম পর্যায়ে কেটে করা যায় না? গাছ যদি বিশেষ প্রয়োজনে কাটতেই হয়, তাহলে হিসাব করে এর সমসংখ্যায় গাছ কি লাগানো যায় না?
২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা বৈঠকে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন আইন ২০২১-এর খসড়া অনুমোদনের সময় ব্যক্তিমালিকানায় থাকা গাছ কাটতে অনুমতির বিধান রাখা হয়। সেই বৈঠক শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদসচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, ‘যাঁরা সাধারণ বাগান করবেন বা স্থায়ী যে গাছ লাগাবেন সেগুলোও তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো কাটতে পারবেন না।
পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ রকম আইন বা নিয়ম আছে। আমার বাড়িতে একটি গাছ পড়ে গেছে, এটা আমি সিটি করপোরেশন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কাটতে পারব না।
এরপর হাইকোর্ট এক রায়ে বলেন, ‘অনুমতি ছাড়া গাছ কাটা যাবে না, গাছ কাটার আগে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।’ বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। এর পরও গাছ কাটা বা খুন করা থেমে নেই।
হাদিস শরিফে আছে, যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে কিয়ামত এসে গেছে, তখন হাতে যদি একটা গাছের চারা থাকে, যা রোপণ করা যায়, তবে সেই চারাটি রোপণ করবে। (বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, মুসনাদে আহমাদ)।
জন্মের সময় এই পৃথিবীকে যেমন পেয়েছিলাম, মৃত্যুর আগে যেন তার চেয়ে একটু ভালোর দিকে এগিয়ে দিতে পারি। একজন মানুষের ন্যূনতম কর্তব্য এটি। এটার জন্য জীবন দিতে হবে না। আমরা যদি বছরে একটি করে গাছ লাগাই ও পরিচর্যা করি, তাহলে প্রতিবছর লাগানো গাছের সংখ্যা হবে সতেরো কোটির বেশি। ‘আরেক ফাগুনে’ তা দ্বিগুণ হবে।
আমরা তো কথা লাগাই। ক্যাচাল লাগাই। মারামারি লাগাই। ফেসবুকে ‘লাগানো’ নিয়ে আদিরসাত্মক কৌতুকে মেতে উঠি। কিন্তু আসল কাজ করি না। তাই আসুন, এই মৌসুম থেকেই শুরু করি।
প্রতিবছর অন্তত একটি করে গাছ লাগাই ও পরিচর্যা করি।
লেখক : কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক


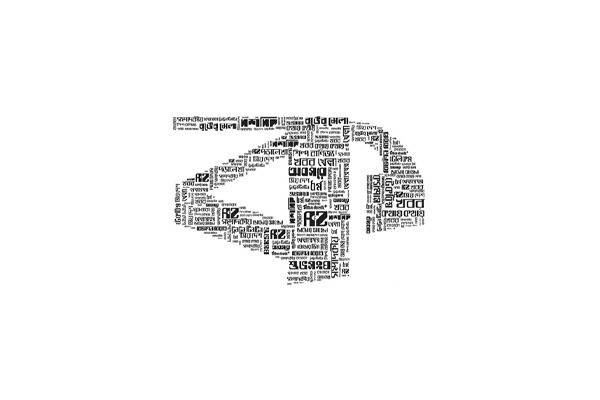




 বিমান দুর্ঘটনার অতিরিক্ত বিপদ হলো যে তার পেটের খোঁড়লে থাকা যাত্রীদেরই মৃত্যু ডেকে আনে তা নয়, তা মৃত্যু ঘটায় ভূমির মানুষদেরও, যাদের ওপর সে আছড়ে পড়ে। ঘটতে পারে
বিমান দুর্ঘটনার অতিরিক্ত বিপদ হলো যে তার পেটের খোঁড়লে থাকা যাত্রীদেরই মৃত্যু ডেকে আনে তা নয়, তা মৃত্যু ঘটায় ভূমির মানুষদেরও, যাদের ওপর সে আছড়ে পড়ে। ঘটতে পারে