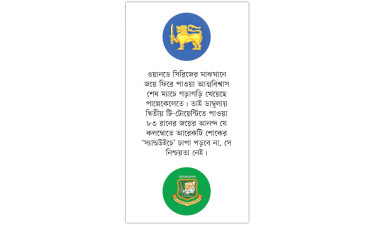দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের সম্পর্ক কত গভীর হতে পারে তার প্রতিফলন গত ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে দেখা গেছে। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের সামরিক কুচকাওয়াজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল সর্বাগ্রে। বিশ্বে বিরল ও অনন্য অসাধারণ ঘটনা। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি ভারত যে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাল, তা দুই দেশের সম্পর্কের রাস্তায় ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অনন্য উদাহরণ
মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)
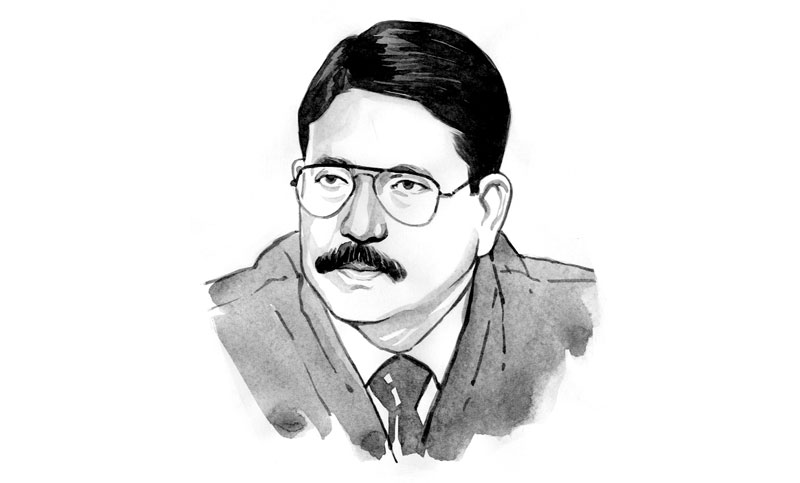
বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর করেন ২৫ বছর মেয়াদি অসাধারণ মৈত্রী চুক্তি। সেই চুক্তির মধ্যে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ ছিল। চুক্তির মোট ১২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৮ ও ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়, দুই দেশের কোনো একটি দেশ যদি অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহলে উভয় দেশ একত্র হয়ে সেই আগ্রাসন মোকাবেল করবে। সদ্যঃস্বাধীন দেশ, সব কিছু বিধ্বস্ত, সশস্ত্র বাহিনী অসংগঠিত, এ অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার জন্য চুক্তির ওই ধারাগুলো তখন একান্ত অপরিহার্য ছিল। একই রকম ধারাসংবলিত আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট। ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ফলেই পাকিস্তানকে সব রকম আশ্বাস দিয়েও একাত্তরের ডিসেম্বরে চীন সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো থেকে পিছু হটে যায়। তারপর ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির ফলে ভারত-সোভিয়েত-বাংলাদেশ মিলে যে অবস্থানের সৃষ্টি হয় তার কারণেই আমেরিকার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে ফেরত চলে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার শুরু থেকেই একাত্তর এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দর্শন ও আদর্শের অভিন্নতা দুই দেশের সম্পর্কের মৌলিক অবলম্বন হিসেবে কাজ করেছে। ৫০ বছরের লিগ্যাসি সাক্ষ্য দেয়, যখনই এর ব্যত্যয় ঘটেছে তখনই সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। বিগত ৫০ বছর দুই দেশের সম্পর্ক যদি একাত্তরের পর্যায়ে থাকত তাহলে শুধু ভারত-বাংলাদেশ নয়, পুরো উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতার চিত্রটি আজ ভিন্ন হতো এবং তাহলে আঞ্চলিক সহযোগিতার উদাহরণ হতে পারত দক্ষিণ এশিয়া।
সম্পর্কিত খবর
দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওগুলোর ভূমিকা
রোকেয়া ইসলাম

এনজিওগুলো বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সব স্তরের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের জন্য তারা ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা প্রচলন করেছে, শিক্ষাগতভাবে তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করেছে, স্বাস্থ্য স্তরে তারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেছে এবং সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করেছে। বিগত কয়েক দশকে দেশটির উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে, যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টার ঘাটতি পূরণে এনজিওগুলো অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।
বাংলাদেশে এনজিওগুলোর ইতিহাস মূলত দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও ১৯৭৪-পরবর্তী কঠিন সময়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।
স্বাধীনতা-উত্তর এই সংকটকালে বিদেশি এনজিওগুলো, বিশেষ করে অক্সফাম, কেয়ার, কনসার্ন, টেরি দাজ হোমস, সেভ দ্য চিলড্রেন, আরডিআরএস ইত্যাদি যুক্তরাজ্য ও ইউরোপ ভিত্তিক কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি সার্ভিসেস ওভারসিজসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে মানবিক সাহায্য; যেমন—ত্রাণ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে এগিয়ে আসে। দেশীয় এনজিওগুলো মূলত এসব বিদেশি সংস্থার আর্থিক সহায়তায় আশির দশকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এগুলোর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, গণস্বাস্থ্য, ভার্ক, বিভিএইচএসএসের মতো সংস্থাগুলো বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক আকারে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল এবং পরে এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় আশা, টিএমএসএস, ব্যুরো বাংলাদেশ ও আরো অনেক এনজিও। গত শতাব্দীর আশি ও নব্বইয়ের দশকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় এনজিওগুলোর দ্রুত বিকাশের কারণে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে দুর্দশাগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আরো অনেক মাঝারি ও ক্ষুদ্র এনজিও কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে এবং এগুলোর প্রতিটিরই দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
সরকারি বিনিয়োগ সংস্থাগুলোর ঋণ পাওয়া দরিদ্রদের জন্য সহজ ছিল না। ফলে এনজিওগুলোর সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সাধারণদের মাঝে ব্যাপকভাবে বিকাশ ঘটায় অতিদরিদ্র জনগণ ক্রমান্বয়ে তাদের দারিদ্র্যের মাত্রা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, মূলত ক্ষুদ্রঋণের কারণে এনজিও কার্যক্রমের ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। সেই সময় প্রতিটি এনজিওর সেবা প্রদানের জন্য অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল হতদরিদ্র বা দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগণ অধ্যুষিত এলাকায় সাধারণত এনজিওগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করত।
একসময় উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর বিভাগের ১০টি জেলার মধ্যে পাঁচটিই অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত ছিল। জেলাগুলো হলো কুড়িগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট। বিভিন্ন জরিপ প্রতিবেদনের মতে, বেশির ভাগই কৃষি শ্রমিক হওয়ায় আশ্বিন-কার্তিক মাস এলেই হাজার হাজার পরিবার কাজের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো। এ কারণেই মূলত উত্তরবঙ্গকে মঙ্গা এলাকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মঙ্গার সময় ১০০ জনের মধ্যে ৭১ জনই ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। ২০১০ সালের পর থেকে উত্তরবঙ্গের এই মঙ্গার কথা আর ততটা শোনা যায়নি এবং ২০১৬ সালের পর থেকে এটি একেবারেই শোনা যায়নি। কারণ দেশি-বিদেশি এনজিওগুলোর সহজ ও কৌশলগত সহযোগিতা এবং এনজিওগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ‘ক্ষুদ্রঋণ’ এই অঞ্চলের মঙ্গা দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। রংপুরের আরডিআরএস, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, আশা, টিএমএসএস, ব্যুরো বাংলাদেশসহ ছোট ও মাঝারি আরো অনেক বেসরকারি সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যা বিশেষত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে।
আশির দশক থেকে এনজিওগুলো ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন থেকে বের হয়ে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে; যেমন—অনানুষ্ঠানিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (শিশু ও বয়স্ক), প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গৃহায়ণ, ক্ষুদ্রঋণ, হাঁস-মুরগি-গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহায়ণ, পরিবেশ সুরক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি অনেক উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে শুরু করে। ফলে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে টাকার গতিশীলতা বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার নানা পথ অনুসন্ধান করা ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি হয়।
শুরু থেকেই এনজিওগুলো কাজ করেছে এমন এক সমাজে, যেখানে লিঙ্গবৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত ছিল এবং এ জন্য তারা নারীর অধিকার প্রচার, সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য কাজ করেছে এবং করছে। ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা এবং আইনি সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে এনজিওগুলো নারীদের তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
দারিদ্র্য দূরীকরণের আরেকটি প্রধান বাধা বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্র। সরকার এককভাবে পুরো জনগোষ্ঠীর শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারেনি, বিশেষ করে গ্রামীণ ও দূরবর্তী এলাকায়। এনজিওগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি প্রদান এবং নতুন শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করে এই ঘাটতি পূরণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো মা ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যানিটেশন বা স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপনের কনসেপ্টটি এনজিও থেকেই শুরু হয়েছিল। দারিদ্র্যের একটি প্রধান সমস্যা ছিল বেকার সমস্যা। আর এটি সমাধানের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট ছিল না বা এখনো নেই। এনজিও সেক্টরের একটি বড় ভূমিকা ছিল শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করায়।
সাধারণত সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (এনজিও) বা বাংলায় বেসরকারি সংস্থা। এ ছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জের নিবন্ধনকৃত ফাউন্ডেশনও এনজিওর অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য এনজিওগুলোর বিকাশ ও কার্যক্রম সারা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে সরকারের সমান্তরাল একটি জনসেবার স্রোত তৈরি হয় এবং এই স্রোতেই বেশির ভাগ দারিদ্র্য ভেসে যায় বাংলাদেশের।
তবে এনজিওগুলো বর্তমানে নানা রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যার মধ্যে বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা, জবাবদিহির সমস্যা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরিবেশের সমস্যা অন্যতম। এনজিওগুলোকে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে এবং বাড়াতে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে, শক্তিশালী অংশীদারি গড়ে তুলতে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণের পক্ষে কাজ চালিয়ে নিতে একটি অত্যন্ত শক্ত মনোবলসম্পন্ন ও দক্ষ নেতৃত্ব থাকতে হবে, যা দেশটিকে আরো উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেবে। এই অগ্রগতি যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকারের ভূমিকা অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে সরকার এমআরএ, পিকেএসএফ ও এনজিও ব্যুরো তথা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, দেশও ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।
লেখক : চেয়ারম্যান, প্রশিকা
গ্যাস সংযোগ কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ!
- ড. মো. ফখরুল ইসলাম

সম্প্রতি সরকারি কর্তৃপক্ষের একটি বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ঝড় তুলেছে তা হলো, কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও বাসাবাড়িতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। ঘোষণাটি নাগরিকদের মনে এক ধরনের বিহ্বলতা ও রসবোধ জাগিয়েছে। অনেকেই মুখ টিপে হাসছেন, কেউ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘মিম’ বানিয়ে ফেলেছেন। একটি মিম বা হাস্যকৌতুকে দেখা যাচ্ছে, ‘বউ : বাসায় গ্যাসের চুলা লাগাবে কবে? স্বামী : কিয়ামত আসুক, তারপর দেখি!’
বাস্তবতা হলো আমাদের প্রচুর গ্যাস আছে, কিন্তু হাতের নাগালে নয়।
কিয়ামতের পর যদি কেউ সত্যি রান্না করতে চায়, তখন কি গ্যাসের চুলা লাগবে, নাকি আগুন তখন অন্য কোনো জায়গায় জ্বলবে? কিয়ামত পর্যন্ত বাসাবাড়িতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ—এটি একটি সাধারণ উক্তি হলেও কারো কারো কাছে এর ভেতর বেদনা লুকিয়ে আছে, বিশেষ করে যাঁদের আয় খুব সীমিত। কেউ কেউ ভাবছেন, কেন এত কঠোর ঘোষণা? আসলে এটি এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল।
প্রশ্ন উঠছে, কিছু জায়গায় এখনো গোপনে টাকা দিয়ে গ্যাস সংযোগ ম্যানেজ হচ্ছে, সেখানে কি কিয়ামত আগে আসবে, না দুর্নীতির বিচার আগে হবে? রাষ্ট্র তার সীমাবদ্ধতা ঢাকতে গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলায় আমরা যুক্তির জায়গা থেকে আবেগ ও অতিশয়োক্তির রাজ্যে প্রবেশ করেছি না তো? এখানে যুক্তিপূর্ণভাবে বলা যেত, বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন সংযোগ স্থগিত রাখা হয়েছে।
রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে আবাসন খাতে বড় একটা পরিবর্তন ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষ জীবনভর সঞ্চয় করে নতুন ফ্ল্যাট কিনছেন, স্বপ্ন দেখছেন নতুন জীবনের। কিন্তু সেই বাড়িতে চুলা বসাতে গেলে তাঁরা জানতে পারছেন সংযোগ নেই!
আমরা মানি দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ সীমিত, উৎপাদন কমছে, চাহিদা বাড়ছে। এলএনজি আমদানির খরচ আকাশছোঁয়া আর বাসাবাড়িতে চিরাচরিত পাইপলাইনের ব্যবস্থায় ব্যাপক অপচয় ও দুর্নীতি বিদ্যমান।
সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সীমিত সম্পদকে ন্যায়সংগতভাবে বিতরণ করা এবং যে সিদ্ধান্তই হোক, ভাষাগতভাবে সংবেদনশীল থাকা। কারণ রাষ্ট্র যখন বলে, কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ, তখন জনগণ প্রশ্ন করে, আমাদের কি তাহলে বেঁচে থাকার অধিকারও মেয়াদহীন হয়ে গেল? যদি আমরা একটু গভীরভাবে ভাবি, তাহলে দেখতে পাই, এই কথাটির ভেতরে যে কেবল ব্যঙ্গ আছে তা নয়, আছে এক দীর্ঘস্থায়ী বেদনা, নীতিনির্ধারণী অপারগতা এবং নাগরিক আস্থার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া।
শেষে একটি নৈতিক প্রশ্ন, সংযোগ বন্ধ, কিন্তু কার জন্য? সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হচ্ছে যদি সত্যি সংযোগ ‘কিয়ামত পর্যন্ত’ বন্ধ থাকে, তাহলে কিছু নতুন ফ্ল্যাটে কিভাবে নিয়মিত গ্যাস আসছে? কে দিচ্ছে? কার অনুমতিতে? কেনই বা এক শ্রেণির মানুষ ঘুষ দিয়ে সংযোগ পাচ্ছেন, অথচ অন্যরা পাচ্ছেন না?
যদি এই অনিয়মই চলতে থাকে, তাহলে সংযোগ বন্ধের ঘোষণা কি কেবল সাধারণ মানুষের জন্যই প্রযোজ্য? রাষ্ট্র কি তাহলে আর্থিক বা সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যকে স্বীকার করে নিচ্ছে? এই ঘোষণার আরেকটি দুঃখজনক দিক হলো এর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারলাম, সরকার এই সংকট সমাধানে কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রকাশ করতে পারেনি। নতুন গ্যাস অনুসন্ধান, অপচয় রোধ, এলপিজির ন্যায়সংগত দামে সরবরাহ, বিকল্প জ্বালানিতে গবেষণা—এসব কিছু নিয়েই সরকারের নীরবতা।
নাগরিকরা এখন ব্যঙ্গ করে প্রতিবাদ করছেন। কারণ তাঁরা আর প্রথাগত চ্যানেলে একটি ‘ব্যুরোক্রেটিক হাইপারবোল’ জবাব আশা করেন না। কিন্তু এই অবিশ্বাস যদি নির্মূল না হয়, গ্যাস সংযোগ তো দূরের কথা, রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মানবিক সংযোগও হারিয়ে যেতে পারে।
লেখক : সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
fakrul@ru.ac.bd
অর্থনীতি গতিশীল রাখতে নির্বাচন জরুরি
- আব্দুল বায়েস

কথিত আছে যে এক হিংসুটে লোক তার প্রতিবেশীকে বলছে, ‘তোমার ছেলে পরীক্ষায় পাস করবে না।’ ছেলেটি যখন পরীক্ষায় পাস দিল, তখন ছেলের বাবাকে বলা হলো, ‘পাস দিয়েছে তো কী হয়েছে, এই ছেলে কোনো দিন চাকরি পাবে না।’ ছেলেটি যখন সত্যি সত্যি চাকরি পেয়ে গেল, তখন বলা হলো, ‘ছোকরা চাকরি পেল বটে, কিন্তু বেতন পাবে না।’ অবশেষে বেতন পাওয়ার পর হিংসুটে লোকটি তার প্রতিবেশীকে যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে, বেতন পাওয়া আর সুখে থাকা এককথা নয়।
দুই
 এ ব্যাপারে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে আপাতত দু-একটি উল্লেখ না করলেই নয়। সদানন্দ ধুম নামে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক কলামিস্ট বেশ কয়েক বছর আগে একটি মন্তব্য ছুড়েছিলেন : প্রায় ৪০ বছর আগে শুধু একজন বেপরোয়া আশাবাদী ছাড়া অন্য কেউ অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী পাকিস্তানের বিপরীতে বন্যাপ্রবণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ওপর বাজি রাখতে চাইত না। যাঁরা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, হেনরি কিসিঞ্জারের নিষ্ঠুর মন্তব্য ‘বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল বাসকেট কেস’, তাঁদের সেই স্বপ্ন ধ্বংস না করলেও যে বিরাট একটি ধাক্কা দিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
এ ব্যাপারে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, তবে আপাতত দু-একটি উল্লেখ না করলেই নয়। সদানন্দ ধুম নামে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক কলামিস্ট বেশ কয়েক বছর আগে একটি মন্তব্য ছুড়েছিলেন : প্রায় ৪০ বছর আগে শুধু একজন বেপরোয়া আশাবাদী ছাড়া অন্য কেউ অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী পাকিস্তানের বিপরীতে বন্যাপ্রবণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ওপর বাজি রাখতে চাইত না। যাঁরা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, হেনরি কিসিঞ্জারের নিষ্ঠুর মন্তব্য ‘বাংলাদেশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল বাসকেট কেস’, তাঁদের সেই স্বপ্ন ধ্বংস না করলেও যে বিরাট একটি ধাক্কা দিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
তিন
এখন বাস্তবতা এই যে কঠিন দুঃসময়ের মধ্যেও বাংলাদেশ প্রশংসনীয়ভাবে টিকে থাকতে পেরেছে, যদিও দেশটিকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে; যেমন—মানুষের স্বাধীনতার অভাব, স্বৈরাচারী কাঠামো, দুর্নীতি ইত্যাদি।
১৯৭৪ সালে ভিজিএফ কার্ড বলে কোনো কিছু ছিল না এবং ওরস্যালাইনের কল্পনা ছিল একপ্রকার বাতুলতা।
চার
তবে এই জেগে ওঠা যে বাংলাদেশের আদি সমালোচকদের ভবিষ্যদ্বাণীকে মোটামুটি মিথ্যা প্রমাণিত করতে পেরেছে, সে কথাটি স্বয়ং সমালোচকদের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে। যাঁরা স্বাধীনতার শুরুতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইউস্ট ফাল্যান্ড ও জে পারকিনসন ৩২ বছর পর ২০০৭ সালে বাংলাদেশে এসে বলে গেলেন, প্রারম্ভিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি প্রকৃত টেস্ট কেসের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যদিও নিশ্চিত করে বলার সময় আসতে অনেক বাকি, এই মুহূর্তে এবং তিন দশকের অধিক সীমিত এবং সুখ-দুঃখের অগ্রগতি দেখে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন হাতের নাগালের মধ্যে। বর্তমানে বাংলাদেশ যে সমস্যার সম্মুখীন; যেমন—রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সম্পদ আয়ের অসম বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই, অন্যান্য দেশে তাদের নিজের মতো করেই সেসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।
পাঁচ
তুলনার কথাটি যখন এসেই পড়ল, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধকালে অবকাঠামোগত ধ্বংস ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি পিছিয়ে থাকলেও সম্প্রতি দেশটির প্রবৃদ্ধির হার পাকিস্তানের হারকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক নির্দেশকগুলোতে বাংলাদেশ যে ব্যাপক উন্নতি করেছে, তাতে একসময় এগিয়ে থাকা পাকিস্তান পিছিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর এবং অসাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদবিরোধী অবস্থানের বিপরীতে পাকিস্তানে জঙ্গিবাদের উত্থান ও গণতন্ত্রের জায়গায় সামরিকতন্ত্রের প্রভাবের কথা আপাতত না-ই বা বলা হলো। সুতরাং যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে যাচ্ছিল এই বলে যে পাকিস্তান ছেড়ে এলে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে, তাদের জন্য বাংলাদেশের তুলনামূলক ভালো অর্জন বুক চাপড়ানো উন্নয়ন-ধাঁধা হিসেবে থাকছে বলে মনে হয়। ভারতের বিপক্ষেও অর্জন অনেক আশাব্যঞ্জক। স্বয়ং নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মাথাপিছু আয়ের পার্থক্যটা ক্রমেই কমতির দিকে।
ছয়
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে এক গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটে এবং জনগণের স্ফীত প্রত্যাশা সামনে রেখে একটি অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। গেল এক বছরে সরকারের সাফল্যের ঝুড়িতে বেশ কিছু পদক্ষেপ প্রশংসা কুড়িয়েছে; যেমন—ব্যাংকিং খাতের নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ, বৈদেশিক মুদ্রার মান সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা ইত্যাদি। কিন্তু বিষম রকমের অভিযোগ আছে যে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষত মব সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এই ব্যর্থতা ঢাকতে নানা গল্প শোনানো হচ্ছে। কলকারখানায় হামলা, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, ব্যবসায়ীদের প্রতি হুমকি ইত্যাদি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ উঠছে। এমতাবস্থায় প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকারের কাছে ক্ষমতা যাওয়া উচিত বলে ধারণা অভিজ্ঞমহলের। সন্দেহ নেই যে রোল মডেল স্ট্যাটাস থেকে বাংলাদেশ এখন বহু দূরে। তাই আশু করণীয় হচ্ছে, চটজলদি নির্বাচন কমিশন সংস্কারের মাধ্যমে ঘোষিত সময়ে দেশে নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক, কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত একটি ন্যায়সংগত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। আমরা চাই না যে বাংলাদেশ পরিচিত হক প্রত্যাশা পূরণের ব্যর্থতার রোল মডেল হিসেবে।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, সাবেক উপাচার্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ট্রাম্পের ইউক্রেসি বয়ান
- জিয়াউদ্দিন সাইমুম

২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচন অনেক আমেরিকানের সামগ্রিক মানসিকতায় এক রূপান্তরমূলক পরিবর্তন তুলে ধরতে পেরেছে। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে প্রচারণা সমাবেশে রিপাবলিকান প্রার্থীর নামই উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প মঞ্চে উপস্থিত হতেন, তখন জনতার স্লোগানটি ছিল : ‘যুক্তরাষ্ট্র! যুক্তরাষ্ট্র! যুক্তরাষ্ট্র!’
এই স্লোগানটির অর্থ কী? এর তাৎপর্য কী? গভীর হতাশা এবং আবেগপ্রবণ আশার শেষহীন দোলাচলে মানসিক উত্তেজনা থেকে স্লোগানটির জন্ম। ট্রাম্পপন্থীদের মতে, ‘আমেরিকাকে আবার মহান করুন’ (MAGA) ধারণাটি কিছু লোকের কাছে রীতিমতো অভিশাপ, কিন্তু দেশপ্রেমিক আমেরিকানদের কাছে স্লোগানটি একটি জাতিকেন্দ্রিক সরকারের জন্য তাঁদের আকুলতার প্রতীক।
ট্রাম্প ও তাঁর আন্দোলন আমেরিকান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমাপ্তির পাশাপাশি একটি নতুন ধরনের সরকার ব্যবস্থা সূচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁদের মতে, এই রূপান্তর কৌশলকে যথাযথভাবে দেশপ্রেমিক ইউক্রেসি হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যা সমসাময়িক আমেরিকান শাসনব্যবস্থায় প্রাচীন গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়ের একটি আধুনিক অনুবাদ।
তাঁদের মতে, এই নতুন ধারণাটির ভিত্তি হচ্ছে নিপাট দেশপ্রেম। তাত্ত্বিক দিক থেকে এটিই ইউক্রেটিক (গ্রিক বঁ থেকে উদ্ভূত, যার আভিধানিক অর্থ ‘ভালো’)।
এই ইউক্রেটিক মূল্যবোধের সম্ভাব্য পরিণতি আঁচ করতে পেরেই মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারের মতো স্বৈরচারী দেশগুলো ট্রাম্প ও তাঁর চৌকস টিমকে নজিরবিহীন আগ্রহে স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়েছে। মাথা ঘোরানো অঙ্কের অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি আর কল্পনাতীত দামি উপহার এই দেশগুলো ট্রাম্পের চরণে নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছে। এই সফর ট্রাম্পের বহুল আকাঙ্ক্ষিত এমন একটি ইউক্রেটিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে সহায়তা করেছে, যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকরা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার এবং একটি আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। চতুর ট্রাম্প সম্ভবত এটি আগেভাগেই স্থির করে ফেলতে পেরেছেন, তাঁর ইউক্রেটিক বিশ্ব গঠনের অর্থনৈতিক দিকটি তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবের দেশগুলো থেকে আদায় করে নিতে পারবেন।
ট্রাম্প উদ্ভাবিত ইউক্রেসি তত্ত্বের ভবিষ্যৎ আসলে কেমন হবে, তা এই গ্রহবাসী জানে না।
তাহলে ট্রাম্প কি গণতন্ত্রের অবসান টেনে আনছেন? হ্যাঁ, যদি প্রশ্নটি আমেরিকান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণের পতনের কথা উল্লেখ করে, তাহলে উত্তরটি ইতিবাচক হতে বাধ্য। কারণ মার্কিন সমাজব্যবস্থা এখন সীমাহীন উদাসীনতা, দৃষ্টিকটু পক্ষপাত এবং আদর্শিক চরমপন্থায় জর্জরিত, যা প্রগতিবাদের ছদ্মবেশে নিজেই নিজের ডেথ ওয়ারেন্ট ইস্যু করে দিচ্ছে, যা প্রায়ই সমাজের সবচেয়ে দুর্বলদের নিয়মিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পন্থায় শোষণ করে যাচ্ছে।
কিন্তু ট্রাম্পের ইউক্রেটিক ভক্তরা পাল্টা বয়ান দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের দাবি ট্রাম্পের ইউক্রেটিক দর্শন আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার জন্য জনগণের ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষয়কে নির্দেশ করছে। এটি মোটেও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিপন্ন করছে না, বরং MAGA (Make America Great Again) এবং MAHA (Make America Honest Again) উদ্যোগের মাধ্যমে ট্রাম্প ও তাঁর মিত্ররা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন না, বরং রূপান্তর করছেন। তাঁরা শাসনের একটি নতুন রূপের সূচনা করছেন, যা কেতাবি নাম ‘ইউক্রেসি’। এটি জনগণের ভালোর জন্য, ভালো মানুষের দ্বারা পরিচালিত একটি সরকার।
লেখক : সাংবাদিক ও গবেষক