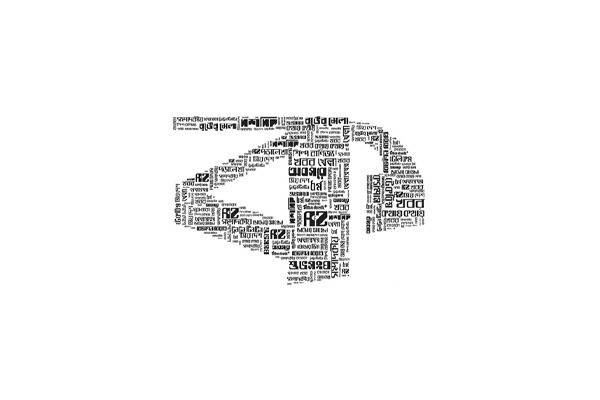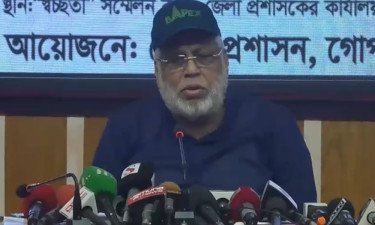আমি যখন হাসপাতালে রুদ্রকে দেখতে গেলাম, তখন বিকেল। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের দেয়ালজুড়ে পড়ন্ত বিকেলের রোদ মাখামাখি করে আছে। এই রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলেও মনটা অস্বস্তিতে ভরা। তিন তলার একটি কেবিনে রুদ্রর চিকিৎসা চলছে।
স্মরণ
দ্রোহের কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
- ইসহাক খান
notdefined

আমি খবর পেয়েছি ওর হাসপাতালে ভর্তির তিন দিন পর। রুদ্র তিন দিন হলো হাসপাতালে আর আমি ওকে এখনো দেখতে যাইনি। বড় বেদনাবোধ নিয়ে ওর কেবিনে ঢুকলাম। চারপাশ ঘিরে আছে ওর স্বজনরা।
রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম।
ডা. সাইফুল্লাহর সঙ্গে কথা হলো। আমি জানতে চাইলাম, ‘ওর কী হয়েছে?’
‘দাদার আলসার। ঘা হয়ে গেছে। নল দিয়ে ঘায়ের লালা বের করা হচ্ছে।’
‘তাহলে তো ওর খুব কষ্ট হচ্ছে?’
সাইফুল্লাহ দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল, ‘তা তো একটু হচ্ছে।’
‘এভাবে আর কত দিন নল নাকে-মুখে থাকবে?’
‘সেটা তো চিকিৎসার ওপর নির্ভর করছে।’
হাসপাতালের ব্যালকনিতে আমাদের কথা হচ্ছিল। আমার চোখের সামনে দুর্দান্ত এক তেজি তরুণের মুখোচ্ছবি ভেসে উঠছিল বারবার। আমাদের সময়ে সবচেয়ে সাহসী বন্ধু, সবচেয়ে তেজি, প্রতিবাদী রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, তার এই অসহায় পরিণতি আমি মানতে পারছিলাম না।
ব্যালকনির এপাশে-ওপাশে ওর ভাইবোনরা বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আহা! ওর ভাইবোনগুলো একেকটা যেন সোনার টুকরো। কি বিনয় সবার। আবীর আবদুল্লাহ, রুদ্রর তিন নম্বর ভাই। ইদানীং এই ভাইটি ফটোগ্রাফিতে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করেছে। হাসপাতালের ব্যালকনিতে আমার পাশে উদাস তাকিয়ে ছিল। ওর বিষণ্ন চোখ জোড়ায় আমি যেন রুদ্রের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম। দুই ভাইয়ের চেহারায় অদ্ভুত মিল। আমার চোখে ভেসে ওঠে, তাগড়া এক যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে দ্রোহের কবিতা পড়ছে, ‘জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন।’
১৯৭৮ সালে সাহিত্য পত্রিকা ‘সমকাল’-এ ওর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার নাম ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’। সেই শুরু উজান স্রোতে যাত্রা। কবিতাটি তাকে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি এনে দেয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতাটি আবৃত্তি হতে থাকে। এই কথাটা বোধ হয় জোর দিয়েই বলা যায়, বাংলাদেশে যাঁরা আবৃত্তি চর্চা করেন, তাঁরা সবাই কোনো না কোনো দিন নিজের তাগিদে এই কবিতাটি কোনো অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছেন। রুদ্র নিজেও এই কবিতাটি অনেক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছে। বাংলাদেশের খ্যাতিমান সব আবৃত্তিকারের কণ্ঠে আমি এই কবিতাটির আবৃত্তি শুনেছি। এমনকি আমি নিজেও এই কবিতাটি দু-একটি অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছি। কিন্তু রুদ্র যখন কবিতাটি পড়ত তখন যেন কবিতাটি অন্য মাত্রা পেত। ওর আবৃত্তি আমাকে বেশি টানত।
ওর সঙ্গে পরিচয়ের পর্বটা নাটকীয়। যদিও আমরা একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছিলাম। কিন্তু আমাদের পরিচয় হয়েছে পরে। আমি কিছুটা অন্তর্মুখী স্বভাবের। সোজা বাংলায় যাকে বলে পলায়নমুখী। তবে আমি ওকে চিনতাম। বাবরি চুল উড়িয়ে সে দলবেঁধে ক্যাম্পাসে আড্ডা দিয়ে বেড়াত। আমারও ইচ্ছা করত ওদের আড্ডায় অংশ নিতে। কিন্তু আমি আমার স্বভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতাম না। আড়ালে থাকতেই আমার বেশি ভালো লাগত। একদিন হাকিম চত্বরে আমাদের আরেক বন্ধু কবি তুষার দাস আমার সঙ্গে রুদ্রর পরিচয় করায়। রুদ্র বিস্ময়ে বলে, ‘আপনি ইসহাক খান! আমি তো মনে করেছিলাম আপনার অনেক বয়স।’
‘আপনার এ রকম মনে হলো কেন?’
‘আপনার লেখা পড়ে। যাক বাদ দেন। আপনি তো প্রচুর লেখেন।’
কথার ফাঁকে কখন আমরা আপনি থেকে তুই হয়ে গেছি তা নিজেরাও জানি না। কী পেল সে আমার মধ্যে—আমি জানি না। আমি নিজেও কি একটা পেয়ে গেলাম—যা এখনো আমার কাছে ব্যাখ্যাতীত। ক্রমে আমাদের ‘তুই’-এর ঘনত্ব বাড়তে লাগল। আমার নাকি বন্ধুভাগ্য ভালো। আমি স্বীকার করি। গর্বিত রুদ্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল কিংবা রুদ্র আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিল। এক সময় আমার হলের ঠিকানা রুদ্রের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে যায়। আমরা একসঙ্গে থাকি। একসঙ্গে চলি। একসঙ্গে খাই। একসঙ্গে ঘুমাই। মজার ব্যাপার হলো, রুদ্র আবাসিক ছাত্র ছিল না। বাসা ভাড়া করে থাকত। বাসা ভাড়া ঠিকই দিত, থাকত আমার সঙ্গে হলে ডাবলিং করে। আমার হলের ঠিকানা হয়ে গেল ওর যোগাযোগের একমাত্র ঠিকানা। ওর চিঠি আসত আমার হলের ঠিকানায়। পত্রিকা আসত। চেক আসত। আর আসত ওর এক সময়ের ভালোবাসার সঙ্গী তসলিমা নাসরিনের চিঠি। অসম্ভব সুন্দর তার হাতের লেখা। তসলিমা চিঠি লিখত নিয়মিত। প্রতি সপ্তাহে তার চিঠি আসত।
রুদ্র আমাকে অন্তর্মুখী স্বভাব থেকে টেনে বহির্মুখী করে। সাহিত্যের আড্ডায় ওই আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত। ওর পরিচয়ের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল। কোনো নতুন জায়গায় গিয়েও ঠিকই ওর চেনা মানুষের দেখা পেয়েছি। রুদ্র চেনার আগে তারাই চিত্কার করে জড়িয়ে ধরত রুদ্রকে।
একদিন সন্ধ্যায় নবাবপুর রোড ধরে হেঁটে যচ্ছি আমি আর রুদ্র। হঠাৎ থেমে বলে, ‘দাঁড়া, তোকে একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।’ কার সঙ্গে? জবাবে বলল, ‘গেলেই দেখতে পাবি।’ আমরা একটি আবাসিক হোটেলে ঢুকলাম। ও হোটেলের রিসিপশনে গিয়ে কথা বলে আমাকে নিয়ে দোতলায় উঠে পড়ল। একটি দরজায় নক করল রুদ্র। একটু পর দরজা খুলে আমার বয়সী একজন যুবক বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে চিনি। তিনি আমাকে চেনেন না। রুদ্রকে দেখে তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, কী মনে করে?
‘এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোর সঙ্গে দেখা করে যাই। অনেক দিন দেখা হয় না।’ আমরা ভেতরে গিয়ে বসলাম। তাঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করাল। রুদ্র বলল, ‘ও হলো এই সময়ের জনপ্রিয় লেখক—ইমদাদুল হক মিলন। আর ও ইসহাক খান। তোর লাইনের জিনিস।’
‘ঠিকই বলেছিস, আসলেই জিনিস।’ মিলন হেসে বললেন।
এ নিয়ে এক পশলা হাসাহাসি হলো। পরিচিত হলাম ইমদাদুল হক মিলনের সঙ্গে। সম্পর্ক শুরু হলো তুই দিয়ে। এই প্রথম কোনো বন্ধুর সঙ্গে ‘তুই’ দিয়ে আমার সম্পর্কের শুরু। সেটাও রুদ্রের কারণে।
মজার ঘটনা হলো, মিলন সেই সময় বিটিভিতে একটি ধারাবাহিক নাটক লিখছিল। তখনো এত চ্যানেল হয়নি। বিটিভি একমাত্র চ্যানেল। লোকজনের উৎপাতে আত্মগোপন করে হোটেলে রুম ভাড়া করে নাটক লিখছে মিলন। শুনে আমি থ। নাটক লেখার জন্য তাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে! মিলন মিথ্যা বলেনি। তার জনপ্রিয়তা তাকে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করেছে। মিলনের এই গোপন আবাসের স্থানটি রুদ্রর অজানা নয়। সেটাও আমাকে বিস্মিত করল।
১৯৯১ সালের ১৯ জুন। হাসপাতালে গিয়ে ওকে দেখে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। বেশ পরিপাটি লাগছিল। বেডে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে উঠে বসল। ‘কেমন আছিস?’
বলল, ‘অনেকটা ভালো।’
আমি বললাম, ‘তোকে দেখেও তাই মনে হচ্ছে, ভালো লাগছে। জানিস, খুব ভালো লাগছে।’ ফেরার সময় বললাম, ‘কাল আসতে পারব না। পর দিন আসব।’
পরদিন মানে ২১ জুন আসব। কিন্তু আমি তখনো জানি না ২১ জুন হবে আমার বন্ধুর জীবনের শেষ দিন। ২০ জুন হাসপাতালে আসতে হলো বন্ধু মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে। রুদ্র আমাকে দেখে বলে, তোর তো আজ আসার কথা না। এসে ভালোই করেছিস। আজ আমাকে রিলিজ করে দিয়েছে। সেদিন আমরা অনেক মজা করেছিলাম। হাসিঠাট্টা হয়েছিল বেশ। তারপর ট্রলি করে ওকে নিচে নামালাম। ওর হাতে অনেক রজনীগন্ধা ফুল। গাড়িতে ওঠার পর রজনীগন্ধার একটি ডাঁটা আমার হাতে দিয়ে বলল, ‘শ্যামলীকে দিস। আর বলিস, এবার সত্যি-সত্যি বদলে যাব।’ বউকে কথাটা বলতে ভুলে গেছিলাম। পরদিন তাকে ভয়াবহ খবরটি দিতে হলো, ‘রুদ্র আর নেই।’
লেখক : গল্পকার, টিভি নাট্যকার
সম্পর্কিত খবর
বিএনপির পথ আটকানোর পাঁয়তারা কেন
- জব্বার আল নাঈম

সন্দেহাতীতভাবে দেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি কঠিন সময় পার করছে। কারণ একদিকে রয়েছে সংস্কারের নামে বিএনপিকে বিব্রত করার কৌশল, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কূটকৌশল ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় দলটি যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, বিএনপি কি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার, নাকি প্রতিহিংসার শিকার? নাকি কারো চক্রান্ত? যদি এমনটাই হয়, তাহলে এসবের সমাধানে বিএনপির কৌশল কী হতে পারে?
বিএনপির ইচ্ছা দ্রুতই রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে সক্রিয় দলগুলোর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, কিন্তু প্রক্রিয়াটা যে সহজভাবে হচ্ছে না কিংবা হতে দেওয়া হবে না, তা মোটামুটি পরিষ্কার।
২
সংস্কার প্রশ্নে বিএনপির কিছু মতভিন্নতা রয়েছে, সেটি সবাই জানে। আবার মতভিন্নতার ভেতর দিয়েই দেশে গণতন্ত্রের ভিত শক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবতা বলে আসলে মতভিন্নতা নয়, বিগত দিনের লড়াই-সংগ্রাম ও নির্যাতনের মাঝেও দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা পেশ করেন, যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলনের মাঠে কর্মীরা জীবনও দিয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে যখন জুলাই চব্বিশ নেমে এলো, পরবর্তী রাষ্ট্র গঠনে প্রাসঙ্গিক হলো বিএনপির সংস্কার প্রস্তাব।
বিএনপিকে সরাসরি মিডিয়া ট্রায়ালের সামনে দাঁড় করানোটা কোনো কোনো দলের পক্ষে যৌক্তিক সমাধান যেন। এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা নিম্নরুচির পরিচয় দিয়ে প্রতিনিয়তই আক্রমণ কিংবা অপমানিত করছেন।
অনুমান করে বলছি, নির্বাচনটি হতে পারে তিনটি ব্লকে। প্রথম ব্লকে বিএনপি, দ্বিতীয় ব্লকে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন ও এনসিপি আর সর্বশেষ ব্লকে ১৪ দল। যদিও নির্বাচনের আগে আরো জল ঘোলা হবে, ঘোলা জলে মাছ শিকার হবে, বিএনপিকে টার্গেট করে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ফেলা হবে। এর পরও সব দলেরই লক্ষ্য থাকবে একটিই—বিএনপি ঠেকাও! তার পরও নির্বাচনের আগে নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি করতে জামায়াত, এনসিপি ও অন্যান্য দলকে নির্বাচনমুখী লাইনে রাখাও বিএনপির দায়িত্ব। তাই সমীকরণ যতই কঠিন হোক, পথ এগোতে হবে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে।
৩
বলার অপেক্ষা রাখে না, নির্বাচন না হলে দেশ রসাতলে যাবে। ইন্টেরিমের ব্যর্থতার ষোলো কলা পূর্ণ হলে দেশ যাবে অন্য কারো কবজায়। এতে ছোট ছোট দলের চেয়ে ক্ষতিটা বড় দল হিসেবে বিএনপির বেশি। এমতাবস্থায় বিএনপি সব দলকে ডেকে প্রশাসনের ব্যর্থতা তুলে ধরার পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচন, সংকট ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারে।
বিএনপিতে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে দেশের প্রায় মোট মুক্তিযোদ্ধার অর্ধেক। দলটির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, যিনি নিজে মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্সের প্রধান ছিলেন। সেই দলটির একাত্তর ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে আপসহীন থাকাটা স্বাভাবিক। আলোচনার সুবিধার্থে বলা যেতে পারে, একজনও মুক্তিযোদ্ধা দলটিতে না থাকলেও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির সূর্যসন্তান। বিএনপি তা জানে, মানে এবং স্বীকারও করে। করতেই হবে। ভবিষ্যতে যেন তা অব্যাহত থাকে বিষয়টি জাতির সামনে পুনরায় ব্যক্ত করার অর্থ হলো দেশের আগের ইতিহাস বিএনপি কখনোই ভোলে না। একই সঙ্গে নব্বই ও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থানে শহীদদের ব্যাপারে বিএনপি বেশ তৎপর। জুলাই চব্বিশ স্মরণে তাদের এক বছর পূর্তিতে নানা রকম উদ্যোগ ও উদযাপন প্রশংসার দাবি রাখে।
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশের ইসলামী দল কিংবা ধর্মপ্রাণ মানুষের পক্ষে বরাবরই শক্ত শক্তি হিসেবে ছিলেন। তা পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত। বর্তমানে অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম, পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিও বিএনপির অবস্থান ধীরে ধীরে জাতির সামনে পরিষ্কার করতে হবে। মোদ্দাকথা, বিএনপিকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সামনের দিকে এগোতে হবে। এই মুহূর্তে বড় দল হিসেবে সম্ভবত এটিই তাদের দায়িত্ব।
লেখক : কবি ও কথাসাহিত্যিক
ঢাকার আকাশে যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণ : এই মৃত্যুর দায় কার
- ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

টর্ট আইনে ‘Act of God’ নামক একটি শব্দ আছে, যা বলতে এমন একটি ঘটনাকে বোঝায়, যা অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রতিরোধ্য। বলা হয়ে থাকে, দুর্ঘটনার ওপর মানুষের হাত নেই। তাই বলে এমন দুর্ঘটনা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না, যা ২১ জুলাই রাজধানী ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ঘটেছে। ওই দিন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণের সময় বিধ্বস্ত হয়।
দেশের ইতিহাসে অত্যন্ত বিয়োগান্ত এ ঘটনায় কেবল স্বজনহারা পরিবারই নয়, বরং পুরো বাংলাদেশ আজ শোকাহত, মর্মাহত। সর্বমহলে নানা প্রশ্নের সঙ্গে একটি সাধারণ প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে আর তা হচ্ছে, ঢাকার মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়, যেখানে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ বসবাস করে, সেখানে যুদ্ধবিমানের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?
জনবহুল এলাকা কখনো যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণের জায়গা হতে পারে না এবং আন্তর্জাতিক প্রটোকলে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘ Operations in populated or congested areas could increase the likelihood of injury to persons and loss of control’ অর্থাৎ জনবহুল বা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এই কার্যক্রম চালানোর ফলে মানুষের আহত হওয়ার এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে।
জানা যায়, ২১ জুলাই ছিল সংশ্লিষ্ট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মো. তৌকির ইসলামের সলো ফ্লাইট ট্রেনিং। সলো ফ্লাইট ট্রেনিং হলো একজন পাইলটের ট্রেনিংয়ের সর্বশেষ ধাপ।
দেশে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা এবারই প্রথম নয়, এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। যদিও এর আগে দেশে একাধিকবার প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটলেও এতগুলো প্রাণহানি ঘটেনি। যেমন—২০১৫ সালের ১ এপ্রিল রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হলে তামান্না রহমান নামের এক পাইলট নিহত হন। তা ছাড়া ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে টাঙ্গাইলে একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হলে বিমানটির পাইলট উইং কমান্ডার আরিফ আহমেদ নিহত হন। এ ঘটনার এক বছর আগে অর্থাৎ ২০১৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর কক্সবাজারে প্রশিক্ষণের সময় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর দুটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে।
যেসব শিক্ষার্থী বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে আছে, তাদের সর্বোচ্চ চিকিৎসার যে আশ্বাস সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, তা যেকোনো প্রকারে সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। এসবের পাশাপাশি বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আহত ও নিহতদের নাম-ঠিকানা সঠিকভাবে তালিকা আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া। তা ছাড়া বিমানবাহিনীর ব্যবহৃত ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরনো বিমানগুলো বাতিল করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আধুনিক বিমান কিনতে হবে। বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অধিকতর নিরাপদ স্থানে করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা আমাদের দেখতে না হয়।
লেখক : অধ্যাপক (আইন বিভাগ) ও সহযোগী ডিন (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ)
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
kekbabu@yahoo.com
৮৬তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি
আলোকিত মানুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
- জুয়েল আইচ

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নামক চিরতরুণ কিন্তু দারুণ সুসার বৃক্ষটি ৮৬ বছর ধরে আমাদের দেশ ও জাতিকে কত ছায়া, ফুল ও ফল দিয়ে চলেছেন; তিনি তাজা থাকতেই নিজ চোখে তা দেখেও গেলেন। এ আমাদের এক বিরাট সৌভাগ্য।
কোটি কোটি মানুষের কথা এই ক্ষুদ্র লেখায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। শুধু আমার অংশটুকু সামান্য কিছু বলি।
 মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে আমি মারাত্মকভাবে আহত হই। সেই অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধ করার শারীরিক সক্ষমতা হারাই। একটু সুস্থ হলে আমাকে নদীয়া জেলার বাহাদুরপুর ক্যাম্প স্কুলে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে আমি মারাত্মকভাবে আহত হই। সেই অবস্থায় সশস্ত্র যুদ্ধ করার শারীরিক সক্ষমতা হারাই। একটু সুস্থ হলে আমাকে নদীয়া জেলার বাহাদুরপুর ক্যাম্প স্কুলে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
আমার থলেতে যত রকম আনন্দ-বিনোদনের উপাদান ছিল, সব ঢেলে প্রতিটি পিরিয়ডকে বিনোদনমূলক শিক্ষার অনুষ্ঠান করতে লাগলাম। ম্যানেজিং কমিটি জোর করে আমায় সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং বছরের মাথায় প্রধান শিক্ষক হতে বাধ্য করল।
আশৈশব যেসব শিল্পের চর্চা করে এসেছি, উৎসাহ পেয়ে তা আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিলাম। এই সুনাম গ্রাম থেকে থানা, মহকুমা হয়ে সমগ্র বরিশাল জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে। এর পরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ার পরামর্শ আসতে শুরু হলো। হঠাৎ ১৯৭৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একদল ডাকাত বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে আবার আমার সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিল। হায়! এখন বাঁচব কিভাবে?
ঢাকা থেকে আমার কাছে টিভিতে জাদু প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়ে একের পর এক টেলিগ্রাম আসতে শুরু করল। পঞ্চম টেলিগ্রামটি এলে বরিশালের এক বন্ধু তা পড়ে বিস্মিত হয়ে বলল, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাহেবকে তুই চিনিস?
—না তো।
—সেই জন্যই তাঁর এতগুলো টেলিগ্রামের পরেও তোর কোনো হুঁশ হয়নি। তাঁর টিভি প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলে মানুষের জীবন ধন্য হয়ে যায়।
—তোরা তো জানিস, আমার সব পুড়ে শেষ। আমি টিভিতে গিয়ে কী দেখাব?
—তবু তুই সশরীরে আজই যাবি। অন্তত সৌজন্যের খাতিরে হলেও তুই গিয়ে ‘স্যরি’ বলে আসবি।
বন্ধুরা সবাই মিলে আমায় জোর করে লঞ্চে তুলে দিল। ব্যস, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এমনই শক্তিশালী চুম্বক, যাঁর স্পর্শে কেউ একবার গেলে আর ছুটে আসতে পারে না।
প্রথম দেখাতেই তিনি আমাকে ভালোবেসে ফেললেন। আমার কোনো ম্যাজিক না দেখেই তিনি আমাকে পুরোপুরি আস্থায় নিয়ে নিলেন। সামনেই বিটিভির ‘ঈদের আনন্দমেলা’। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে আমাকে ‘আনন্দমেলা’র ক্লোজিং পারফরমার হিসেবে রাখলেন। ঈদের রাতে ‘আনন্দমেলা’ প্রচারিত হলো। আমার প্রদর্শিত ‘শূন্যে ভাসমান তরুণী’ টিভির অগণিত দর্শককে বিস্ময়ে হতবাক করে ফেলল। রাতারাতি টিভি আমায় জাতীয় পর্যায়ের শিল্পী বানিয়ে দিল।
কোনো অডিশন ছাড়াই সায়ীদ স্যার আমাকে এতটা আস্থায় স্থান দিচ্ছেন বলে তাঁর মেধাবী সহকারীদের খুব সংশয় ছিল। এখন তাঁরাই আমার সেরা ভক্ত। তাঁদের মধ্যে ডা. লিয়াকত আলী, ডা. আরিফ, মিজারুল কায়েস, খান লোদী, সুশীল সূত্রধরের কথা আমি জীবনেও ভুলব না।
টিভি প্রোগ্রামের পাশাপাশি আমার স্টেজ শোও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। প্রতিটি স্টেজ শোর দর্শক সারিতে বসে সায়ীদ স্যার নোটবইয়ে আমার ব্যক্তিত্ব, উপস্থাপন, কথা বলা, দর্শকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে আরো ভালো কিভাবে করা যায় সেই পরামর্শ লিখে আমায় দিতেন। সে ছিল আমার জন্য এক মহার্ঘ উপহার।
বছরখানেকের মাথায় আমাদের চার-পাঁচ জনকে নিয়ে তিনি শুরু করলেন পাঠচক্র। প্রথম দিকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনের রাস্তা পেরিয়ে একটি সস্তা ‘ভাতের হোটেলে’ বসতাম। একখানা বই ভাগাভাগি করে পড়ে পরের সপ্তাহে যার যার নিজস্ব মতামত বলে আলোচনায় মেতে উঠতাম। কণ্ঠস্বর ম্যাগাজিনের সাবেক সম্পাদক, অত্যন্ত সফল টিভি উপস্থাপক এবং আমি ছাড়া বাকি সবাই স্যারের সরাসরি ছাত্র। স্যার সবার বিশ্লেষণ মনোযোগসহকারে শুনতেন। সব মিলিয়ে যখন তিনি উপসংহার টানতেন, তখন সবার মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ক্রমে আমাদের বসার একটি ঠাঁই হলো। ৩৭ ইন্দিরা রোড। স্যারের দৃষ্টি সব সময় ভালো থেকে আরো ভালো, বড় থেকে আরো বড়। তাঁর দৃষ্টি বহুধা বিস্তৃত। সেই থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে আমার নাড়ির বাঁধন কখনোই ছিন্ন হয়নি।
আমি দলবল নিয়ে দেশময় শো করে বেড়াচ্ছি। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার ম্যাজিক হওয়ার কারণেই হয়তো দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের সাংবাদিকদেরও দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। হঠাৎ ১৯৮১ সালে ‘সোসাইটি অব আমেরিকান ম্যাজিশিয়ানস’-এর আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম ম্যাজিক দেখাতে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের কোনো ম্যাজিশিয়ানকে আন্তর্জাতিক ম্যাজিক সম্মেলনে দুই হাজার ম্যাজিশিয়ানের সামনে ‘আদর্শ পারফরমার’ হিসেবে ম্যাজিক দেখানো শুধু আমার নয়, দলের কাছেও ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক। দেশের জন্যও ছিল এ এক বিরল সম্মান।
সম্মেলনে দেখানো আমাদের শোর একটি ভিডিও ক্যাসেট সোসাইটি অব আমেরিকান ম্যাজিশিয়ানস আমাদের উপহার দিয়েছিল। তখন বাংলাদেশে ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে আসা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের আশা ছিল আমেরিকায় কী ঘটেছিল, টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দর্শক তা দেখুক। কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কিছুতেই সেই ভিডিও ক্যাসেট আমাকে দিল না। প্রচণ্ড আনন্দ নিয়ে দেশে ফিরেছি। শুরুতেই খেলাম একটি বড় হোঁচট। মনমরা হয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে বের হলাম। গনগনে রোদ। বাইরে বেরিয়েই যা দেখলাম, আমার হৃদয়টা স্নিগ্ধ সুখে ভরে গেল। আমাকে স্বাগত জানাতে আমার কোনো ম্যাজিশিয়ান বন্ধু এয়ারপোর্টে ছিল না কিংবা ছিল না কোনো সাধারণ ভক্তও। কিন্তু যাঁদের কখনো আশাই করিনি এমন একদল মানুষ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। হাতে তাঁদের ফুলের তোড়া এবং সুদীর্ঘ ফুলের মালা। দলের সবাই ছিলেন সে সময়ের ক্ষুদ্র বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চা মেয়ে লুনা ও জয়া।
একসঙ্গে দল বেঁধে হাঁটছি। আর সেই দলের সামনে ও পেছন দিকে উল্টো হেঁটে ক্যামেরা চালাতে চালাতে ছুটছেন সুশীল সূত্রধর। সবাই মিলে আমেরিকার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বৃষ্টির মতো প্রশ্ন করতে লাগলেন। আর আমিও এত দিন পরে আপনজনদের বলতে পেরে খুব আনন্দিত বোধ করছিলাম। কিছুতেই যখন প্রশ্ন শেষ হচ্ছিল না, তখন সিদ্ধান্ত হলো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে (ইন্দিরা রোডে) একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভা হয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে আলোচনা। সে আনন্দ ভোলার নয়।
সেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে চলে এলো বাংলামোটরের আজকের নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানায়। ক্ষুদ্র একতলা পুরনো বাড়ি থেকে এখনকার সুরম্য অট্টালিকাই শুধু নয়, অনেকগুলো ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি, বই পড়া ও সেরা পাঠকদের পুরস্কৃত করার কর্মসূচির মতো অসংখ্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ডালপালা, শাখা-প্রশাখা সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আরো পড়তেই থাকবে।
এই কেন্দ্রের কর্ণধার দুর্লভ ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের ৮৬তম জন্মবার্ষিকীতে জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন।
লেখক : বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী
বীর মুক্তিযোদ্ধা, চিত্রশিল্পী ও ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত
বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবাকে শিল্প হিসেবে দেখা হোক
- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরীফ আজিজ, পিএসসি (অব.)

২৪ জুলাই ‘আন্তর্জাতিক বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মকর্তা দিবস’। বাংলাদেশেও ২৪ জুলাই এই দিনটি উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশে বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবা বা কম্পানিগুলোর আগমন ঘটে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে, যখন সিকিউরেক্স, অতন্দ্র ও নিশ্চিত, শিল্ডসসহ বেশ কয়েকটি কম্পানি ছোট পরিসরে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে আরো অনেক কম্পানি কার্যক্রম শুরু করে।
২০১৬ সালের ১ জুলাই ‘হোলি আর্টিজান’ হামলায় ঢাকার গুলশানে ১৮ জন বিদেশি নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যার পর তা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থানের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। আমরা একটি মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে সুনাম হারাই। তখন দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থায় সংস্কার আনা হয়।
২০০৬ সালে সরকার বেসরকারি নিরাপত্তা কম্পানিগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবা আইন ২০০৬’ প্রণয়ন করে, যা শিল্পের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। এই আইনের মাধ্যমে বেসরকারি নিরাপত্তা শিল্প দেশব্যাপী একটি অপরিহার্য পরিষেবা হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং দেশের নিয়মিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টায় পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।
আজ সারা দেশে ৮০০টিরও বেশি নিরাপত্তা কম্পানি কাজ করছে। এই কম্পানিগুলো ১২ লাখের বেশি কর্মীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে দূতাবাস, হাইকমিশন, জাতিসংঘের সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, সব ধরনের শিল্প, পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যালস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-অ্যাপার্টমেন্টসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। তারা প্রতিদিন হাজার হাজার কোটি টাকা নগদ বহনকারী যানবাহনের মাধ্যমে স্থানান্তর বা পরিবহন করে। দেশের ২০ হাজারের বেশি এটিএম বুথের অপারেশন বন্ধ হয়ে যাবে যদি নিরাপত্তা কম্পানিগুলো কাজ বন্ধ করে দেয়।
বেসরকারি নিরাপত্তা কম্পানিগুলো তাদের কার্যক্রমের পরিধি বাড়িয়েছে এবং বহুমুখী করেছে। এর মধ্যে রয়েছে তদন্ত পরিষেবা, নির্বাহী/ঘনিষ্ঠ সুরক্ষা পরিষেবা, যথাযথ যাচাইকরণ (Due Diligence), জরুরি উচ্ছেদ, সংকটপূর্ণ/দূরবর্তী অঞ্চলের অপারেশন, ইভেন্ট নিরাপত্তা, লজিস্টিক্যাল সহায়তা, ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা, মেরিটাইম নিরাপত্তা, ডগ স্কোয়াড সহায়তা (K9) এবং বিবিধ পরিষেবা।
বাংলাদেশে নিরাপত্তা কম্পানিগুলোর আরো শক্তিশালী হওয়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে সহায়তা প্রয়োজন। কর্মীদের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো সংস্থান নেই বললেই চলে। এই খাতে নিয়োজিত ১২ লাখের বেশি মানুষ নিয়মিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করছেন। দুর্ভাগ্য, তাঁদের অবদানের তেমন কোনো স্বীকৃতি নেই। তাঁদের প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতি প্রয়োজন।
দেশ, সমাজ ও সাধারণ মানুষের জন্য বিশাল অবদান রাখা সত্ত্বেও বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবা সামাজিকভাবে এখনো সম্মানিত নয়। এই পরিষেবার প্রতি আকর্ষণও কম। এর প্রধান কারণ এটি সাধারণত খুব কম বেতনের পেশা। গ্রামের একটি মেয়ে একজন নিরাপত্তা প্রহরীকে বিয়ে করতে চায় না। কারণ সে জানে, ছেলেটি গরিব এবং সমাজের অন্যান্য উর্দিধারী পরিষেবার মতো তার কোনো মর্যাদা নেই।
দেশে বড় কম্পানি, ব্যাংক কনগ্লোমারেট, বড় সিএসআর পারফরমার রয়েছে, যারা ৮ ঘণ্টার মাসিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রতি গার্ডকে সর্বনিম্ন মজুরি বোর্ড অনুযায়ী আট হাজার টাকা প্রদান করে। এত কম পারিশ্রমিকে কিভাবে এই খাত থেকে ন্যূনতম ভালো পরিষেবা আশা করা যায়?
কভিড-১৯-এ এই দরিদ্র নিরাপত্তাকর্মীরা অন্যান্য ফ্রন্টলাইন যোদ্ধার মতো অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জন্য কোনো স্যালুট বা প্রণোদনা ছিল না। নিরাপত্তারক্ষীরা সত্যিই অবহেলিত রয়ে গেছেন।
তবু বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবা একটি ব্যবসা হিসেবে টিকে আছে। উন্নত বিশ্বে এটি একটি বড় ব্যবসা। আশা করি, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে পরিস্থিতি আরো উন্নত হবে এবং এটি ব্যবসা হিসেবে টিকে থাকবে।
লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলিট ফোর্স
এলিট সিকিউরিটি সার্ভিসেস লি.