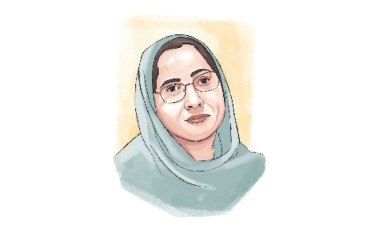মনে দুঃখ পাই, যখন দেখি বাংলাদেশ হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে তার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো চার লেনে রূপান্তর করছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সেগুলো এত এত টাকা ব্যয় করে নির্মাণ করা হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। সেই পুরনোটিই নতুন করে তৈরি করা চার লেন সড়ক। চার লেনের রোডের নাম দিয়েছে ‘হাইওয়ে’।
ভিন্নমত
চার লেন রোডে রিকশা চলে!
- আবু আহমেদ
notdefined

হাইওয়ে ধরে ঢাকা থেকে ফেনী যেতে লাগার কথা তিন ঘণ্টা; লেগে গেল পাঁচ ঘণ্টা। কারণ হলো গাড়ি যে গতিতে যাওয়ার কথা, সেই গতিতে যেতে পারেনি। পথে অনেক বাজার অতিক্রম করে যেতে হলো, যেগুলোর অবস্থান হয় হাইওয়ের ওপর, না হয় এগুলোর কোল ঘেঁষে। অনেক সময়ক্ষেপণ হয়ে গেল মেঘনা ব্রিজের পশ্চিম অংশে। এক ঘণ্টা জ্যামে বসে থাকতে হলো।
 গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। কোনো কোনো গাড়ি আইন ভঙ্গ করে উল্টো দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। তবে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেগুলো যেতে পারেনি। একটু সামনে গিয়ে আবার মাথাটা মেইন লেনের দিকে ঢুকিয়ে দিল। তাতে জ্যামটা যেন আরো তীব্র হতে লাগল। কোনো পুলিশকে দেখলাম না নিয়ম ভঙ্গ করে যেসব গাড়ি উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে থামানোর জন্য। অনেকটা ফ্রি স্টাইলেই চালকরা গাড়িগুলো পুরো রাস্তায় রেখে দিয়েছে। ফল হয়েছে উল্টো দিক থেকে যেসব গাড়ি আসছে সেগুলোও জ্যামে আটকে গেল। এক বিরক্তিকর ও হতাশার চিত্র সবার মুখে ফুটে উঠছে। কিন্তু কিছুই করার নেই, ঘটনার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া! খবর নিয়ে জানা গেল এত গাড়ি একসঙ্গে চিকন মেঘনা ব্রিজে উঠতে পারছে না। তাই ব্রিজের মুখ থেকে দুই মাইল লম্বা এই যানজট। এটা নাকি নিত্যই ঘটছে। মাঝেমধ্যে হাইওয়ে পুলিশের দেখা পাওয়া যায়। তবে তারাও যেন অসহায়। সবই যেন তাদের সক্ষমতার বাইরে। শেষ পর্যন্ত তারাও গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকটা নিয়তির ওপর ছেড়ে দেওয়া, যখন যানজট নিরসন হবে তখন হবে। কারো যেন কিছু করার নেই। আমি ভাবলাম, হায় রে এ দেশের নীতিনির্ধারকরা তোমরা কিভাবে এত বোকা হলে! তোমরা যদি বুদ্ধিমান হতে, তাহলে তো আগেই বোঝার কথা চার লেন হলে গাড়ির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে, জাপানিদের দেওয়া অর্থে আড়াই দশক আগে নির্মিত সরু মেঘনা ব্রিজ তো এত গাড়িকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম হবে না। বাংলাদেশের অর্থের কি এতই অভাব যে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে আরেকটি মেঘনা ব্রিজ তৈরি করা গেল না। কেন আমরা বারবার ছোট একটা ব্রিজ তৈরি করতেও বিদেশিদের সাহায্যের দিকে চেয়ে বসে থাকি।
গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। কোনো কোনো গাড়ি আইন ভঙ্গ করে উল্টো দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। তবে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেগুলো যেতে পারেনি। একটু সামনে গিয়ে আবার মাথাটা মেইন লেনের দিকে ঢুকিয়ে দিল। তাতে জ্যামটা যেন আরো তীব্র হতে লাগল। কোনো পুলিশকে দেখলাম না নিয়ম ভঙ্গ করে যেসব গাড়ি উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে থামানোর জন্য। অনেকটা ফ্রি স্টাইলেই চালকরা গাড়িগুলো পুরো রাস্তায় রেখে দিয়েছে। ফল হয়েছে উল্টো দিক থেকে যেসব গাড়ি আসছে সেগুলোও জ্যামে আটকে গেল। এক বিরক্তিকর ও হতাশার চিত্র সবার মুখে ফুটে উঠছে। কিন্তু কিছুই করার নেই, ঘটনার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া! খবর নিয়ে জানা গেল এত গাড়ি একসঙ্গে চিকন মেঘনা ব্রিজে উঠতে পারছে না। তাই ব্রিজের মুখ থেকে দুই মাইল লম্বা এই যানজট। এটা নাকি নিত্যই ঘটছে। মাঝেমধ্যে হাইওয়ে পুলিশের দেখা পাওয়া যায়। তবে তারাও যেন অসহায়। সবই যেন তাদের সক্ষমতার বাইরে। শেষ পর্যন্ত তারাও গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকটা নিয়তির ওপর ছেড়ে দেওয়া, যখন যানজট নিরসন হবে তখন হবে। কারো যেন কিছু করার নেই। আমি ভাবলাম, হায় রে এ দেশের নীতিনির্ধারকরা তোমরা কিভাবে এত বোকা হলে! তোমরা যদি বুদ্ধিমান হতে, তাহলে তো আগেই বোঝার কথা চার লেন হলে গাড়ির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে, জাপানিদের দেওয়া অর্থে আড়াই দশক আগে নির্মিত সরু মেঘনা ব্রিজ তো এত গাড়িকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম হবে না। বাংলাদেশের অর্থের কি এতই অভাব যে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে আরেকটি মেঘনা ব্রিজ তৈরি করা গেল না। কেন আমরা বারবার ছোট একটা ব্রিজ তৈরি করতেও বিদেশিদের সাহায্যের দিকে চেয়ে বসে থাকি।
এটা আমাদের নিয়তি নয়, এটা হলো আমাদের অজ্ঞতা আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অপারগতা। আমরা কি বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চিন্তাগুলো বদলাতে পারি না। পারি, তবে সবাই পারে না। পারলে তো এক হাজার কোটি (আনুমানিক) টাকায় আরেকটা মেঘনা ব্রিজ এত দিনে হয়ে যেত। সেই দিন যদি গাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞেস করা হতো আচ্ছা আপনি যানজট থেকে মুক্ত হয়ে গন্তব্যে যেতে পারবেন, তবে সে জন্য অর্থ দিতে হবে, কত দেবেন বলেন। তাঁদের বেশির ভাগের উত্তর হতো ৫০০ থেকে এক হাজার টাকা, তবু যানজট থেকে বাঁচাও। এটিই হলো অর্থনীতি। মানুষ অর্থ দিয়ে যানজটমুক্ত সড়কে যেতে রাজি। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, সেই পথটি মানুষের জন্য খোলা নেই। সরকারি ব্রিজ সামান্য টোল, অনেক গাড়ি। সুতরাং যানজটে বসে থেকো। অর্থ এখানে কোনো কাজ করবে না কিংবা অর্থকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ব্রিজটি যদি অর্থনৈতিকভাবে এতই মূল্যবান হয়, তাহলে এই ব্রিজকে সরকারি মালিকানায় রেখে কেন মানুষকে যানজটে ভোগান্তির মধ্যে ফেলে রাখা! এই ব্রিজকে কি শেয়ারবাজারের মাধ্যমে হাজারো বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে অনেক আগেই আরেকটি মেঘনা ব্রিজ তৈরি করা যেত না? যেত তো অবশ্যই। সে জন্য যা করা যেত, তা হলো মেঘনা-দাউদকান্দি ব্রিজ দুটিকে পাবলিক লিমিটেড করে একটা আলাদা কম্পানি করতে হতো। সেই কম্পানিতে সরকার চাইলেই ৫১ শতাংশ বা মেজরিটি শেয়ার রাখতে পারত। বাকি ৪৯ শতাংশ শেয়ারবাজারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিক্রি করতে হতো। আমার বিশ্বাস, যে মূল্যে ওই ৪৯ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা যেত, সেই বিক্রি থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা দ্বিতীয় মেঘনা-দাউদকান্দি ব্রিজ অর্থায়ন করেও আরো অর্থ বেঁচে যেত। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে সরকার দ্বিতীয় মেঘনা-দাউদকান্দি ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের জন্য এই পদ্ধতির অর্থায়নের দিকে যাচ্ছে না কেন? ওই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছেও নেই, স্রেফ হা-হুতাশ করা ছাড়া। শুধু এটুকুই বলব, যাঁদের হাতে ব্রিজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের এসংক্রান্ত কোনো জ্ঞান নেই।
রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের প্রকৌশলীরা সারা জীবন দেখে আসছেন সরকার বা বিদেশি কোনো সংস্থা অর্থ দিচ্ছে, তাঁরা সেই অর্থে কনস্ট্রাক্টর নিয়োগ দিয়ে ব্রিজ নির্মাণ করেছেন। তাঁদের কাছে বাজার থেকে ব্রিজ নির্মাণের অর্থায়নের জন্য অর্থ নেওয়াটা অপরিচিত। কিন্তু ধরে নিলাম রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের প্রকৌশলীরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ বা বাজার থেকে অর্থ নিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু ওই মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদে আসীন লোকেরাও কি এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাবে ভুগছেন? মনে তো হয় না। যেটা তাঁদের ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে, সেটা হলো তাঁরা মনে করেন এত দিন তো এভাবেই চলছে। প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করতে হবে কেন? কিন্তু সেই প্রথার ফল তো হলো মেঘনা ব্রিজের দুই দিকে দুই মাইল লম্বা ট্রাফিক জ্যাম। যে লোকটা তাঁর গাড়িতে মেঘনার পশ্চিম অংশে দেড় ঘণ্টা বসেছিলেন, তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আচ্ছা আপনি যানজটের এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে কত টাকা দিতে ইচ্ছুক? সেই লোক অবশ্যই বলবেন, ‘ভাই আরো ২০০ টাকা দেব, তবু যানজটের এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচান।’ এর অর্থ কী? অর্থ হলো যারা ব্রিজ ব্যবহার করছে তারা যানজটমুক্ত অবস্থায় পার হতে আরো অর্থ দিতে রাজি। কেন আমি এ কথাগুলো বললাম। বললাম এ জন্য যে এই ব্রিজগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও চালানো যায়।
বাংলাদেশ অর্থনীতির অনেক স্থাপনাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালানো যায়, তবে যারা চালাবে তারা কিন্তু পুরো ধারণাটির সঙ্গেই অপরিচিত। ফলে সরকার অবকাঠামো স্থাপনা তৈরি করছে ঠিকই, কিন্তু ওগুলো অর্থনৈতিকভাবে চালানোর অভাবে পুনর্নির্মাণের জন্য বা নতুন কোনো অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অর্থসংকটে ভোগে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ফোর লেন রোডের ব্যয় কত? কয়েক হাজার কোটি টাকা তো অবশ্যই হবে। কিন্তু কারা এ ব্যয় বহন করছে। আমার মতে দেশের জনগণ। অথচ দেশের জনগণ কি এই ফোর লেন রোড ব্যবহার করছে? করছে না। তাহলে সবাই অর্থ দেবে কেন? এটাই হলো এক ধরনের অবিচার। উচিত ছিল যারা ফোর লেন রোড ব্যবহার করছে, সেই বাস-ট্রাক ও প্রাইভেট কারের মালিকদের বলা তাদের ব্যবহারপ্রতি অর্থ প্রদান করার জন্য। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক বা দেশের অন্যত্র নির্মিত ফোর লেন রোড বাস-ট্রাক, প্রাইভেট কারই বেশি ব্যবহার করছে। তাহলে তাদের কেন আনুপাতিক হারে নির্মাণ ব্যয়ের অর্থ দিতে বলা হচ্ছে না? এটা হতো যদি রোডগুলো অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহারের প্রশ্ন আসত।
এখন যে অবস্থা, তাতেই এগুলো হলো কমন পাবলিক সুডস, যার ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে, অর্থ দিতে হবে না। এভাবে চলতে দিলে আমরা বহু অর্থ ব্যয়ে সড়ক তৈরি করব বটে, সেই সড়ক মেরামত করার জন্য বা নতুন রোড তৈরি করার জন্য অর্থ পাব না। আমাদের অর্থের সংকট কোনো দিনই যাবে না। সরকারকে অনুরোধ করব, অন্য দেশ কিভাবে তাদের হাইওয়েগুলো ব্যবহার করছে এর একটু খোঁজ করার জন্য। নিশ্চয়ই অন্য দেশ তাদের হাইওয়েগুলোতে বাজার বসতে ও রিকশা চলতে দিচ্ছে না। আমাদের হাইওয়েগুলোতে বাস-ট্রাকওয়ালারা পার্কিং স্ট্যান্ড (Parking Stand) বানিয়েছে।
কয়েক দিন আগে আমাদের ছাত্রদের আমন্ত্রণে তাদের একটা পিকনিক হাউসে গেলাম গাজীপুর চৌরাস্তা পেরিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডে কয়েক কিলোমিটার পার হলে রোডের পশ্চিম পাশে একটা পিকনিক স্পটে। স্পটটা বেশ ভালোই। অনেক খোলামেলা—চারদিকে বনজঙ্গল আর ধানক্ষেত। যিনি স্পটের মালিক, তিনি বাংলাদেশ বিমানের সাবেক পাইলট। স্পটে গিয়ে দেখলাম তিনি বারান্দায় বসে আছেন। বেশ শৌখিন লোক মনে হলো। আমাকে দেখে বসতে দিলেন। চা পান করালেন। তাঁর পাইলটজীবনের অনেক কথা শুনলাম। পিকনিকে যাওয়াটা আমার সার্থক হয়েছে। পুরনো এবং বর্তমানের অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পেরেছি। তবে যাওয়া-আসার অভিজ্ঞতা ভালো নয়। রাস্তা চওড়া, কিন্তু দখলকৃত। রাস্তা ফোর লেন হয়েছে; কিন্তু বাস্তবতা হলো এই ফোর লেন রাস্তার দুই লেনেই ট্রাক-বাস পার্কিং করে রাখা হয়েছে। মধ্যখানের সরু লেনটায় যানজট লেগেই আছে। রাস্তা হলো ফোর লেনের; কিন্তু সেই রাস্তা যদি বাস-ট্রাকের স্ট্যান্ড হয়ে যায়, তাহলে ওই রাস্তাকে ফোর লেনের বা হাইওয়ে বলে লাভ কী? আমরা রাস্তা নির্মাণ করি বহু অর্থ ব্যয়ে; কিন্তু রাস্তা ব্যবহার ম্যানেজমেন্ট জানি না। আমার মনে হয় যাঁরা রাস্তাগুলোর দায়িত্বে আছেন তাঁদের রোড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শুধু রাস্তা তৈরি করে দিলেই রাস্তা জনগণকে কাঙ্ক্ষিত উপকার দেবে না। ওগুলো যদি দখল হয়ে যায়, তাহলে জনগণের অর্থের অপচয় শুধু বাড়বে।
লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত খবর