তবু কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে হকিংয়ের মতামত কি?
‘সবই কি পূর্বনির্ধারিত’—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বলেছেন তা ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’র দুই তীর ঘেঁষে যায়। তবে ‘না’র দিকটায় জোর বেশি। তিনি যখন দর্শনের নিয়তিবাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত, তখন তাঁর ভাবনার কিছুটা হদিস মেলে। কিন্তু গোল বাধে যখন একই সঙ্গে বলেন, মহাবিশ্বের প্রাথমিক নকশা হয়তো ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন, কিংবা হয়তো সেটাও নির্ধারিত হয়েছিল বিজ্ঞানের বিধিগুলো দিয়ে, তখন ওই দুই ‘হয়তো’ সত্যি আমাদের গভীর সমস্যার গহ্বরে নিক্ষেপ করে।
এবং করে যখন তিনি ‘সব কিছু পূর্বনির্ধারিত’ এই তত্ত্বের সমস্যা নিয়ে ভাবিত হন এবং স্পষ্ট ভাষায়ই বলেন, ‘আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে। আমরা যদি কিছু করব বলে ঠিক করি তাহলে সেটা করার স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে।’ তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে যোগ করা যায় এমন কথা যে সে কাজটি করে ফেলার পর পূর্বনির্ধারিত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।
হকিং মনে করেন, একটি ‘পূর্ণাঙ্গ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব’ বিজ্ঞানেরও অনেক প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করতে পারে। জীবনের উদ্ভব সম্পর্কেও একই ধরনের সংশয় ও অনিশ্চয়তা। ডারউইনের ‘ন্যাচারাল সিলেকশন’, বিবর্তনবাদ ও মানবপ্রজাতির জন্ম যদি অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে কয়েকটি পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত মিলনের পরিণাম হয়ে থাকে তাহলে ছোট্ট জটিল দ্বিকুণ্ডলীর ডিএনএ অণুই বা কেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্তনের ধারায় গঠিত হতে পারবে না?
হয়তো এমন কোনো বিবেচনায় হকিং লিখেছেন, আদিম স্তরে ডিএনএর পাকখাওয়া জোড়া কুণ্ডলী হয়তো একটি উন্নতি ছিল। এমন এক বিবেচনা থেকে হকিং মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ নিয়ে অতিসংক্ষেপে কিছু কথা বলেছেন তাঁর ‘কৃষ্ণগহ্বর’ বইটিতে। আরো বলেছেন, ‘সবই পূর্বপরিকল্পিত’ এমন ধারণার ভিত্তিতে কেউ নিজের আচরণ ঠিক করতে পারে না।
তবে এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তায় সংশয়বাদের দিকে ঝোঁকটাও সত্যি, যেমনটা বলা হয় ওমর খৈয়ামের নাস্তিবাদ সম্পর্কে। কারণ সব পূর্বনির্ধারিত কি না এ প্রশ্নে ধর্মীয় মতবাদের সহায়তায় নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিতর্কের শেষে হকিংয়ের মন্তব্যটি দ্ব্যর্থবোধক : ‘সব কিছু কি পূর্বনির্ধারিত’—এ প্রশ্নের জবাবে আমার উত্তর ‘হ্যাঁ’। কিন্তু উত্তরটা ‘না’ হতে পারে, কারণ কী পূর্বনির্ধারিত তা আমরা কোনো দিনও জানতে পারব না।
এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। কোনো একটি বইতে পড়েছিলাম এমন তথ্য যে জীববিজ্ঞানীদের তুলনায় পদার্থবিজ্ঞানীরা অধিকমাত্রায় ভাববাদী। এ মন্তব্যের পক্ষে প্রমাণ মেলে জিনস, নিউটন প্রমুখ থেকে আইনস্টাইনের মতো পদার্থবিজ্ঞানীর পরম শক্তিবিষয়ক ভাবনায়। বেশ কিছুদিন আগে সংবাদপত্রের এক মন্তব্যে পড়ি একই বিষয়ে হকিংয়ের বিশ্বাসের কথা। আবার এই কিছুদিন আগে সংবাদপত্রেই মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। তাঁর কোন বক্তব্যটিকে সঠিক বলে মনে করব? শেষটা কি?
এ সমস্যার বড় কারণ জীববিজ্ঞানীদের আর মহাকাশবিজ্ঞানীদের কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য। মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য আয়তন, প্রায় সীমাহীন পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানীর যুক্তিতর্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই দার্শনিকের ভাববাদ বিজ্ঞানীর চেতনায় প্রভাব বিস্তার করে। তবু মানতে হয়, অগ্রজদের তুলনায় হকিং অনেকটাই বস্তুবাদী।
হয়তো তাই অনেক আগেকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হন যে অনেকের মতে তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে বাদ দিয়েছেন। জবাবে হকিং বলেন, ‘আমার গবেষণার ফল হচ্ছে মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু, সেটা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত খেয়াল—এ কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার প্রশ্ন, মহাবিশ্ব অস্তিত্বের সমস্যা কেন নিল? আপনার ইচ্ছা হলে বলতে পারেন, এই প্রশ্নের উত্তরই ঈশ্বরের সংজ্ঞা।
দুই.
অসাধারণ মেধাবী মহাকাশবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি, ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি, বিলাতের অক্সফোর্ডে; যদিও তাঁর পরিবারের বাসস্থান ছিল লন্ডনে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাই পড়াশোনাটাও অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ পরিসরে। শিক্ষার্থী জীবনের গোড়া থেকে তাঁর ঝোঁক ছিল গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের দিকে, বিশেষ করে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে।
একপর্যায়ে মহাকাশবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তৈরি হয়। সে জন্য এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর কেমব্রিজে তাঁর পড়াশোনা ও গবেষণা। এরই মধ্যে তিনি দুরারোগ্য মোটরনিউরন রোগে আক্রান্ত হন। নামটা বেশ খটোমটো, সংক্ষেপে ASL. চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এ সম্পর্কে একটি সরস ঘটনা না বলে পারছি না। মেডিসিনের মোটাসোটা বইটিতে ‘নার্ভাস সিস্টেম’ (স্নায়ুতন্ত্র) অধ্যায়টি সবচেয়ে বড়। পড়তে গিয়ে প্রবল হতাশা। ওই ASL থেকে অধিকাংশ রোগের সম্পর্কে লেখা—রোগের উৎস বা কারণ অজ্ঞাত। এর চিকিৎসাও নেই।
তাহলে এত পরিশ্রমে এগুলো পড়ে কী হবে? আর সে প্রতিক্রিয়ায় আমার এক বন্ধু যখনই ‘নার্ভাস সিস্টেম’ পড়তে গিয়ে এজাতীয় বক্তব্যের সম্মুখীন হতেন, তখনই ওই বিশাল মোটা বইটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিতেন। রুমে গভীর মনোযোগে পাঠরত দুই সহপাঠীর চমকে উঠে প্রশ্ন : ‘কী, হলোটা কী?’ জবাব : না, এগুলো পড়ার কোনো অর্থ নেই। অবশ্য পরে একসময় মেঝে থেকে বইটা কুড়িয়ে এনে আবার পড়া শুরু, পরে আবারও একই ঘটনা। এই নিয়ে কী হাসাহাসি!
আশ্চর্য এমন এক কঠিন মস্তিষ্ক স্নায়ুরোগে আক্রান্ত স্টিফেন হকিং চিকিৎসকের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত করে সত্তরোর্ধ্ব বয়স অবধি বেঁচে থেকে মহাকাশবিজ্ঞানের চর্চায় নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারে অবিশ্বাস্য অবদান রেখে গেলেন। বিশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানে বড় দুটি আবিষ্কার ম্যাক্স প্ল্যাংকের কোয়ান্টামতত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব।
দুটি তত্ত্বই পদার্থবিজ্ঞানে বৈপ্লবিক চরিত্রের। কিন্তু আশ্চর্য যে আইনস্টাইন কোয়ান্টামতত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কথাটা হকিংয়ের। কিন্তু এ দুই তত্ত্ব সম্পর্কে হকিং কী বলেন? তিনি যেমন আপেক্ষিকতত্ত্ব মানেন তেমনি কোয়ান্টামতত্ত্ব। কিন্তু তাঁর অধিক পক্ষপাত কোয়ান্টামতত্ত্বের প্রতি। এই কণাবাদী তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেছেন তাঁর বিস্ময়কর তত্ত্বগুলোর ক্ষেত্রে।
তাঁর স্থান-কালবিষয়ক বইতে তিনি লিখেছেন : ‘কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ যোগ করলে এমন একটি সম্ভাবনা মনে আসে, যে সম্ভাবনা আগে ছিল না।’ মহাবিশ্ব বিজ্ঞানকে জনবোধ্য করতে এ বইটি (‘আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম’) অবিশ্বাস্য ভূমিকা পালন করে (১৯৮৭)। একটি তথ্যে দেখছি, বইটির বিক্রয়সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি। ভাবা যায় না।
পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর গবেষণাকর্মের শুরুতেই বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়টি বেছে নেন। তাঁর মৌলিক গবেষণার প্রধান বিষয় ‘কৃষ্ণগহ্বরতত্ত্ব’ (ব্ল্যাক হোল থিওরি) বা বিগ ব্যাং তত্ত্বকেও প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর গবেষণাকর্মের প্রথম পর্বে সহকর্মী ছিলেন মেধাবী গবেষক রজার পেনরোজ, জর্জ এলিস প্রমুখ। দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ কোয়ান্টামতত্ত্ব নিয়ে নিজস্ব গবেষণাকর্মে (১৯৭৪ থেকে) একইভাবে সহকর্মী ছিলেন বিজ্ঞানী গ্যারি গিবনস, ডন পেজ প্রমুখ।
কৃষ্ণগহ্বরবিষয়ক বিস্ফোরণ তত্ত্বের নানা দিক, বিশেষ করে সেখান থেকে শক্তিকণার বিকিরণ (হকিং রেডিয়েশন) নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাঁর খ্যাতির সীমানার অভাবিত বিস্তার ঘটায়। এ আলোচনায় পদার্থবিজ্ঞানের জটিলতায় প্রবেশ না করে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে পদার্থবিজ্ঞানে যেসব ‘বল’ আবিষ্কৃত হয় সেগুলোকে এক তত্ত্বে প্রকাশের চেষ্টা চালিয়েছেন পদার্থবিজ্ঞানীরা।
হকিংও এ প্রচেষ্টার যাত্রী। তবে আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদান রেখেছেন স্টিফেন হকিং। অবাক হওয়ার কিছু নেই সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাস্মারক লেখাগুলোর সংখ্যাধিক্য দেখে। কারণ তাঁর বৈশিষ্ট্য গবেষণাগারের বাইরে বৈশ্বিক সমস্যা, বিশ্বজনসমস্যা, অনাকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, আঞ্চলিক যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি নিয়ে ভাবনা এবং সে ভাবনার প্রকাশ বিবৃতিতে, সাক্ষাৎকারে। সর্বোপরি গবেষণাগারের আবিষ্কার ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের গোচরে নিয়ে আসা। যে উদ্দেশ্যে বিশেষ কয়েকটি বই লেখা জনবোধ্য ভাষায়। এ কাজটি অন্য প্রতিভাবান পদার্থবিজ্ঞানীরা করেননি।
হুইলচেয়ারে বসা মহাকাশবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংকে নিয়ে তাই বাংলাদেশেও সংবাদমাধ্যমে বিচিত্র শিরোনামে শ্রদ্ধা নিবেদন তাঁর প্রয়াণ উপলক্ষে। কারো ভাষ্যে তিনি ‘মহাকালের নায়ক’, কারো ভাষ্যে ‘খেয়ালি বিজ্ঞানী’, কারো মতে ‘কোথাও নিউটন, আইনস্টাইনকে ছাড়িয়ে হকিং’ ইত্যাদি। আমাদের এক বিজ্ঞানীর মতে, ‘তিনি মানবজাতিকে বিজ্ঞানের নতুন স্তরে নিয়ে গেছেন।’
এমন সব শিরোনামের নিবন্ধের তাত্ত্বিক আলোচনার শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশে প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের স্মরণে এ সাদামাটা অতাত্ত্বিক লেখাটি পরিবেশিত।
লেখক : কবি, গবেষক, ভাষাসংগ্রামী
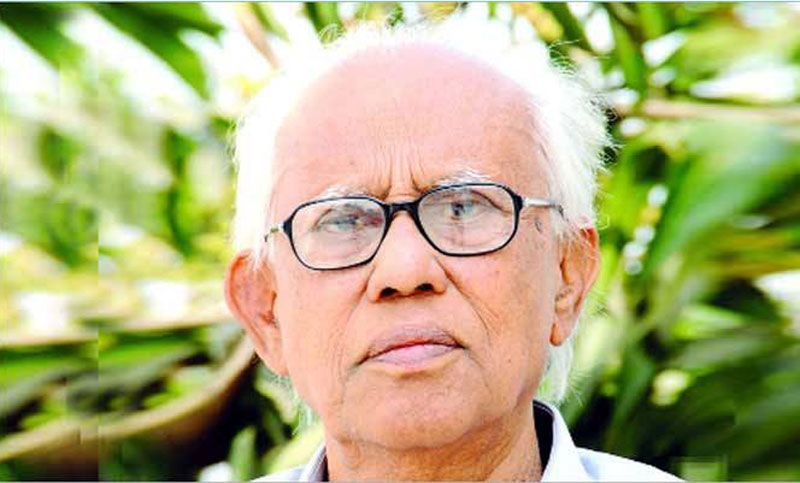
 একমাত্র শেষোক্তজনেই এ বিষয়ে এবং ‘পূর্বনির্ধারিত’ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেখানেও তিনি ঘুরেফিরে সংশয়বাদী। তাঁর জটিল তত্ত্বের গভীরে নাক গলানোর সাধ্য আমার নেই। তত্ত্বকে সাধারণের বোধগম্য করতে তাঁর লেখা বইগুলো তাঁর মতামত বোঝার পক্ষে সহায়ক।
একমাত্র শেষোক্তজনেই এ বিষয়ে এবং ‘পূর্বনির্ধারিত’ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেখানেও তিনি ঘুরেফিরে সংশয়বাদী। তাঁর জটিল তত্ত্বের গভীরে নাক গলানোর সাধ্য আমার নেই। তত্ত্বকে সাধারণের বোধগম্য করতে তাঁর লেখা বইগুলো তাঁর মতামত বোঝার পক্ষে সহায়ক।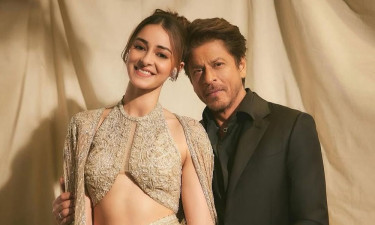






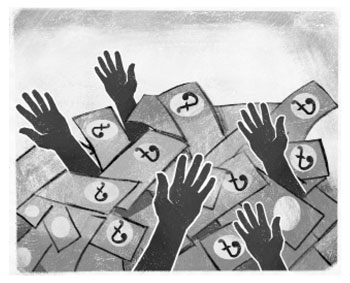 সব আশাব্যঞ্জক গল্পের একটা অন্ধকার দিক থাকে। বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রাকে তেমনি এক আলো-আঁধারির খেলা বললে বোধ করি ভুল হবে না। একদিকে উন্নয়নের ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, অথচ অন্যদিকে ধনী-গরিব বৈষম্য ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতিবিদ হারসম্যান ও রথচাইল্ড বলেছেন, টানেল প্রভাবের কথা : বিদ্যমান কাঠামোতে আয়বৈষম্যের প্রতি যদি সহনশীলতা কম থাকে, তাহলে
সব আশাব্যঞ্জক গল্পের একটা অন্ধকার দিক থাকে। বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রাকে তেমনি এক আলো-আঁধারির খেলা বললে বোধ করি ভুল হবে না। একদিকে উন্নয়নের ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, অথচ অন্যদিকে ধনী-গরিব বৈষম্য ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতিবিদ হারসম্যান ও রথচাইল্ড বলেছেন, টানেল প্রভাবের কথা : বিদ্যমান কাঠামোতে আয়বৈষম্যের প্রতি যদি সহনশীলতা কম থাকে, তাহলে 