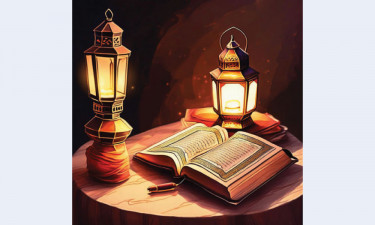সেখানে তার অঢেল সম্পদের পাশাপাশি তার এই ঘটনাটি বর্ণিত আছে যে, সে মুসা (আ.)-কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি নিজেকে আল্লাহর মনোনীত বান্দা বলে দাবি করো। আমিও তো আল্লাহর মনোনীত বান্দা। কারণ ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আমি তোমার চেয়ে অনেক অগ্রগামী (তাওরাত, আসহা-১৬)।
বাইবেলের পুরনো সুসমাচার ((Old Testament))-এর সম্পূর্ণ বিপরীত পবিত্র কোরআনে কারূনের ধন-সম্পদের লোভ, তার সীমাহীন ঔদ্ধত্যের কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু ওই চ্যালেঞ্জের বর্ণনা কোথাও নেই এবং বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। বাইবেলের ওই উক্তি বস্তুবাদী ইহুদিদের এই দর্শনকেই সমুন্নত করে যে সম্পদশালীরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। কোরআনের শিক্ষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাওরাতের উল্লিখিত গ্রন্থের ওই পরিচ্ছেদে কারূনের সম্পদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে- তার কোষাগারের চাবিগুলো চামড়ার তৈরি ছিল এবং ৩০০ উট ওগুলোকে বহন করত। কিন্তু আরবি মুফাসসিরের ভাষ্য অনুযায়ী, চাবিগুলো বহন করতে ৬০টি খচ্চরের প্রয়োজন হতো। 'উসবাহ' শব্দটি আরবি ভাষায় ১০ থেকে ৪০ ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো, কারূনের ধনাগারের চাবি বহন করতেই ২০-৩০ জন লোকের প্রয়োজন হতো। এখানে তাওরাতের বর্ণনার অসারতাই প্রমাণিত হয়। কারণ চামড়ার চাবি সাধারণত এত ভারী হয় না। কিছু কিছু মুফাসসির তাওরাতের বরাত দিয়ে এ কথাও উল্লেখ করেন যে, কারূন মুসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই ছিল। তাই সে এ প্রবঞ্চনায় ছিল যে, আমি নবীর বংশধর এবং অনেক ধন-সম্পদেরও অধিকারী। তাই আমি মুসা (আ.) থেকে অনেক গুণে উত্তম। কারূনের বিশদ বর্ণনা সংবলিত সুরা কাসাস মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষাপট এটা হতে পারে যে, কুরাইশের সরদাররা নবী করিম (সা.)-কে ঠাট্টা করে বলত, আমাদের আল্লাহ তায়ালা অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন। তুমি যদি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে, তোমার কাছেও অনেক ধন-সম্পদ থাকত। কাফেররা এসব কথা সর্বদা বলত এবং মনে করত, রাসুল (সা.) যে ইসলামের প্রতি লোকদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তিনি নিজ অসহায়ত্বের কারণে কখনো সফল হবেন না এবং তারা সর্বদা সফলতার পথেই হাঁটবে। এ ঘটনার মাধ্যমে ধন-সম্পদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করতে হবে, কোথায় ব্যয় করতে হবে? কারূনের ঘটনায় যদিও বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়নি; তথাপি এই মৌলিক বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্পদ যদি মানুষদের আত্ম-অহমিকায় লিপ্ত করে দেয় এবং সে এ কথা ভাবতে থাকে যে, এগুলো শুধু আমার যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার কারণেই অর্জিত হয়েছে, তখন তার কাছ থেকে এই সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।
পবিত্র কোরআন কারূনের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে এভাবে- প্রথমে কারূনের অঢেল ধন-সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়। এরপর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-
'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো' (আয়াত : ৭৭)। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে নিজের পরকালকে সাজাও। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সম্পদ সত্তাগতভাবে কোনো মন্দ জিনিস নয়; কিন্তু সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু দুনিয়া আর দুনিয়ার ভোগবিলাস, তখন সম্পদ মানবজাতির শুধু ক্ষতি ছাড়া কিছুই করতে পারে না। পক্ষান্তরে সম্পদ দিয়ে মানুষ নিজের পরকালকেও সাজাতে পারে। আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, নিঃস্বদের সঙ্গে ভালো আচরণ এবং জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন- হাসপাতাল, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে নিজের আখিরাতের জন্য উত্তম পাথেয়ও জোগাড় করতে পারে। তখন কিন্তু সম্পদ মন্দ কোনো জিনিস নয়। 'ওয়াবতাগি ফী মা আতাকাল্লাহু'- এই বাক্যে ওই সব কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যাতে সে ভালো কাজের মাধ্যমে নিজের আখিরাতকে সমুজ্জ্বল করতে পারে।
পৃথিবীতে বসবাসের আসবাব, যেমন- বাড়িঘর, যানবাহন- এগুলো অর্জন করতে কোনো বাধা নেই। এই চিরসত্যকে মওলানা মছনবী (রহ.) স্বীয় অমর গ্রন্থ মছনবী শরিফে এভাবে ব্যক্ত করেছেন-
'জিসতে দুনিয়া আজ খোদা গাফেল বুদান/ফি ফামাশ ওয়া নাকরা ওয়া ফি জিন্দোজান'
অর্থাৎ দুনিয়াদারি হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া, কাপড়চোপড়, ধন-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজন এগুলো দুনিয়াদারি নয়।
'তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না।' দেখুন, ইসলাম কত চমৎকারভাবে সৎকাজের প্রচার-প্রসারে উৎসাহিত করেছে! আল্লাহ তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে যেমন তোমাকে ধন-সম্পদের অধিকারী করেছেন, তেমনি তুমিও লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আফসোস! শত আফসোস! যদিও কোরআন আমাদের জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, কিন্তু মুসলিম দেশের লাখপতি, কোটিপতি ও শিল্পপতিরা ওইভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে না, যেভাবে ফোর্ড ফাউন্ডেশন (Ford Foundation) অথবা রকফেলার ফাউন্ডেশনসহ (Rokfeller Foundation) অন্যান্য বিধর্মী জনকল্যাণমূলক সংস্থা করে থাকে।
'ফাসাদ' আরবি ভাষার একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। অর্থ বিশৃঙ্খলা। চাই দর্শনগত হোক বা বস্তুগত হোক, সব এর অন্তর্ভুক্ত। 'ফাসাদুল লাবান' অর্থ দুধ বিনষ্ট হওয়া। ফাসাদের বিপরীতে শব্দ 'সিলাহ', এর অর্থ কল্যাণ। যে ব্যক্তি সমাজের উপকারে আসছে না, সে যেন সমাজে প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যকে সমাজে বিশৃঙ্খলা বিস্তারে ব্যবহার করছে, তারা বড় অপরাধী এবং কোরআনের দৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলাকারী।
'কারূন বলল, আমি এই ধন-সম্পদ আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চেয়ে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না' (আয়াত-৭৮)। আজ উপসাগরাঞ্চলে যারা বসবাস করে, তাদের কাছে কারূনের চেয়ে অনেক বেশি ধন-সম্পদ আছে। কিন্তু তারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না এবং মুসলমানদের ওপর যে বিপদ আসে, তাতেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় না। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্মানের আসনে সমাসীন করেননি। বরং তারা পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং তারা নিজেরা পূর্ণ স্বাধীনও নয়। তারা বিশেষ ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। কারূনের শেষ পরিণতি তাদের ভাগ্যেও জুটতে পারে। 'একদিন কারূন পূর্ণ জাঁকজমকসহকারে তাদের সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো' (আয়াত-৭৯)।
ইয়াওমুয জিনাহ, যা তাদের কাছে একটি উৎসবের দিবস ছিল। এর পূর্ণ বিবরণ যদিও কোরআনে উল্লেখ নেই, কিন্তু (Jewish Encyclopedia)-তে উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে পাঁচ হাজার দাসী ছিল, যারা স্বর্ণালংকারে সুসজ্জিত ছিল। অনেক অশ্বারোহী ও চাকরবাকরও ছিল।
'যারা পার্থিব জীবনের প্রত্যাশী ছিল, তারা বলল, হায়! কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের যদি তা দেওয়া হতো! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান।'
আমাদের মধ্যেও অনেকেই সম্পদশালীদের দেখলেই প্রত্যাশা করে যে, হায়! আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা অনুচিত।
'আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদের, যারা ইমানদার ও সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া সাওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী' (আয়াত-৮০)।
এখান থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ইমানদারের জন্য কারূনের মতো প্রাচুর্যে প্রত্যাশী হওয়া সমীচীন নয়। বরং আল্লাহর প্রতিদানেরই প্রত্যাশী থাকবে।
'অতঃপর আমি কারূণ ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না' (আয়াত-৮১)।
এরপর দ্বিতীয় গ্রুপের আলোচনা করা হয়,
'গতকাল যারা তার মতো হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়! আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরও ভূগর্তে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফের সফলকাম হবে না। অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ কখনো সফল হয় না' (আয়াত-৮২)।
এই পুরো ঘটনার সারাংশ সামনের আয়াতে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে- 'এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা পৃথিবীর বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম তো খোদাভীরুদের জন্যই' (আয়াত-৮৩)। এরপর মহান আল্লাহ একটি সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করেন, 'যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিণামেই প্রতিফল পাবে' (আয়াত-৮৪)। অর্থাৎ একটি নেকির প্রতিদানে ১০টি নেকি। বরং এরূপ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, ৭০০ নেকি পর্যন্ত আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন। তার বিপরীত একটি মন্দ কাজের জন্য একটি মন্দ কাজের শাস্তিই ভোগ করতে হবে।
এটি ওই কারূনের ঘটনা সারাংশ, যাকে আল্লাহ তায়ালা অঢেল ধন-সম্পদ দান করা সত্ত্বেও সে সৎকাজ করে কোটি কোটি নেকি উপার্জন করতে পারেনি; বরং সে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। ফলে সে পৃথিবীতেও তার সম্পদ ভোগ করতে পারেনি। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যদি আমরা সীমা লঙ্ঘন না করে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করি, তাহলে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণই থাকবে না। আর গরিবরাও সম্পদের প্রত্যাশা না করে আখিরাতের প্রতিদান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করাটাই আল-কোরআনের শিক্ষা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।
সৌজন্যে : উচ্চতর তাফসির গবেষণা বিভাগ
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা